একদা 'ভেজাল শরৎ' নিয়ে করুণ বিড়ম্বনার শিকার হয়েছিলেন দুই বাংলার প্রবল জনপ্রিয় কথাশিল্পী শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
সময়টা ১৯১৭ সাল।
শরৎবাবুর চরিত্রহীন উপন্যাস সবে বেরিয়েছে। এ উপন্যাস নিয়ে চারদিকে তাঁর নিন্দা ও নামডাক—দুই–ই হচ্ছে। যেমন আসছে শংসাবাক্য, তেমনি পাচ্ছেন তির্যক সমালোচনাও। প্রকাশকেরা এমন বই-ই চেয়েছিলেন।
এই একই সময়ে দেখা গেল শরৎচন্দ্রের নামে আরেকটি উপন্যাসও বেরিয়েছে, 'চাঁদমুখ'! এখানেই শেষ নয়, চাঁদমুখ বিক্রিও হচ্ছিল খুব। অথচ এই উপন্যাস তো শরৎচন্দ্র লেখেননি! ‘কী হচ্ছে এসব!’ হইচই শুরু করে দিলেন তাঁর প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। তবে আসল শরৎচন্দ্র ব্যাপারটা কানেই তুললেন না। কিন্তু প্রকাশক মশাই নাছোড়বান্দা। তিনি ব্যবসায়ী, ম্যালা খরচ করেছেন শরতের বইয়ে। এখন যদি নকল কেউ এসে ব্যবসায় জেঁকে বসে, তাহলে তো তাঁকে পথে বসতে হবে।
একদিন হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এসে শরৎচন্দ্রকে বললেন, "ওহে শরৎ, এর একটা কিছু বিহিত করো। তোমার নাম ভাঁড়িয়ে আরেক শরৎ চাটুজ্যে যে বাজারে বই ভালোই কাটিয়ে দিল।"
কে শোনে কার কথা। এসব পাত্তাই পেল না শরৎচন্দ্রের কাছে। তিনি বললেন, পাঠকই ধরে নেবে কে খাঁটি আর কে ভেজাল। আদতে এমনটা হয়নি। আমজনতার খুব অল্পই সেটা ধরতে পেরেছে। এদিকে তত দিনে তাঁর নামে 'হীরক দুল' ও 'শুভ লগ্ন' নামে উপন্যাস বেরিয়ে গেছে আরও দুটো। এবার কিছুটা টনক নড়ল শরৎচন্দ্রের। জানার চেষ্টা করলেন, কে এই ভেজাল শরৎ?
'ভেজাল শরৎ' ছিলেন 'গল্পলহরী' নামক এক পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তখন তাঁর খুব দুর্দিন চলছিল, পত্রিকা চলে না। কিন্তু 'খাঁটি শরৎ' আর তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নামটি একই। তাই 'নাম' পুঁজি করে নেমে গেলেন উপন্যাস রচনায়; এবং দেখলেন, বইয়ের কাটতি বেশ ভালো। সুতরাং আর থামলেন না।
তত দিনে নকলের হাত থেকে বাঁচতে উপায় খুঁজছিলেন আসল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু উপায়ই বা কী? হাজার হলেও 'নকল শরৎচন্দ্র' যে একটা পত্রিকার সম্পাদক, তাঁর নামে তো আর মামলা-মোকদ্দমা করা যায় না। সেটা তাঁর নিজেরই মানে ঠেকে। আবার এককথায় তাঁকে নকল ঠাওরানোও কি ঠিক হবে! ওই বেচারাও তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এসব সাত-পাঁচ ভেবে অস্থির তখন দেবদাসের স্রষ্টা। নিজের নাম নিয়ে তিনি তখন ঘোর দুর্বিপাকে।
এ সময় এগিয়ে এলেন 'বাতায়ন' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল। তিনি ছিলেন শরৎবাবুর খাস লোক। তাঁরা দুজনে বসে অনেক ফন্দি-ফিকির করলেন, কীভাবে থামানো যায় ব্যাটাকে! কিন্তু কোনোটিই মনঃপূত হয় না শরৎচন্দ্রের। একবার অবিনাশ তাঁকে বলেন, "বরং আপনিই চলে যান তার কাছে। আপনাকে ফিরিয়ে দেবে না। বিহিত একটা হবেই।" এ প্রস্তাব পছন্দ হয় না শরৎচন্দ্রের। পরক্ষণে শরৎ বলেন, "অবিনাশ, তুমিই যাও। গিয়ে তাকে মারপিটের ভয় দেখাও। বলো, চরিত্রহীন বইটি প্রকাশের পরে অনেকেই শরৎচন্দ্রকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করছে। সিটি কলেজের ছেলেরা মারতেও পারে। এখন যদি আপনি শরৎচন্দ্র নামে লেখেন, তবে কখন আবার বিপদে পড়বেন।"
অবশেষে আসল শরৎচন্দ্রের হয়ে অবিনাশ ঘোষালই গেলেন নকল শরৎচন্দ্রের কাছে। প্রস্তাব দিলেন নাম পাল্টানোর। কিন্তু না, ওটা তো করবেন না তিনি। অতঃপর 'গল্পলহরীর শরৎচন্দ্র' বললেন, "এক কাজ করা যাক, বইয়ে বড় করে আর্ট পেপারে ছবি ছাপলেই তো মামলা খতম। আমি আমার বইয়ে ছবি ছাপব, তিনিও যেন তাঁর বইয়ে ছবি ছাপেন।" কথা শেষে ফিরে গেলেন অবিনাশবাবু।
মাসখানেক পরে বাজারে এল 'গল্পলহরীর শরৎচন্দ্রের' নতুন বই, 'কণকাঞ্জলি'। এখানে শিরোনাম পৃষ্ঠার আগের পৃষ্ঠায় বড় করে তাঁর দাড়িসমেত ছবি দেওয়া হলো, নিচে লেখা, ‘শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জুনিয়র)’।
এই সপ্তাহেই অবিনাশ ঘোষাল তাঁর বাতায়ন পত্রিকায় মূল শরৎচন্দ্রের ছপি ছাপতে চাইলেন। কিন্তু সমস্যা ঘটল অন্যত্র। আসলজনেরও তখন দাড়ি আছে— ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। এখন দুজনেরই যদি এক রকম ছবি ছাপা হয়, তাহলে লোকে আসল-নকল বুঝবে কেমন করে!
অগত্যা আসল শরৎচন্দ্রই তাঁর শখের দাড়ি কাটলেন। তারপর শরৎবাবুর দাড়িহীন ছবি ছাপা হলো বাতায়ন-এ। আর ওই ছবির নিচে লেখা হলো, ‘চরিত্রহীন উপন্যাসের লেখক শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়’।
একবার রাগের চোটে কথাই বন্ধ করে দিলেন শরৎচন্দ্র। যতই অভিন্নহৃদয় বন্ধু হোন, এ অপমান তিনি সহ্য করবেন না! কিছুতে না।
গোলমালটা লেগেছিল তাঁর অন্যতম অভিন্ন হৃদয় বন্ধু, সাহিত্যিক ও লেখক শ্রী হেমেন্দ্রকুমার রায়ের সাথে।
হেমেন্দ্রকুমারও সহজে ভাঙার নন! তিনি মনে করেন, যা করেছেন, ঠিক করেছেন। বরং শরৎবাবু যা করেছেন, তার এটাই যোগ্য জবাব।
প্রেসিডেন্সি কলেজের এক ছাত্রসভা। সাহিত্যসম্রাটকে নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎই তাঁকে ‘সেকেলে বঙ্কিম’ বলে ঠাট্টা করে বসলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কথাটি কানে গেল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের।
বন্ধুর এ কথায় এতটাই আহত হন যে, একটি পত্রিকায় শরৎচন্দ্রকে চড়া ভাষায় এক হাত নিয়ে বসলেন।
এমনকী পাল্টা যুক্তি দিয়ে দেখালেন, বঙ্কিম যদি ‘সেকেলে’ হন, তাঁর কাছে শরৎচন্দ্র 'আরও বেশি সেকেলে'।
লেখা পড়ে শরৎচন্দ্র প্রায় নির্বাক। টানা এক বছর ভাল করে কথাই বলেননি বন্ধুর সঙ্গে। পরে অবশ্য আবার সব ভুলেটুলে যান।
'‘দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোর কৃপাদায় পড়াইল পারসী।।’’
হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামকে নিয়ে এই পঙতি লিখেছিলেন রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। স্বভাবতই, সে গ্রাম জড়িয়ে ছিল মহাকবির নামের সঙ্গেই। তবে তার পরে বাংলা সাহিত্যের মহাকাশে আর এক নক্ষত্র জন্ম নিলেন এই দেবানন্দপুরেই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ১২৮৩ সালের ৩১ ভাদ্র এক গরিব ব্রাহ্মণ পরিবারে কথাসাহিত্যিকের জন্ম।
ছেলের সাড়াশব্দ না পেয়ে আদরের সুরে মা ডাকলেন— ‘‘ন্যাড়া, ও ন্যাড়া, খাবি আয় বাবা!’’ তবু উত্তর নেই। রান্নাঘরে ন্যাড়াকে পাওয়া গেল না। গোয়ালঘরেও না। রেগে গিয়ে স্বামীকে বললেন, ‘‘হ্যাঁগা, নিজে তো বেশ খেয়েদেয়ে এখন ঐ ছাইপাঁশ নভেলগুলো পড়ছো! আর ওদিকে ছেলেটা না খেয়ে পাড়ায় টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেদিকে কি খেয়াল আছে?’’ বাবা অবশ্য হাসিমুখে বললেন, ‘‘যাবে আর কোথায় ভুবন! দেখ, ও হয়তো ঐ রায়েদের আমবাগানে ফড়িং ধরছে।’’ সত্যিই তাই। আমবাগানে সুন্দর একটা ফড়িং ধরতে গিয়ে পাখা ভেঙে ফেলেছে ‘বাউন্ডুলে’ ছেলে। তাই তাঁর মন খারাপ। অবশেষে বাবার কথায় ফড়িংটাকে বাগানে রেখেই বাড়ির পথে ফেরে ন্যাড়া। আর প্রতিজ্ঞা করে, ‘‘আমি একটাও ফড়িং বাক্সে রাখবো না। সব উড়িয়ে দেবো।’’ বাবা অবাক হন— ‘‘সামান্য একটা ফড়িংয়ের জন্যে কি কাঁদতে আছে রে?’’
তবে, বালক ন্যাড়া ওরফে শরৎচন্দ্রের লেখাপড়ার প্রতি প্রায় কোনও আগ্রহ ছিল না। গ্রামের পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ছেলেকে ভর্তি করে দিয়েছিলেন বাবা মতিলাল। ছেলের সেখানে না যাওয়ার কারণটা যে ঠিক কী, সেটা বুঝতে পারতেন না তিনি। এক দিনের কথোপকথন ছিল এই রকম:
—ন্যাড়া, পাঠশালায় যাস না কেন?
—ভাল লাগে না যে।
—না পড়লে বড় হবি কি করে?
—পড়লে বুঝি বড় হওয়া যায়?
—হ্যাঁ রে, হ্যাঁ।
তার পরে শরৎ পাঠশালায় গেলেন। তাতে গোল বাড়ল। দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ করে তুললেন পিয়ারী পণ্ডিতকে। এক দিন পাঠশালায় নতুন ছেলে ভর্তি হয়েছে। শরৎ তাঁর কাছে জানতে চাইলেন, সে লিখতে পারে কি না। জবাবে ‘না’ শুনে ‘তবে দে, তোর লেখা লিখে দিই’ বলে স্লেটে বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন, ‘তুই একটা গাধা’। তার পর হঠাৎ হেঁচে তন্দ্রাচ্ছন্ন পণ্ডিতকে জাগিয়ে তুললেন। তাঁর চোখ পড়ল নতুন ছেলেটির উপরে, ‘‘কী ছাঁদের আঁক কচ্ছিস দেখি।’’ স্লেট হাতে নিয়েই পন্ডিতের চিল-চিৎকার, ‘‘বলি, হ্যাঁ রে ছুঁচোমুখো—‘‘তুই একটা গাধা’’ তার মানে কি রে উল্লুক? কেন লিখেছিস জবাব দে।’’ ছেলেটি কাঁপতে কাঁপতে শরতের দিকে তাকায়। আমবাগানে পলায়ন বিনা তাঁর আর কোনও উপায় রইল না।
সন্ধেয় বাড়ি ফিরে বই নিয়ে বসতেন না শরৎ। ভাল লাগত না। ঠাকুমার কাছে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনতে পছন্দ করতেন। আর এক এক সময়ে আশ্চর্য হয়ে বাবার লেখার ঘরে গিয়ে বসতেন। মোটা খাতায় মতিলালের সুন্দর হস্তাক্ষর দেখে জানতে চাইতেন, সেগুলো কী। মতিলাল বলতেন, ‘‘আগে বড় হ’ তারপর ওসব বুঝবি।’’ অবশেষে সে বাবার কাছ থেকে উত্তর আদায় করেই ছাড়ে। ওগুলো নাটক। আসলে মতিলালের পরিবারের আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভাল ছিল না। তার মধ্যেই যাত্রাপালা লেখার কাজ চলত। কাজেই পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যঙ্গ জুটত।
পিয়ারী পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে শরৎকে ভর্তি করা হল সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্যের নতুন বাংলা-স্কুলে। কিন্তু অর্থকষ্ট বাড়তে থাকায় অবশেষে হুগলির পাট চুকিয়ে ১৮৮৬ সালে সপরিবার ভাগলপুরে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন মতিলাল। সেখানে সবাই জানত, শরৎ খুব ভাল ছেলে। ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে ভর্তিও করে দেওয়া হল তাঁকে। কিন্তু এত দিন সে এতই কম শিখেছে যে অকূলপাথারে পড়ল। শরতের একটা গুণ— জেদ ছিল ষোলো আনা। সহপাঠীদের চেয়ে পিছিয়ে থাকার ‘অগৌরব’ সহ্য হল না। লেখাপড়ায় ভাল হয়ে উঠলেন সেই দুরন্ত বালক। মামাবাড়িতে দারুণ গল্পের আসর বসত। তাতেও আগ্রহভরে যোগ দিলেন তিনি। এক দিন শরতের মাসিমা কুসুমকামিনী দেবী ‘কপালকুণ্ডলা’ পড়ছেন। হঠাৎ শরতের প্রশ্ন, ‘নবকুমারকে কাপালিক কেটে ফেলবে?’ তার পরে নিজেই বলেছিলেন, ‘কেটে ফেললেই তো গল্প শেষ হয়ে যাবে। ও কাটবে না।’
দেবানন্দপুরের সঙ্গ ছাড়ার পর অনেকটাই বদলে যান শরৎ। সেটা বুঝতে পেরে খুশি হয়ে মা ভুবনমোহিনীও স্বামীকে বলেছিলেন, “শোরো আজকাল কী শান্ত হয়েছে!” ১৮৮৭ সালে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাশ করে স্থানীয় ইংরেজি স্কুলের সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন তিনি। প্রথম বছর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান তো পানই, সাথে পেয়ে যায় একেবারে ডাব্ল প্রোমোশন! খেলাধুলো আর দুষ্টুমির বদলে মন আকৃষ্ট হয় স্বাস্থ্যচর্চার দিকে। যেমন ভাবা, তেমনই কাজ। কয়েক জন সঙ্গীকে নিয়ে তৈরি করে ফেললেন স্বাস্থ্যচর্চার দল।
বেশ কিছু দিন শ্বশুরবাড়িতে কাটানোর পরে আত্মীয়দের মধ্যে গোলযোগ বাধতে শুরু করায় সপরিবারে পৈতৃক ভিটেতে ফিরতে হয় মতিলালকে। ১৮৮৯ সালে শরৎ ফেরে দেবানন্দপুরে। লেখাপড়া চলতে থাকে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে। পুরনো বন্ধুবান্ধব ফের জুটে যেতেই থিয়েটারের নেশা চেপে বসে। গ্রামের জমিদার নবগোপাল দত্ত মুন্সীর পুত্র অতুলচন্দ্র খুব ভালবাসতেন শরৎকে। তাঁকে মাঝে মাঝে কলকাতায় এনে থিয়েটার দেখিয়ে বলতেন, অভিনয়ের বিষয়বস্তু গল্পের মতো করে লিখতে পারলে পুরস্কার দেবেন। শরৎ লিখতেন এবং পুরস্কারও আদায় করতেন।
শরতের কাব্যপ্রীতির সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে সাংসারিক অনটন। ১৮৯৪-এ ফের ভাগলপুরেই ফিরতে হয় মতিলালদের। শরতের সাহিত্যপ্রেম নিয়ে ‘বাল্যস্মৃতি’তে পাওয়া যায় দু’টি ঘটনা। লিখছেন, “এই সময় বাবার দেরাজ থেকে বের করলাম ‘হরিদাসের গুপ্তকথা’ আর বেরুলো ‘ভবানী পাঠক’। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে। স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদ-ছেলের পাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে।” আর এক জায়গায়, “পিতার নিকট হইতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি।... কিন্তু এখনো মনে আছে ছোটবেলায় তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছিলাম। কেন তিনি এইগুলি শেষ করে যাননি— এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে-ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে।”
এ বার তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুল। আবার ভাগলপুরের পুরনো বন্ধুরা। শরৎ যে পরিবারে বড় হচ্ছিলেন, সেখানে উকিল হওয়াটাই জীবনের লক্ষ্য। অতএব প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এফএ পড়া শুরু হল। আলাপ হল রাজেন্দ্রনাথ মজুমদারের সঙ্গে। এই রাজুই হলেন ‘শ্রীকান্ত’র ইন্দ্রনাথ। নির্জন গড়ের ধারে বসে মনের আনন্দে বাঁশি বাজাতেন রাজু— আকৃষ্ট হয়েছিলেন শরৎ। ঘুড়ি ওড়ানো, তামাক খাওয়া, গান-বাজনা, রাজুর সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, আবার ফিরে আসা, একসঙ্গে নৈশ-অভিযানে জেলেডিঙিতে মাছ-চুরি, যাত্রা-থিয়েটারের মহড়া— চলতে লাগল বন্ধুত্ব যাপন।
১৮৯৫ সালে প্রয়াত হলেন শরতের মা ভুবনমোহিনী। বিহ্বল মতিলাল শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাসা বাঁধলেন খঞ্জরপুর গ্রামে। সেখানেই আবার সমবয়সিদের নিয়ে ‘সাহিত্য-চক্র’ গড়ে তুললেন শরৎ। চলতে লাগল লেখালেখি। সেখানেই এক দিন পঠিত হল ‘অভিমান’ গল্পটি। বন্ধুমহলে লেখক হিসেবে পরিচিতি তৈরি হতে লাগল। সাহিত্যের ভূত এমন ভাবেই ঘাড়ে চেপে বসল যে, এফএ পরীক্ষায় ফল ভাল হল না। পরিবারের মুখের দিকে তাকিয়েও চিরদিনের মতো কলেজের পাট চুকিয়ে সাহিত্য জগতেই আশ্রয় নিলেন তিনি।
শুরু হল ‘কুঁড়ি সাহিত্যিক’ নামে এক সাহিত্য-সভা। বার হতে লাগল হাতে লেখা পত্রিকা ‘ছায়া’। তবে সাহিত্য করে সংসার চলে না। চললও না। জমিদার শিবশঙ্কর সাউকে ধরে তাঁর রাজবনেলী স্টেটে একটা চাকরি জোটানো গেল। তবে টেকানো গেল না। বাবার সঙ্গে মন কষাকষি হল। বাড়ি ছাড়লেন শরৎচন্দ্র।
ঘুরতে ঘুরতে হাজির হলেন মুজফ্ফরপুরে। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের কলমে— “একদিন সন্ধ্যার সময় ক্লাবে তাঁদের দলবল মিলিত হলেন— এমন সময় গেরুয়া-বসনধারী এক তরুণ সন্ন্যাসী এসে পরিষ্কার হিন্দী ভাষায় সবিনয়ে লিখবার সরঞ্জাম প্রার্থনা করলেন।” দেহাতি ছদ্মবেশ ধরা পড়ল। পরিচয় মিলল শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এ দিকে অনুরূপা দেবীর লেখা থেকে জানা যায়, এ সময়ে নিরুদ্দিষ্ট শরতের খাতা থেকে একের পর এক গল্প উদ্ধার হয়েছে— ‘বোঝা’, ‘অনুপমার প্রেম’, ‘বামুনঠাকুর’, ‘কোরেল গ্রাম’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘বড়দিদি’। মুজফ্ফরপুরে বসেই ‘ব্রহ্মদৈত্য’ নামে এক উপন্যাস লেখা শুরু করেন শরৎ। এখানে আলাপ হয় মহাদেব সাউ নামে এক জমিদারের সঙ্গে। ‘শ্রীকান্ত’র কুমারসাহেব তিনিই। অবশেষে ১৯০৩-এ পিতৃবিয়োগের খবর শুনে খঞ্জরপুর ফেরেন শরৎ।
তখন একটা কাজের বড়ই দরকার। কলকাতায় মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে হাজির হলেন শরৎ। উপেন্দ্রনাথের ভাই লালমোহনের কোর্টের কাগজপত্র ও দলিলের অনুবাদের কাজ মেলে। তবে কলম কি আর থামে? ভাগলপুরের যোগেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা থেকে জানা যায়— “তিনি ১৩০৯ সালে একবার ‘কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতা’য় তাঁহার মাতুল সুরেন্দ্রনাথের নামে রচনা পাঠাইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন।” গল্পটির নাম ‘মন্দির’। আসলে শরৎ নিজ নামে কিছু প্রকাশ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন।
এ দিকে মাত্র তিরিশ টাকা বেতনে কাজ করতে শরতের তখন আপত্তি। উপেন্দ্রনাথের কাছে কিছু টাকা ‘কর্জ’ চাইলেন তিনি। বললেন, “এখানে থাকতে আমার মন চাইছে না, উপীন। রেঙ্গুনে নাকি ভাগ্য ফেরে।” রেঙ্গুন তার ঠিক অচেনাও নয়। মাসিমা সেখানে থাকতেন। ১৯০৩ সালে ২৭ বছর বয়সে জাহাজে করে বর্মায় গিয়ে হাজির হন শরৎ। মাসিমারা খুবই বড়লোক। তাঁদের ঘরের ছেলে হয়ে থাকতে শুরু করেন তিনি। সুতরাং জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিছু দিনের মধ্যে বর্মী ভাষাটাও শিখে নেন। অকস্মাৎ মাসিমার স্বামী উকিল অঘোরবাবু প্রয়াত হওয়ায় তাঁরা রেঙ্গুনের পাট চুকিয়ে চলে যান কলকাতা। ফের পথে বসেন শরৎ! তবে এই যাত্রায় কায়ক্লেশে চাকরি জুটিয়ে ফেলেন।
বাবা মারা যাওয়ার পর তিন নাবালক ভাইবোনের একমাত্র আশ্রয় তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। নিঃস্ব অগ্রজ বেরোলেন চাকরির খোঁজে। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তথা উপীন নামের এক আত্মীয়ের সূত্রে একটা চাকরির ব্যবস্থা হল। বেতন ৩০ টাকা।
কিন্তু অত কম টাকায় পোষায় না। ফের বেশি মাইনের চাকরির খোঁজ। এক দিন উপীনের কাছে কিছু টাকা কর্জ চেয়ে বসেন! টাকায় কী হবে? ‘‘এখানে থাকতে আমার মন চাইছে না, উপীন। রেঙ্গুনে নাকি ভাগ্য ফেরে।’’ অগত্যা উপীন তাঁকে জাহাজে তুলে দেন, সঙ্গে ৪০ টাকা। সালটা ১৯০৩।
ভিনদেশে গিয়ে কষ্ট অনেকটা ঘোচে। বর্মা রেলের এজেন্ট জনসন সাহেবের অফিসে ৭৫ টাকা মাইনেতে একটা চাকরি হয়। কিন্তু যাঁর ভরসায় রেঙ্গুন যাত্রা, সেই উকিল অঘোরনাথবাবু কিছু দিনের মধ্যেই নিউমোনিয়ায় মারা যান।
শরৎচন্দ্র ফের নিরাশ্রয়। এ সময় উত্তর বর্মার কিছু অঞ্চলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশে ঘুরে ঘুরে গান গাইতে থাকেন। গানের গলা বেশ ভাল ছিল তাঁর। রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গন) এক অফিসে চাকরি পান, গাইয়ে হিসেবে খ্যাতিও জোটে। বন্ধুদের অনুরোধে বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবের সভ্য হন। প্রবাসী বাঙালিদের সান্ধ্যকালীন মজলিশ তখন তাঁর গানে মাতোয়ারা।
এক দিন শরৎচন্দ্রকে অফিসের মেসে নিয়ে যান সহকর্মী যোগীন্দ্রনাথ সরকার। গানের অনুরোধ আসতে থাকে, হারমোনিয়াম নিয়ে সুর ধরেন শরৎচন্দ্র— ‘শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখবো বলে হে/ তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।’ ঘরে ভিড় জমে গিয়েছিল, তবে হাসি-আড্ডার বদলে এ গানে করুণ রসের উদ্রেক হয়। গান শেষ হওয়ার পর ফের অনুরোধের আসর। অফিসের দাদামশাইয়ের মন্তব্য, ‘‘এমন মধুর গান এ-শালার-দেশে কেউ গাইতে পারে?’’
১৯০৫। শরৎচন্দ্র তখন থাকেন মণীন্দ্রকুমার মিত্র নামে এক ভদ্রলোকের বাড়িতে। মিত্রবাবু এক দিন জানালেন, কবি নবীনচন্দ্র সেন রেঙ্গুনে এসেছেন, তাঁর সংবর্ধনার আয়োজন হচ্ছে, শরৎচন্দ্রকে গান গাইতে হবে। বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাবে অনুষ্ঠান। তখন সেখানে শরৎচন্দ্রের গাওয়া সবচেয়ে জনপ্রিয় গান ‘ওহে জীবন-বল্লভ, ওহে সাধন-দুর্লভ’। অনেকেই ধরে নিলেন, শরৎচন্দ্র কবি-সংবর্ধনায় এই গানটাই গাইবেন। অফিসে হুল্লোড়, জল্পনাও। কেউ কেউ আবার আগে থেকে অফিস ছুটি নেওয়ার ফন্দি করতে লাগলেন, না হলে ‘শরৎদা’র গান মিস হয়ে যেতে পারে! কুমুদিনীকান্ত কর নামে এক কর্মচারী উত্তেজনার চোটে থেকে-থেকে বলতে থাকলেন ‘‘শরৎদা কি জয়!’’
অনুষ্ঠান শুরু হল। ক্লাব ভরভরন্ত। এ দিকে উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়েই এক ফাঁকে বেরিয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। নবীনচন্দ্র তখন গান শুনে আপ্লুত, ‘‘এ যে তোমাদের রেঙ্গুন-রত্ন!’’ গায়কের সঙ্গে আলাপ করতে চাইলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র হাওয়া। অনেক খোঁজাখুঁজির পর ক্লাবের এক ঘরে তাঁর সন্ধান মিলল। কিন্তু কিছুতেই কবির সঙ্গে দেখা করলেন না। ‘‘হৈ-চৈ করে এমনভাবে যশ কুড়িয়ে লাভ কী?’’
হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন, ‘শরৎচন্দ্রের মুখে রবীন্দ্রনাথের নব নব গীত শুনে রেঙ্গুনের বাঙালীরা আনন্দে মেতে উঠতেন,—বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতিতেও তাঁর দক্ষতা ছিল অপূর্ব্ব!’ তবু রেঙ্গুনে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের খ্যাতির লোভ ছিল না। দীর্ঘ প্রবাসে নির্জন ঘরে লিখে চলতেন। কিন্তু ছাপতেন না। তবু ১৯০৭ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হল ‘বড়দিদি’। লেখকের অজ্ঞাতসারেই। সে সময় কলকাতা থেকে সম্পাদক সরলা দেবীর নামে কাগজ চালাতেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। তিনি জানতেন, রেঙ্গুনে যাওয়ার আগে নিজের লেখাগুলি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর কাছ থেকেই ছোট উপন্যাস ‘বড়দিদি’ আনিয়ে তিন কিস্তিতে ছেপে দেওয়া হয়েছিল। লেখকের মত নেওয়া হয়নি, কেননা তিনি মত দেবেন না, এ ব্যাপারে সবাই নিশ্চিত ছিলেন।
পরিবার, বন্ধু, কাউকে কিছু না জানিয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বর্মা (এখন মায়ানমার) পাড়ি দিয়েছিলেন। কিন্তু জাহাজ বর্মার রাজধানী রেঙ্গুনে ঢোকার আগেই তাঁকে যেতে হল ‘কোয়ারান্টিন’-এ। সেই সময় কোনও বন্দরে সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে সেখান থেকে জাহাজ অন্য বন্দরে প্রবেশের আগে জাহাজকে বন্দর থেকে কিছুটা দূরে অন্য এক জায়গায় কয়েক দিন রাখা হত। একেই বলা হয় কোয়ারান্টিন। রেঙ্গুন তখন প্লেগে ভয়ংকর বিপর্যস্ত। বর্মার সাহেবসুবোরা ধরেই নিয়েছিল, প্লেগ ছড়িয়েছে তৎকালীন বম্বের বন্দরে জাহাজে জাহাজে যে কুলিরা কাজ করে, তাদের থেকে। রেঙ্গুন ঢোকার আগেই কুলি আর ডেকের অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রও গেলেন আটকে। এক জঙ্গলঘেরা জায়গায় কাটালেন নয় নয় করে সাত দিন।
অবশেষে ঢোকা গেল রেঙ্গুন শহরে। হাত একেবারে খালি। সে সময় রেঙ্গুন শহরে একটিমাত্র বাঙালি হোটেল—‘দাদাঠাকুরের হোটেল’। সেখানে থেকেই শরৎচন্দ্র তাঁর মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ঠিকানা জেনে শেষমেশ পৌঁছলেন তাঁর কাছে। অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রেঙ্গুনের নামকরা উকিল। শরৎচন্দ্র সাত দিন আটকে ছিলেন শুনে মেসোমশাই বললেন, ‘‘তুই আমার নাম করতে পারলি না? আমার নাম করে কত লোক পার হয়ে যায়, আর তুই পড়ে ছিলিস করনটিনে!’’
বর্মি ভাষা শিখে শরৎচন্দ্র যদি বর্মায় ওকালতি করে তা হলে তাকে আর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে হবে না, এ কথা শরতের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়কে অঘোরবাবু আগেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু শরতের আর উকিল হওয়া হল না। কারণ, তিনি বর্মি ভাষার পরীক্ষাতেই পাশ করতে পারলেন না।
উকিল না হয়েও প্রায় তেরো বছর তিন মাস বর্মায় কাটিয়ে ফেললেন শরৎচন্দ্র। বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন উত্তর বর্মার অলিতে-গলিতে। মিশেছিলেন চোর, ডাকাত, খুনি... হাজারও মানুষের সঙ্গে। বিচিত্র সেই সব অভিজ্ঞতা!
বর্মার নানান জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল সরকারি কন্ট্রাক্টর গিরীন্দ্রনাথ সরকারের। পেশায় সরকারি চাকুরে, কিন্তু তাঁর নেশা ছিল ভ্রমণ। শরৎচন্দ্র বর্মি ভাষা একেবারেই বুঝতে পারতেন না। গিরীনবাবুই তাঁর দোভাষীর কাজ করতেন। এক দিন দু’জনে ঘুরতে বেরিয়েছেন। রাস্তায় দেখলেন, মাছ কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে এক দল বর্মি মেয়ের সঙ্গে কিছু লোকের ঝগড়া হচ্ছে। গিরীনবাবুকে জিজ্ঞেস করে শরৎচন্দ্র জানলেন, বর্মায় মরা মাছের খুব কদর। জ্যান্ত মাছ মেরে খাওয়া নাকি ওদের কাছে অধর্ম। ব্যাপারটা জেনে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, ‘‘তা হলে দেখছি একদিন গুচ্ছের মাছ মেরে ওদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে।’’ উত্তরে গিরীনবাবু বললেন, ‘‘উহুঁ, ওরা এমনি এমনি নেওয়ার পাত্র নয়, যা নেবে পয়সা দিয়ে নেবে। আর যদি বোঝে মতলব খারাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফনানে-ছা। মানে জুতোপেটা!’’
শোনা যায়, প্রণয়ঘটিত ব্যর্থতার যন্ত্রণা ভুলতে প্রথম জীবনে হাতে পয়সা পেলেই শরৎচন্দ্র বেজায় মদ্যপান করতেন। মাঝে মাঝে মদ খেয়ে বেহুঁশও হয়ে পড়তেন। এক দিন শরৎচন্দ্রের বাড়িতে মদ শেষ। কী করা যায়? গভীর রাতে এক বাঙালি বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চললেন তাদেরই পরিচিত এক বর্মি বন্ধুর বাড়ি মদ আনতে। বর্মি বন্ধুটির হার্টের অসুখ থাকায় তাঁর মদ খাওয়া নিষেধ ছিল। অনেক অনুরোধের পর বন্ধুর স্ত্রী মদের বোতল বের করে দিলেন। এ দিকে শরৎ ও অন্য বন্ধুদের কী খেয়াল হল, তাঁরা মদ খেতে বসে পড়লেন ওই বর্মি বন্ধুর বাড়ির বারান্দাতেই। মদ খাবে না, এই শর্তে সেও আসরে যোগ দিল। স্ত্রীর নজরদারিতে গোড়ায় মদ না খেলেও, স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়লে বন্ধুদের অনুরোধে যথারীতি মদের গ্লাসে চুমুকও দিয়ে ফেলল। তার কিছু ক্ষণ পরেই হঠাৎ বুক চেপে ধরে বিকট আর্তনাদ, এবং মৃত্যু!
এর পর শরৎচন্দ্র মদ ছেড়ে আফিম ধরেছিলেন। যে নেশা তাঁর জীবনের শেষ দিন অবধি ছিল। ভাল গান গাইতেন, শরতের গানে মুগ্ধ হয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁকে ‘রেঙ্গুন রত্ন’ উপাধি দিয়েছিলেন।
রেঙ্গুনের যৌনপল্লিতেও নাকি শরৎচন্দ্রের যাতায়াত ছিল। এক বার একটি মেয়ের কাছে গিয়ে দেখলেন, তার বসন্ত রোগ হয়েছে। তা দেখে বন্ধুরা সকলে ভয়ে পালিয়ে গেলেও শরৎচন্দ্র কিন্তু পালালেন না। পয়সা খরচ করে ডাক্তার ডাকলেন, মেয়েটির চিকিৎসা করলেন। এত কিছু করা সত্ত্বেও মেয়েটি বাঁচল না। শরৎচন্দ্র মেয়েটির সৎকারও করেছিলেন।
রেঙ্গুনে বাড়ি ভাড়া করে থাকতেন লোয়ার পোজনডং-এর এক মিস্ত্রিপল্লিতে। সেখানকার মানুষজনের আপদে-বিপদে সাহায্য করা, অসুখে হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ দেওয়া, সব মিলিয়ে শরৎচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন মূর্তিমান মুশকিল আসান। শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা দেখে বন্ধু গিরীন মিস্ত্রিপল্লিকে মজা করে বলতেন ‘শরৎপল্লি’।
এই মিস্ত্রিপল্লিতেই এক অসহায় মেয়েকে সাহায্য করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র বিপদে পড়েছিলেন। ওই পল্লিতে থাকত এক দম্পতি। বছরখানেক পর মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়লে যুবকটি তাকে ছেড়ে পালায়। মেয়েটির প্রসব বেদনা উঠলে স্থানীয় লোকজন গেলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করতে। শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকলেন। সন্তান প্রসবের পর মেয়েটির দুঃখের কাহিনি শুনলেন ও যুবকটির খোঁজে লোক লাগালেন। খোঁজ পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র লোক মারফত যুবকটিকে বলে পাঠালেন, সে যেন তাঁর স্ত্রী ও সন্তানকে গ্রহণ করে। যুবকটি কিন্তু মেয়েটিকে তাঁর স্ত্রী হিসেবে অস্বীকার করল। তারা যে বিবাহিত ছিল না সেটাও জানা গেল। ছেলেটি তখন অন্য এক জায়গায় সংসার পেতেছে।
শুনে বেজায় চটলেন শরৎচন্দ্র। অসহায় মেয়েটিকে বললেন, যুবকের বিরুদ্ধে খোরপোশের মামলা করতে। মামলা কোর্টে উঠলে যুবকটি বলল, মেয়েটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক আছে। সদ্যোজাত সন্তানটি তার নয়, শরৎচন্দ্রের। আর সন্তান প্রসবের সময় সে কারণেই নাকি শরৎচন্দ্র খরচাপাতি করে ডাক্তার আনিয়েছিলেন। বিচারক সব শুনে ডাক্তারের বয়ান নিলেন। ডাক্তার জানালেন, শরৎচন্দ্র তাঁকে ডাকলেও প্রসবের সময় মেয়েটি তাঁর স্বামীর নাম, মানে ওই যুবকটির নামই করেছিল। যে নাম তার ডায়েরিতে লেখা আছে। বিচারক সিদ্ধান্ত শোনালেন। যুবকটি খোরপোশ দিতে বাধ্য হল।
শরৎচন্দ্রের ছিল মাছ ধরার নেশা। বর্মার পেগুতে থাকাকালীন তিনি প্রায়ই যেতেন মাছ ধরতে। এক দিন পুকুরঘাটে গিয়ে দেখলেন, এক সাহেব বেশ তরিবত করে মাছ ধরতে বসেছেন। এ দিকে অল্প সময়ের মধ্যেই শরৎচন্দ্র ধরে ফেললেন একখানা বড় মাছ। তা দেখে ওই সাহেব স্পষ্ট বাংলায় শরৎচন্দ্রের মাছ ধরার তারিফ করে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করতে লাগলেন। সুদূর পেগুতে সাহেবের মুখে বাংলা শুনে শরৎচন্দ্র তো অবাক। পরে জেনেছিলেন, সাহেব অনেক দিন কলকাতায় ছিলেন, সেখানেই বাংলা শেখেন। কথায় কথায় সাহেব জানালেন, আজ মাছ নিয়ে বাড়ি না ঢুকলে মেমসাহেব তাঁকে আস্ত রাখবেন না। কারণ, প্রচুর টাকা খরচ করে তিনি রেঙ্গুন থেকে পেগু এসেছেন স্রেফ মাছ ধরার নেশায়। এখন যদি একটাও মাছ নিয়ে যেতে না পারেন, তা হলে লজ্জার কথা। সব শুনে শরৎচন্দ্র হেসে বললেন, ‘‘আপনি কিছু মনে করবেন না, আমার মাছটি নিয়ে যান।’’
পেগুর বিখ্যাত শিকারি মিস্টার প্যাখামের সঙ্গে শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝেই শিকারে বের হতেন। এক বার সবাই শিকারের আশায় ঝোপের মধ্যে অপেক্ষা করছেন। এমন সময় হঠাৎ গুড়ুম শব্দ। দেখা গেল, শরৎচন্দ্র একটা চিল শিকার করে ফিরছেন। সবাই অবাক। শরৎচন্দ্র বললেন, ‘‘ঝোপের মধ্যে জড়ভরতের মত বসেছিলাম। একদল বককে দেখে গুলি ছুঁড়লাম। মরল চিল।’’ তার পর মৃত চিলের ডানা ধরে দেখিয়ে সবাইকে বললেন, ‘‘দেখো। চিলের গায়ে কোথাও গুলি লাগেনি, এ তো গুলির শব্দে হার্টফেল করেছে।’’
রেঙ্গুনের বাড়িতে ছিল তাঁর নিজস্ব একটি লাইব্রেরি। কাঠের এই বাড়িটি তিনি কিনেছিলেন এক ইউরোপীয় সাহেবের কাছ থেকে। এক বার আগুন লাগল সেই বাড়িতে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল সব কিছু। তার মধ্যেই ছিল ‘চরিত্রহীন’ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি এবং তাঁর নিজের আঁকা বেশ কিছু পেন্টিংও। সব খুইয়ে নিঃস্ব হয়ে শরৎচন্দ্র পথে এসে দাঁড়ালেন, কুকুর ‘ভেলি’ আর পোষা কাকাতুয়া ‘বাটুবাবু’র সঙ্গে।
আক্রান্ত হলেন রোগে। হাত-পা ফুলে যাচ্ছে, যন্ত্রণা। অবস্থা এমন, প্রায়-পঙ্গু পা নিয়ে চলাফেরাই করতে পারেন না। ডাক্তার জানালেন, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের কারণেই এই দশা, বর্মা ছাড়লে তবেই এ রোগ সারবে। এ দিকে চিকিৎসার জন্য ছুটি চাওয়া নিয়ে অফিসে বড়সাহেবের সঙ্গে বচসা বাধল। শরৎচন্দ্র খুব উত্তেজিত হয়ে তেড়ে গেলেন সাহেবের দিকে। বাঙালি কেরানির ঔদ্ধত্য দেখে সাহেব স্তম্ভিত!
সে দিনই কাজে ইস্তফা দিলেন শরৎচন্দ্র। ফিরলেন দেশে। দেশে ফিরে চেহারায় বদল আনলেন। রেঙ্গুনে থাকার সময় দাড়ি রেখেছিলেন। ঘন ঘন সিগারেট খেতেন। খেলতেন দাবা। জীবনচর্চায় ছিল ফরাসি বোহেমিয়ানিজমের প্রভাব। তখন তাঁর গুরু ফরাসি সাহিত্যিক এমিল জোলা। বর্মা থেকে ফেরার কয়েক বছর পর দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ফেললেন। শুরু হল আর এক নতুন জীবন।
‘বড়দিদি’-র প্রথম কিস্তি পড়ে ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকার শৈলেশচন্দ্র মজুমদার সটান রবীন্দ্রনাথকে অভিযুক্ত করে বসেছিলেন, তাঁদের দাবি অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথ ‘ভারতী’-তে লেখা দিয়েছেন বলে। রবীন্দ্রনাথ তো অবাক, ‘‘উপন্যাস লিখ্লামই বা কখন্ আর ভারতীতে তা প্রকাশিত হ’লই বা কেমন ক’রে?’’ শৈলেশবাবুর পাল্টা: ‘‘নাম না দিলেই কি এ আপনি লুকিয়ে রাখ্তে পারেন?’’ আসলে ‘বড়দিদি’ পড়ে বাঙালি পাঠকসমাজের একটা বড় অংশের ধারণা জন্মেছিল, এ নিশ্চয়ই ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ‘বড়দিদি’ পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরে জনমতের চাপে শরৎচন্দ্রের নাম প্রকাশ করে ‘ভারতী’। তবে এত ঘটনার কিছুই জানতে পারেননি লেখক। এমনকি, এই উপন্যাস প্রকাশের খবরটাও এক বইয়ের দোকান থেকে পান রেঙ্গুনের সহকর্মীরা। শরৎচন্দ্র ‘ভারতী’তে চিঠি দেন, পরে মাসে মাসে পত্রিকা আসতে থাকে তাঁর কাছে।
বস্তুত, বর্মাবাসের আগে পর্যন্ত খানিকটা দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েই এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কেবল অনিশ্চয়তার মধ্যে ছুটে বেড়াতে হত শরৎকে। রেঙ্গুন তাঁকে কিছুটা সুস্থিতি দেয়। প্রবাসকালে মনের বৈরাগ্যও কিছুটা ক্ষীণ হয়ে আসে। সংসারী হওয়ার সাধ জাগে। বিয়েও করেন।
"একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবী শেষ ক’রে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত, উদ্যম সীমাবদ্ধ— শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম, ভয়ের কথা মনেই হোলো না।’’
প্রায় ১৮ বছর পরে, ১৯১৩ সালে, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিজের পুনরাগমনকে এ ভাবেই দেখেছিলেন শরৎচন্দ্র। নবপ্রকাশিত ছোট পত্রিকা ‘যমুনা’তে এ সব লেখা ছাপা হতে শুরু করে।
গল্পের শুরুটা অবশ্য বেশ কয়েক বছর আগেই। ১৩১৪ বঙ্গাব্দ। সরলা দেবী তখন ‘ভারতী’র সম্পাদক এবং সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় কলকাতা থেকে তাঁর নামে কাগজ চালান। সৌরীন্দ্রমোহন জানতেন, রেঙ্গুন যাওয়ার আগে নিজের লেখাগুলি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে রেখে গিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র। সেখান থেকে ছোট উপন্যাস ‘বড়দিদি’ আনিয়ে তিন কিস্তিতে ‘ভারতী’তে ছাপিয়েও দেন। লেখকের অনুমতি নেননি, কারণ নেওয়ার চেষ্টা করলে মিলত না! লেখা নিয়ে হইচই পড়ে। শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতেই রসজ্ঞ পাঠক ও সমালোচক মহলে তাঁকে নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃতি অনিবার্য। কাজেই কালের নিয়মে হারিয়ে যান শরৎচন্দ্র। এর পর কী ভাবে ফিরলেন, তাঁর বয়ানেই জানা যায়।
শুধু ফেরা নয়, অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পাঠকমহলে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কয়েক বছরের মধ্যে চাকরি ছেড়ে পাকাপাকি সাহিত্যিক। ‘চরিত্রহীন’ যখন বই আকারে বেরোল, দাম সাড়ে তিন টাকা। প্রথম দিনই বিক্রি হয়েছিল সাড়ে চারশো কপি। বাংলা সাহিত্যে এই রেকর্ড আর কারও ছিল না। পরে তা ভাঙে শরৎচন্দ্রের ‘পথের দাবী’র সৌজন্যে। রেঙ্গুনে অজ্ঞাতবাসের জন্য গেলেও সেখােনই আত্মপ্রকাশ করেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ‘রামের সুমতি’, ‘পথনির্দ্দেশ’, ‘বিন্দুর ছেলে’, ‘নারীর মূল্য’, ‘চরিত্রহীন’-এর জন্ম সেখানেই।
‘যমুনা’ থেকে ‘ভারতবর্ষ’। এ বার কলম চালিয়ে অর্থলাভও হতে লাগল। তবে কেবল ‘ভারতবর্ষ’ নয়, শরৎচন্দ্র ছড়িয়ে পড়লেন ‘বঙ্গবাণী’, ‘নারায়ণ’, ‘বিচিত্রা’য়। কোনও কোনও উপন্যাস সরাসরি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল, যেমন ‘বামুনের মেয়ে’। এ পর্বে লিখলেন ‘বিরাজ-বৌ’, ‘পণ্ডিত-মশাই’, ‘বৈকুণ্ঠের উইল’, ‘মেজদিদি’, ‘দত্তা’, ‘পল্লীসমাজ’, ‘অরক্ষণীয়া’, ‘নিষ্কৃতি’, ‘গৃহদাহ’, ‘দেনা-পাওনা’, ‘নববিধান’, ‘মহেশ’, ‘পথের দাবী’, ‘শেষ প্রশ্ন’... স্বল্প কালপর্বে পরপর এতগুলি জনপ্রিয় ও অমর সৃষ্টি করে যেতে পারেন কেউ? সত্যিই বিস্ময়কর!
‘নারায়ণ’ পত্রিকার গল্পের জন্য শরৎচন্দ্রকে একটা সই করা চেক পাঠিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, সঙ্গে লিখেছিলেন, ‘আপনার মতন শিল্পীর অমূল্য লেখার মূল্য স্থির করবার স্পর্দ্ধা আমার নেই, টাকার ঘর শূন্য রেখে চেক পাঠালুম, এতে নিজের খুসি-মত অঙ্ক বসিয়ে নিতে পারেন!’ এবং নিজের অসাধারণতার মূল্যও নির্ধারণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র— একশো টাকা! দেশবন্ধুর পদক্ষেপেই সাহিত্যিকের জনপ্রিয়তা অনুমেয়।
বাংলা রঙ্গালয়ে শরৎ-সাহিত্যের চাহিদা তৈরি হয়েছিল। সর্বাগ্রে অভিনীত হয়েছিল ‘বিরাজ-বৌ’। নাট্যরূপ দিয়েছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে। তার পর শিশিরকুমার ভাদুড়ী। ‘ভারতী’তে ‘দেনা-পাওনা’র নাট্যরূপ দিয়েছিলেন শিবরাম চক্রবর্তী, নাম ‘ষোড়শী’। অভিনয় করালেন শিশিরকুমার। সাফল্যের পরে অভিনীত হল ‘রমা’, ‘চরিত্রহীন’, ‘অচলা’, ‘বিজয়া’।
নাটকের পরে চলচ্চিত্র। এবং শিশিরকুমার। নির্মিত হল ‘আঁধারে আলো’র চিত্ররূপ। তার পরে ‘দেবদাস’, ‘শ্রীকান্ত’, ‘বিজয়া’, ‘পণ্ডিত মশাই’ ইত্যাদি। তাঁর লেখা দেশি-বিদেশি ভাষায় অনূদিত হতে থাকল। এক কথায়, সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উত্তরণ ও উত্থান রূপকথার মতো। হেমেন্দ্রকুমার রায় বর্ণনা করেছিলেন, ‘যৌবনে যে-শরৎচন্দ্রের দেশে মাথা রাখবার ছোট্ট একটুখানি ঠাঁই জোটে নি, ট্যাঁকে দুটি টাকা সম্বল ক’রে যিনি মরিয়া হয়ে মগের মুল্লুকে গিয়ে পড়েছিলেন, প্রৌঢ় বয়সে তিনিই যে দেশে ফিরে এসে বালিগঞ্জে সুন্দর বাড়ী, রূপনারায়ণের তটে চমৎকার পল্লী-আবাস তৈরি করবেন, মোটরে চ’ড়ে কলকাতার পথে বেড়াতে বেরুবেন...’ সত্যিই, তাঁর দূর বা নিকটজনেরা ভাবতেও পারেননি।
ভারতবর্ষের সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে ‘দেবদাস’ শব্দটি পরিচিত। অদ্ভুত, স্বপ্নময় প্রেমের এক জাদুময়ী হাতছানি এই ‘দেবদাস’ কাহিনীতে। ২০১৭ সালে চলে গিয়েছে 'দেবদাস’-এর শতবর্ষ। অগোচরে। অনাদরে।
শরৎচন্দ্রের অল্প বয়সের রচনা ‘দেবদাস’। অল্প বয়স বলতে পরিণত লেখক হয়ে ওঠার আগে। লেখা শুরুর সময় বিতর্কিত। তবে জানা যায় প্রকাশনার সন। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য। প্রমথবাবু এবং শরৎচন্দ্রের মধ্যে ছিল বন্ধুত্বের সম্পর্ক। ‘দেবদাস’ প্রকাশের জন্য শরৎচন্দ্রকে প্রমথনাথবাবুই প্রথম বলেন। শরৎচন্দ্র এক কথায় রাজি হয়েছিলেন, এমনটা বলা শক্ত।
শরৎচন্দ্র এক চিঠিতে প্রমথনাথ বাবুকে লেখেন, ‘দেবদাস ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়। ওটা ছাপা হয় তা আমার ইচ্ছা নয়। ‘দেবদাস’ নিও না, নেবার চেষ্টাও কোরো না। ওটা ইমমর্যাল’।
বাংলা ১৩২৩ সাল। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে (ইয়াঙ্গন)। সুযোগ এল। এ বার প্রমথবাবু অন্য পথ অবলম্বন করলেন। ধরলেন শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে। লুকিয়ে সংগ্রহ করলেন ‘দেবদাস’-এর পাণ্ডুলিপি। শরৎচন্দ্রের অজ্ঞাতসারেই শুরু হল প্রকাশ। ‘ভারতবর্ষ’ পত্রিকায়। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যার শুরু। ১৩২৪-এর আষাঢ়ে শেষ। অব্যবহিত পরেই ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন সম্পূর্ণ ‘দেবদাস’ উপন্যাস মলাটবন্দি হয়। প্রকাশক ‘গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স’। অবিভক্ত বাংলায় পাঠক সমাজের হাতে এল ‘দেবদাস’। অবশ্য শরৎচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্তে চমকপ্রদ তথ্য মেলে। ১৯০০ সালে শরৎচন্দ্র নাকি এই উপন্যাস লেখা শুরু করেন। তখন তাঁর বয়স বছর চব্বিশ। তবে বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, তা এখনও গবেষণা-বিবেচ্য।
উপন্যাসের শতবর্ষ। কিন্তু ষোড়শ পরিচ্ছেদের কাহিনি মানব মানসে আজও যৌবনে। অমরত্ব যেন তার পরিচিতিতেই। বারবার চলচ্চিত্রে ঘটেছে ‘দেবদাস’-এর নির্মাণ-বিনির্মাণ। কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু সেই প্রেম। কৃত্বিত্ব কিন্তু অবশ্যই কথাশিল্পীর। নিখাদ আবেগ। বাস্তব চালচিত্র। সংস্কার-কুসংস্কার। আর্থিক–বর্ণ-কৌলিন্য। চরিত্র নির্মাণ। ঘটনাস্থলের বৈচিত্র্যময় নির্বাচন, যা স্রেফ শরৎচন্দ্রেরই আপন শৈলি। শুরু থেকেই ঠাস বুনন। পাঠক বাঁধা পড়ে কাহিনির শেষ তক্ পড়ার তাগিদে।
আর একে উপজীব্য করেই ‘দেবদাস’-এর চাহিদা। নির্মাণ হয়েছে যুগে যুগে অনেক চলচ্চিত্র। আগামী দিনেও যা পূর্ণচ্ছেদ পাবে না বলেই অনুমান। ‘দেবদাস’ ঘটনাবহুল। আবার ঘটনাগুলি বহুস্থানিক। তালসোনাপুর, হাতিপোতা, কলকাতা, অশত্থঝুড়ি, কাশী, এলাহাবাদ, মুম্বই-সহ নানা স্থান। কমবেশি সবই গুরুত্বপূর্ণ। তবু অনন্যমাত্রিক হাতিপোতা, যার উল্লেখ উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে। হাতিপোতা গ্রামে জমিদার ভুবন চৌধুরীর দালান। উপন্যাসের শেষও এই গ্রামে। জমিদার বাড়ির সামনে।
হাতিপোতা গ্রাম কিন্তু কাল্পনিক নয়। বাস্তবে এই গ্রামের অবস্থান রয়েছে বর্তমানে পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমায়। ধাত্রীগ্রামের কাছে। নান্দাই পঞ্চায়েতে। সরকারি জরিপে তা স্টেশন পান্ডুয়া থেকে ‘ষোলো ক্রোশ পথ’। অতীতে গোরুর গাড়ির একটা পথও ছিল বলে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস।
হাতিপোতা আজও দেবদাসময়। গ্রামের প্রাচীন মানুষদের বিশ্বাস, শরৎচন্দ্র নদীপথে নান্দাই এসেছিলেন এক বার। সে সময় স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন। শোনেন ‘দেবদাস’-এর অনুরূপ এক জনশ্রুতি, যা কতকটা হাতিপোতা গ্রামের জমিদার চৌধুরীবাড়ি কেন্দ্রিক। তার পরে শরৎচন্দ্র তাঁর কল্পনা, স্ব-অভিজ্ঞতা ও এই লোককথিত গল্প মিশিয়ে লেখেন ‘দেবদাস’। গ্রামে রয়েছে এক ঈদ্গাহ। আর সেখানে প্রাচীন এক ইটের মহল্লার ধ্বংসাবশেষ। গ্রামবাসীরা বলেন, এটাই ছিল জমিদারদের কাছারিবাড়ি। কতিপয় বৃদ্ধদের কথায়, সেখানে একটা প্রাচীন অশ্বত্থ গাছও ছিল। উপন্যাস অনুযায়ী, যার তলায় রোগক্লিষ্ট নায়ক দেবদাস শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। আজ গাছটি নদীর ভাঙনের কবলে পড়ে লুপ্ত।
হাতিপোতার গ্রামবাসীদের মন-মজ্জায় দেবদাস। তাঁরা সেখানে গড়েছেন ‘দেবদাস স্মৃতি ক্লাব’। মাঘের প্রথম সপ্তাহে প্রতি বছর বসে দেবদাস মেলা। দেবদাসকে তাঁরা নিজেদের মানুষ বলে মনে করেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে প্রায়ই হাতিপোতায় আসেন দেবদাস অনুরাগী সংস্কৃতিবান মানুষ। অনেক কিছু জানার ইচ্ছে নিয়ে কথা বলেন। যোগাযোগ রাখেন হাতিপোতার সঙ্গে। ‘দেবদাস’-এর শতবর্ষে তাঁদেরও আগ্রহে খামতি নেই।
অনেকের কাছে ‘দেবদাস’-এর অর্থটা হয়ে দাঁড়িয়েছে, বাণিজ্যিক আয়-উৎসের উর্বর আধার। কোটি কোটি টাকার সফল বাজি। চলচ্চিত্র জগৎ থেকে প্রকাশনা ঘর। কিন্তু শতবর্ষের কথা কার্যত তাঁদের অজানা রয়ে গিয়েছে বলেই মনে হয়।
শুধু মনে রেখে দেয় হাতিপোতা। সম্প্রতি রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছেন। সম্প্রীতি আর শ্রদ্ধায়। গর্বে আর অহঙ্কারে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর কালজয়ী ‘দেবদাস’-কে।
রেঙ্গুন থেকে ফিরে শিবপুরে বাড়ি ভাড়া নিলেও ভিড় আর ভাল লাগছিল না শরৎচন্দ্রের। তাই পাণিত্রাসে (বা সামতাবেড়) নিরালায় বাড়ি বানান। বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি, লেখার ঘরে বসে রূপনারায়ণ দেখা যায়। কখনও লিখতেন, পড়তেন, ভাবতেন। বাগানে গাছেদের সেবা করতেন, পুকুরে মাছেদের খেতে দিতেন।
তবে আদর্শ জীবনে জরা আসে, রোগব্যাধি বাসা বাঁধে। শরৎচন্দ্রের অসুখ ছিলই। এক সময়ে প্রত্যেক দিন জ্বর আর শরীরময় যন্ত্রণা হতে থাকল। চিকিৎসকের নিষেধ সত্ত্বেও জোর করে পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করালেন। তারিখটা ১২ই জানুয়ারি। চার দিন পরে ১৩৪৪-এর ২ মাঘ ৬১ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন শরৎচন্দ্র। বিরাট শোভাযাত্রায় কেওড়াতলা মহাশ্মশানে জনপ্রিয় সাহিত্যিকের শেষকৃত্য হয়েছিল।
বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন, “আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের সাধারণ নিয়মানুসারে বঙ্কিমের প্রতিভার শক্তি পঁয়তাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আসিল।” শরৎচন্দ্রকে দেখলে কি সে কথা বলতেন? তাঁর প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ চল্লিশের কোঠায় গিয়ে প্রকাশিত হয়। তাঁর জীবনকে মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করা যায়— দেবানন্দপুর-ভাগলপুর, ব্রহ্মদেশ, হাওড়া-শিবপুর, সামতাবেড়-কলকাতা। সাহিত্যসাধনাও চার পর্বে। ভাগলপুরে ছোট সাহিত্যগোষ্ঠী। ব্রহ্মদেশে ‘বড়দিদি’ প্রকাশের পরে খ্যাতির সূচনা। দেশে প্রত্যাবর্তন। অবশেষে সাহিত্য সাধনার সূত্র ধরেই শিখরে আরোহণ।
এই গগনচুম্বী জনপ্রিয়তার ব্যাখ্যা করেন অজিতকুমার ঘোষ, “শরৎচন্দ্র সোজাভাবে, স্পষ্ট ভাষায় ও দুঃখ বেদনার কারুণ্যে সিক্ত করিয়া সমাজের সমস্যা তুলিয়া ধরিলেন এবং আমাদের প্রচলিত সংস্কার, নীতিবোধ ও ধর্মবোধের অন্যায় ও জবরদস্তি চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন। ইহার ফলে আমাদের বদ্ধ অচলায়তনের দ্বার যেন হঠাৎ খুলিয়া গেল, এবং সেই মুক্ত দ্বার দিয়া যত আলো ও বাতাস আসিয়া মুক্তির আনন্দে আমাদিগকে চঞ্চল করিয়া তুলিল।”
বাংলা সাহিত্য কোনও গরিবকে ধনী করে তুলেছে, এমন বোধ হয় শরৎচন্দ্রের আগে সে ভাবে কল্পনা করা যেত না। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। রবীন্দ্রনাথ জমিদার। শরৎচন্দ্র এক এবং একমাত্র সাহিত্যেরই জোরে দু’পায়ে ভর দিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।
(তথ্যসূত্র:
১- ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. ক্ষেত্রগুপ্ত, বিশ্বসাহিত্য ভবন।
২- কথাশিল্পের কথামালা: শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর, ভীষ্মদেব চৌধুরী, অবসর প্রকাশনা সংস্থা (২০০৭)।
৩- শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
৪- উদ্ভাসিত শরৎচন্দ্র: পত্রে ও সাময়িকপত্রে, সুদীপ বসু, দে’জ পাবলিশিং।
৫- শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য, ড. নিতাই বসু, টিচার্স বুক এজেন্সী (২০১৪)।
৬- দরদী শরৎচন্দ্র: মণীন্দ্র চক্রবর্তী।
৭- সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র: হেমেন্দ্রকুমার রায়।
৮- শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার: অজিতকুমার ঘোষ।
৯- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে জানুয়ারি ২০১৯ সাল।
১০- আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই জানুয়ারি ২০১৮ সাল।
১১- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে জুলাই ২০১৯ সাল।
১২- আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জানুয়ারি ২০১৬ সাল।
১৩- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই জানুয়ারি ২০১৮ সাল।)
১- ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ড. ক্ষেত্রগুপ্ত, বিশ্বসাহিত্য ভবন।
২- কথাশিল্পের কথামালা: শরৎচন্দ্র ও তারাশঙ্কর, ভীষ্মদেব চৌধুরী, অবসর প্রকাশনা সংস্থা (২০০৭)।
৩- শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
৪- উদ্ভাসিত শরৎচন্দ্র: পত্রে ও সাময়িকপত্রে, সুদীপ বসু, দে’জ পাবলিশিং।
৫- শরৎচন্দ্র : জীবন ও সাহিত্য, ড. নিতাই বসু, টিচার্স বুক এজেন্সী (২০১৪)।
৬- দরদী শরৎচন্দ্র: মণীন্দ্র চক্রবর্তী।
৭- সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র: হেমেন্দ্রকুমার রায়।
৮- শরৎচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যবিচার: অজিতকুমার ঘোষ।
৯- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে জানুয়ারি ২০১৯ সাল।
১০- আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭ই জানুয়ারি ২০১৮ সাল।
১১- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে জুলাই ২০১৯ সাল।
১২- আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই জানুয়ারি ২০১৬ সাল।
১৩- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ই জানুয়ারি ২০১৮ সাল।)





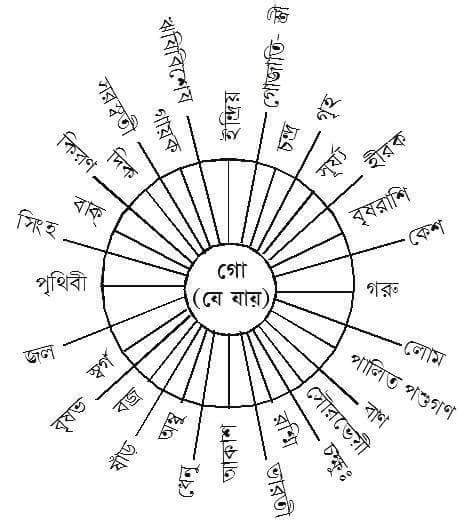

0 মন্তব্যসমূহ