স্বামী বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা। গুরু-শিষ্যার এক অসামান্য সম্পর্ক। স্বামীজির সংস্পর্শে আসার পর মার্গারেট নোবেল আক্ষরিক অর্থেই তাঁর পরবর্তী সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন ভারত ও ভারতবাসীর সেবায়। আইরিশ খাপ খোলা তলোয়ারের মতো তেজস্বিনী এক নারীকে স্বামীজি কী মন্ত্রে আদ্যন্ত ভারতীয়ায় রূপান্তরিত করলেন, তার থই আজও পাওয়া যায় না।
রক্তে আইরিশ, লোকমুখে ইংরেজ রমণী। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর লন্ডনে আলাপ। বয়সে তখনও তরুণী। ওয়েস্ট এন্ডের এক বৈঠকখানায় বিবেকানন্দের একটি অভিভাষণ শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল তরুণীটির। সময় ১৮৯৫, নভেম্বর। তাঁর পোশাকি নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। যে জীবন তিনি এত দিন খুঁজছিলেন, যে সন্ধানী মন নিয়ে তাঁর আকুলতা কোথাও শমিত হতে পারছিল না, বৃত্তিতে শিক্ষয়িত্রী এই মহৎপ্রাণ অন্বেষণ করছিলেন তাঁর পরিসর, তাঁর আত্মোৎসর্গের সঠিক জায়গা, বিবেকানন্দের ধারাবাহিক আলোচনা চক্রে উপস্থিত থেকে তিনি পেয়ে গেলেন সেই মহানভূমির ঠিকানা— ভারতবর্ষ।
২৩শে জুলাই, ১৮৯৭। আলমোড়া থেকে মিস নোব্লকে লিখছেন বিবেকানন্দ, ‘‘কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্তমানে দুর্ভিক্ষনিবারণই আমাদের কাছে প্রধান কর্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কাজ চলছে, দুর্ভিক্ষ-সেবা, প্রচার এবং সামান্য শিক্ষাদান।... তুমি এখানে না এসে ইংল্যান্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশি কাজ করতে পারবে।’’ ২৯শে জুলাইয়ের চিঠিতে আরও খোলাখুলি লিখলেন স্বামীজি, ‘‘এ দেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কী ধরনের, তা তুমি ধারণা করতে পারো না। এ দেশে এলে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা... তা ছাড়া জলবায়ু অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান।... শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র পাবার উপায় নেই।’’
ভারতবর্ষীয় বাস্তবের কঠোর ছবি তুলে ধরেও অবশ্য মিস নোব্লকে ইংল্যান্ডে আটকে রাখা গেল না। তিনি এ দেশে এলেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা অসুবিধেও টের পেলেন। ৩১শে জানুয়ারি ১৮৯৮। এরিক হ্যামন্ডকে তাঁর ভারতবাসের অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন মিস মার্গারেট নোব্ল। সে চিঠিতে মিশেছে চকিত কৌতুক। পার্ক স্ট্রিটের যে বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সে বাড়ির স্নানঘরটিই আয়ারল্যান্ডের মেমসাহেবের কৌতুকের কারণ। স্নানঘরে জলের একটি কল আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে টিনের মগে করে মাথায় জল ঢালতে হয়। এমন ধারা স্নানের অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন। কিছু দিন যেতে না যেতেই অবশ্য এই দেশের সব কিছুই বড় আপন বলে মনে হল। পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার ফেলে আসা অভ্যেস ভুলে এই দেশটিকেই কর্মসূত্রে নিজের করে নিলেন। মিস নোব্ল হয়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। কিন্তু কী ভাবে? কোন মন্ত্রে?
বিবেকানন্দ যে কথাগুলি লিখেছিলেন তা সর্বৈব সত্য। এক জন শিক্ষিত ইউরোপীয়ের কাছে এ দেশের দুর্দশা বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক। নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পক্ষে বাইরের এই প্রতিকূলতাই যথেষ্ট। তবু নিবেদিতা এই প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। অন্তর্দৃষ্টি বলতে কিন্তু অলৌকিক কিছু নয়। অন্তর্দৃষ্টি হল দেখার সেই চোখ যা অন্যের অবস্থানকে বুঝতে চায়, তাকে ‘অপর’ হিসেবে দূরে ঠেলে রাখতে চায় না। এই দৃষ্টি নিবেদিতা অর্জন করেছিলেন তাঁর ইতিহাসবোধ থেকেই। কোনও নতুন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অপরিচয়ের দূরত্ব মোচন করা যায় কী ভাবে? নিবেদিতা লিখছেন, ‘‘দ্য ফাউন্ডেশন-স্টোন অব আওয়ার নলেজ অব আ পিপল মাস্ট বি অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব দেয়ার রিজিয়ন।’’ ভারতবর্ষের মানুষদের বুঝতে গেলে সে দেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য খেয়াল করতে হবে। এও বললেন যে, জানতে হবে সেখানকার মানুষদের শ্রমের প্রকৃতিটি ঠিক কী রকম।
নিবেদিতা তখনও এ দেশে আসেননি। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবি দৃষ্টি সম্বন্ধে ঠাট্টা করে লিখেছিলেন ‘‘বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এ জন্য এ দেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে Moor বলিতে লাগিলেন।’’ নিবেদিতা তো সাধারণ মেমসাহেব ছিলেন না, ভারতবর্ষকে চেনা ও চেনানোর সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। নিজের দেশে যা আছে অপর দেশেও তাই থাকবে এবং তা না-থাকলে মন্দ বলতে হবে এই সঙ্কীর্ণ আধিপত্যকামী দৃষ্টির অধিকারী কেবল পাশ্চাত্যের মানুষেরাই ছিলেন না, ভারতীয়রাও ছিলেন। ভারতীয়রা সাহেবদের মতো ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না বলে তাঁদের সঙ্কীর্ণতায় আধিপত্যবাদ ছিল না, তবে সাহেবমাত্রেই খারাপ এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল ছিল। সাহেব-মেমসাহেবদের যে বাঙালি-বাড়ির ত্রিসীমানায় যেতে দিতে নেই সে সংস্কার ছিল ষোলো আনা। নিবেদিতাকে সংস্কারমুক্ত মা সারদা তাঁর বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা টের পেয়েছিলেন সারদা মায়ের পরিজনেরা এই উদার বাঙালিনীকে একঘরে করতে তৎপর। তিনি নিজেই অন্য বাড়িতে উঠে গেলেন।
বিবেকানন্দ যে ধর্ম-আন্দোলনের প্রবক্তা, সেই ধর্ম আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই ধারার মিলন। বিবেকানন্দ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ নামের যে ধারাবাহিক নিবন্ধটি ‘উদ্বোধন’ পত্রে লিখেছিলেন, তাতে এই দুই সংস্কৃতির মিলনের কথা ছিল। দুই পক্ষেরই অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন— প্রাচ্যকেও চিনতে হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার রীতি-নীতি, পাশ্চাত্যকেও বুঝতে হবে প্রাচ্যের গুরুত্ব। বিবেকানন্দের অনুগামী নিবেদিতার জীবন এই ব্রতেই স্থিতি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষকে চেনাই ছিল তাঁর সাধনা, শুধু যে নিজে চিনছেন তা-ই নয়, তিনি ভারতবাসীদেরও তাঁদের দেশ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন। পরাধীন ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাস নেই। নিবেদিতা তাঁদের হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে তৎপর। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এঁদের সঙ্গে নিবেদিতার সখ্য গভীর। নিবেদিতার উৎসাহেই ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটল। ভারতীয় পুরাকথাকে, গুহাচিত্রের ঐশ্বর্যকে নিবেদিতার সাহচর্যে ভারতীয়রা পুনরাবিষ্কার করলেন। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করছিলেন ইংরেজিতে। নিবেদিতা তাঁর ইংরেজি পরিমার্জনা করে দেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক উপাদান নিয়ে দীনেশচন্দ্রকে নানা প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নে দীনেশচন্দ্রের কাছে তাঁর নিজের দেশের সংস্কৃতি নতুন অর্থে উন্মোচিত হয়। নিবেদিতা লেখেন 'Cradle Tales of Hinduism'। সে বইতে আছে সতীর কাহিনি। সতীর কাছে পিতা দক্ষ শিবের নিন্দা করছেন। ‘‘থিফ, রাসকাল, ইভল, ডিজনেস্ট, ডটার-স্টিলার দ্যাট হি ইজ়!’’ দক্ষের তো অন্তর্দৃষ্টি নেই, তাই এ ভাবেই দেখেন তিনি শিবকে। সতী জানেন এ তো শিবের প্রকৃত রূপ নয়, দেখার চোখ না থাকলে সে রূপ অধরা থেকে যায়। শিবকে দেখার অন্তর্দৃষ্টি ছিল সতীর, যেমন ভারত সম্বন্ধে দেখার গভীর দৃষ্টির অধিকারিণী ছিলেন নিবেদিতা। তাঁর প্রয়াণের পর যে সংবেদী প্রয়াণলেখ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাতে নিবেদিতাকে উপমিত করেছিলেন সতী হিসেবেই।
তা হলে কি এ দেশের অভাব নেই কিছুর? অন্তর্দৃষ্টিতে ভেতরের রূপ দেখেই মোহিত হয়ে থাকতে হবে? না, তা নয়। বিবেকানন্দ তাঁর পত্রে জানিয়েছিলেন নিবেদিতাকে সেবাকার্যের কথা, শিক্ষাব্রতের কথা, এ দেশের অভাবের কথা। নিবেদিতা এ দেশে এসে সে-দু’টি কাজই গ্রহণ করলেন, শিক্ষা আর সেবা এই দুই তাঁর ব্রত। সে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল কারণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারে তিনি এ দেশকে ভালবেসে ছিলেন। তাঁর ইস্কুলে যে পড়ুয়ারা আসে নিবেদিতা তাদের সম্বন্ধে নোট রাখেন। তাদের প্রবণতার ইচ্ছে-অনিচ্ছের খোঁজ নেওয়া চাই। তাঁর এ বাড়ির উঠোনে মাঝে মাঝে আসেন বাঙালি প্রতিবেশীরা। তাঁদের চেয়ারে বসতে দিয়ে মাটিতে বসে থাকেন নিবেদিতা। প্লেগ কলকাতায় মহামারির আকার নেয়। অক্লান্ত সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে দরিদ্র ভারতবাসীর অজ্ঞানতার শেষ নেই যেন। সেবাকার্যে দেশীয় যুবকদের সাহায্য নেন তিনি। বর্জ্যপদার্থ পরিষ্কার করেন যাঁরা, তাঁদের শারীরিক সামর্থ্য ও দেহসৌষ্ঠবে তিনি মুগ্ধ— এঁদের কিনা ভারতীয় সমাজের প্রান্তে ঠাঁই হয়! গোপালের মায়ের সেবা করেন একান্তে। গোপালের মা বালবিধবা, মা সারদার কাছে থাকেন। দু’জনে দু’জনের ভাষা বোঝেন না। তবু অন্তরের যোগ টের পাওয়া যায়। গোপালের মায়ের পায়ের কাছে বসে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেন। এই বিধবার মধ্যে যেন খুঁজে পান নিজের ঠাকুমাকে। সারদা মায়ের বাড়িতে যান। সেখানে নিঃশব্দ বোঝাপড়ায় মেয়েরা ঠাকুরের পুজোর আয়োজন করছেন। তাঁদের এই সম্মিলিত পুজোর আয়োজনে কৌম সমাজের প্রাণ-স্পন্দন টের পান। এ ভাবেই প্রাত্যহিক ছোট ছোট কাজের মধ্যে এ দেশের সঙ্গে তাঁর আদান-প্রদান চলে। এই আদান-প্রদান চলে বলেই স্বামীজির প্রয়াণের পরেও এই দেশেই থেকে গেলেন তিনি। বিবেকানন্দ তাঁর পত্রে লিখেছিলেন নিবেদিতাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এ দেশকে নিজের মতো করে চিনেই নিবেদিতা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছিলেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সীমার বাইরে যে দেশ, তাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।
বিবেকানন্দ প্রথমে মার্গারেটকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। নিদারুণ দারিদ্রপীড়িত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ইংরেজ শাসনের উৎপীড়নে রক্তাক্ত দেশটিতে এসে, অনালোকিত নারীদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিতে চাওয়া উইম্বলডনের এই শিক্ষিকাকে প্রবল ভাবে হতাশ হতে হবে। পরিষ্কার ভাষায় একটি চিঠিতে মার্গারেটকে লিখলেন, “এ-দেশে যে কী দুঃখ, কী কুসংস্কার, কী দাসত্ব— সে তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এ-দেশে এলে দেখবে, চারদিকে অর্ধনগ্ন অগণিত নর-নারী, — ‘জাতি’ ও স্পর্শ সম্বন্ধে তাদের উদ্ভট ধারণা, শ্বেতাঙ্গরা মনে করবে, তোমার মাথা খারাপ, তোমার প্রতিটি গতিবিধি তারা সন্দেহের চোখে দেখবে। তা ছাড়া দারুণ গরম। আমাদের শীতকাল অধিকাংশক্ষেত্রে তোমাদের গ্রীষ্মকালের মতো। দক্ষিণে তো সবসময় আগুনের হল্কা। শহরের বাইরে ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ...এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস করো— স্বাগত তুমি, শতবার স্বাগত।”
স্বামীজির ওই ‘স্বাগত’ শব্দটিই মার্গারেটকে উদ্দীপিত করেছিল, ভারতের ভয়াবহ চরিত্রচিত্র নয়। নভেম্বর ১৮৯৫ থেকে তাঁর স্বপ্নযাত্রা ধরলে তা চূড়ান্ত হল জানুয়ারি ১৮৯৮-এ। ঠিক তিন বছর পরে মার্গারেট তখনকার বন্দর নগরী কলকাতার মাটিতে পা রাখলেন। কলকাতায় সে সময়ে শীতের আমেজ। শহরের কোনও ঘিঞ্জি অঞ্চলে নয়, আপাতত তখন তিনি থাকছেন চৌরঙ্গি অঞ্চলের একটি হোটেলে। ব্যবস্থাপনা অবশ্যই স্বামীজির। কোন হোটেল, তা এখনও জানা যায়নি। তবে যে জাহাজে মার্গারেট কলকাতায় এসেছিলেন, তার নাম ‘মোম্বাসা’। জানুয়ারির শেষ থেকে মার্চের একেবারে মাঝামাঝি সম্ভবত মার্গারেট কলকাতা ও চারপাশ ঘুরে দেখেছেন, তাঁর জীবনদেবতা বিবেকানন্দের অন্যান্য গুরুভ্রাতা ও অনুরাগীদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। সম্ভবত বলছি এই কারণে, ওই কয়েক মাসের মধ্যে লেখা নিবেদিতার কোনও চিঠি পাওয়া যায়নি। এর সম্ভাব্য কারণ, তখন মিস ম্যাকলাউড ও শ্রীমতী ওলি বুল ভারতে। বিবেকানন্দের বন্ধু ম্যাকলাউডকেই প্রাণ খুলে চিঠি লিখতেন মার্গারেট। সর্বাধিক পত্রপ্রাপিকার সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ সে সময়ে যেখানে হাতের মুঠোয়, সেখানে পত্রপ্রেরণ অবান্তর। তবু এই পর্বে লেখা (১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮) একটি চিঠিতে সমসময়ের ইতিহাস খানিকটা চিত্রিত করেছেন মার্গারেট। প্রাপক তাঁর অন্যতম বন্ধু নেল হ্যামন্ডের স্ত্রী। তাঁকে লেখা সেই চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন, “...মঙ্গলবার স্বামীজির সাক্ষাৎ পেলাম। গতকাল তাঁর অতিথি হিসাবে পিকনিক করলাম সুন্দর এক নদীর তীরে (গঙ্গাতীরে), যে-জায়গাটি মিস মূলার মঠ তৈরির জন্য স্বামীজিকে কিনে দিচ্ছেন। জায়গাটা ঠিক উইম্বলডন কমনের কোন একটি অংশের মতোই— গাছপালাগুলোকে খুব খুঁটিয়ে নজর না করলে তফাৎ ধরা পড়ে না।...” এখানে বলে রাখা ভাল, অন্তরঙ্গ বন্ধু নেল হ্যামন্ডকেই পরবর্তী সময়ে লেখা একটি চিঠিতে অকপটে মার্গারেট লিখেছিলেন, “Oh, Nell, Nell, India is indeed a holy land.”
এ বছরের মার্চ মাসেই তাঁর জীবনের দু’টি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল। ১৭ই মার্চ বাগবাজার পল্লির বোসপাড়া লেনের ১০/২ নং বাড়িতে তাঁর গুরুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীমা সারদা দেবীর দর্শন লাভ করে তিনি ধন্য হলেন। সারদা দেবী তখনও প্রায় অবগুণ্ঠিতা, মৃদুভাষিণী, সর্বসাধারণের কাছে অপরিচিতা। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্য ও গৃহী ভক্তরা তাঁর অপার মাতৃত্ব একটু একটু করে উপলব্ধি করছেন। বিকশিত হচ্ছে সারদার বিশ্বমাতৃকা শক্তি। অন্তরালে নির্মিত হচ্ছে তাঁর সর্বগ্রাহ্য, সর্বজনীন জননীর রূপপ্রতিমা। মা সারদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি মার্গারেটের ভাষায় ‘Day of days’। শ্রীমা সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছিল, “তিনি অনাড়ম্বর, সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।” সারা জীবন শ্রীমা সম্পর্কে এই পাবনীভাবনা তাঁকে প্রাণিত করেছিল। বলা যায়, নিবেদিতার অন্তরের নিভৃত কোণে জুঁইফুলের মতো বিরাজ করতেন সারদা, হৃদয়ে অমলিন শ্বেতপদ্মের মতো অধিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ, আর মননে-চিন্তনে, কর্মে বজ্রাগ্নির মতো প্রতিভাত হতেন বিবেকানন্দ।
মিস নোবলের জীবনে দ্বিতীয় এবং অভাবনীয় ঘটনার দিনটি এল ঠিক সাত দিন পরে অর্থাৎ ২৫শে মার্চ। ওই দিন মার্গারেটকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে অবস্থিত অস্থায়ী বেলুড় মঠে স্বামীজি দীক্ষা দিলেন। বিবেকানন্দের স্নেহাশ্রয়ে ও আন্তরিক উপদেশে প্রাণিত মার্গারেট শিবপুজো করলেন। খুব সংক্ষিপ্ত পুজো, মন্ত্র, স্তোত্র। ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত বিদেশিনীর কাছে এই দিনও আর এক অভিধায় ভূষিত— ‘The day of Annunciation’। এই দিনটিতেই তো স্বর্গের দেবদূত যিশুজননী মেরিকে স্বপ্নে জানিয়েছিলেন— তোমার গর্ভে ঈশ্বর জন্মলাভ করবেন! দীক্ষার অন্তে মার্গারেটের হৃদয়ের ‘রাজা’ বিবেকানন্দ প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর নতুন নাম রাখলেন— নিবেদিতা। মার্গারেট রূপান্তরিত, নিবেদিত হলেন, লাভ করলেন নবজন্ম। এখানে বলা যেতেই পারে, ১৮৯৮ সালের প্রেক্ষাপটে ‘নিবেদিতা’ নামটি ভীষণ ভাবে আধুনিক। ‘ডেডিকেশন’ যাঁর রক্তস্রোতে নিয়ত প্রবাহিত, তাঁকে এ ছাড়া আর কোন নামেই বা চিহ্নিত করা সম্ভব? তখনকার দিনে নারীদের নাম যেন পুরাণকল্পের সম্ভার কিংবা ছন্দের পারম্পর্য। তার চেয়েও বিপজ্জনক, চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন নামাবলি— তাতে না আছে সম্মান, না আছে মর্যাদা। এই সব ক’টি দিক বিচার করলে ‘নিবেদিতা’ নামটি অবিকল্প। কেননা স্বামীজি মর্মে মর্মে জানতেন, তাঁর এই মানসকন্যাটি সর্ব অর্থেই ‘আত্মাহুতির সমিধ’।
যাজকদের মতো প্রায় পা অবধি ঢাকা শ্বেতশুভ্র গাউন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কোমরে দড়ির মতো পাকানো রিবন, মাথায় লম্বা চুল— তবে এলায়িত নয়, খোঁপার আকারে পিছনে বেঁধে রাখা চুলের গুচ্ছ। সমস্ত দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সকালবেলার রৌদ্রদীপ্ত আলো। মুখ বিরক্তিহীন, জগৎ ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি প্রসন্নতায় পূর্ণ। বৈরাগ্যের প্রতীক গৈরিক বসন তিনি কখনও পরেননি। বরং ব্রহ্মচর্যের নিষ্কলুষ পোশাককে সারা জীবনে মহত্তর করেছেন। পুরুষদের দেউড়ি থেকে মহিলামহল পর্যন্ত আলোচনার কেন্দ্রস্থলে তিনি। সমস্ত ঔৎসুক্যের নির্যাস প্রচারিত হতে সময় লাগল না। সংস্কারে আচ্ছন্ন উত্তর কলকাতার বোসপাড়া অঞ্চলের মানুষ জেনে গেল, এই বিদেশিনী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বা সিস্টার নিবেদিতা। হিন্দু ধর্মের ‘টলারেন্স’ ও ‘অ্যাকসেপ্ট্যান্স’-এর চিরসত্যকে যিনি আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে এসেছেন, এই তরুণীকে তিনিই নিয়ে এসেছেন এ দেশের সেবাব্রত সম্পাদনের জন্যে। তাঁরা এও জানলেন, এঁর ভিতরে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন এক মহীয়সী সত্তা, যে সত্তার কাছে সিমলার নরেন দত্তের আহ্বান— “জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের ধারা; হায়! যুগ যুগ ধরে তা চলতে থাকবে! পৃথিবীর যারা বীরোত্তম ও সর্বোত্তম, তাদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে ‘বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।’ ...নিঃস্বার্থ, অগ্নিজলন্ত প্রেম যাঁদের মধ্যে— তাঁদের এখন জগৎ চায়। সেই প্রেম প্রতিটি উচ্চারিত শব্দকে বজ্র করে তুলবে।”
এত দূর জানার পরেও পল্লিসমাজের ভ্রুকুঞ্চন থেকেই গেল। কেননা এই নারী যে বিধর্মী, ম্লেচ্ছ, বিদেশ থেকে এসেছেন! এঁর ছোঁয়াছুঁয়িতে জাত রাখাই যে বড় দায়! রেনেসাঁস ঋদ্ধ কলকাতা তখনও এই ঘন অন্ধকারে আচ্ছাদিত। এখন গল্পের মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু এটাই সত্যি। এর পরেও প্রশ্ন জাগে, চতুর্দিকের এই বিরূপতা, অসহযোগিতা, লুকোনো ঘৃণা, অপমানজনক চক্রান্ত সত্ত্বেও নিবেদিতা তাঁর কোন মাধুর্য, কোন সৌন্দর্যকে দৃপ্ত পদক্ষেপে ধূলিধূসরিত পথে পথে বয়ে নিয়ে নির্ভীক ভাবে চলতেন? এর উত্তরে মহান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের একটি আলাপচারিতার উল্লেখই যথেষ্ট। এক বর্ণময় বর্ণনায় নিবেদিতার বাহ্যিক ও অন্তঃস্থিত রূপকে তিনি ছবির মতো এঁকে দিয়েছেন। হ্যারিংটন স্ট্রিটে মার্কিন কনসুলেটে একটি সান্ধ্য আসরে আমন্ত্রিতদের মধ্যে নিবেদিতাও একজন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে নিবেদিতা, “সন্ধে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপালিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে কি বলব, যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল।... ‘সুন্দরী সুন্দরী’ কাকে বল তোমরা, জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা— সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল। ...সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থিরমূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা বললে মনে বল পাওয়া যেত। ...নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দু’টি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।”
প্রথমে ঠিক হয়েছিল, বোসপাড়া লেনের যে বাড়িতে মা ঠাকুরানি থাকেন, সেখানেই হবে নিবেদিতার আশ্রয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় বাধা দিল তখনকার কলকাতার গোঁড়ামি। ব্রাহ্মণী সারদার সঙ্গে একই বাড়িতে নিবেদিতা! এ তো জাতধর্মের উপরে আঘাত শুধু নয়, সরাসরি সমাজবিরোধিতা! অথচ এই সমাজরক্ষকরা হয়তো জেনেও জানতেন না, এই বিদেশিনীকে সারদা দেবী নিজের মেয়ের মতো দেখেন, তাঁকে ‘আদরের খুকি’ বলে ডাকেন। শত ইচ্ছে থাকলেও নিবেদিতা বুঝতে পারছিলেন, বাধার পরিমাণ বিপুল। তা ছাড়া তিনি ভারতে এসেছেন নারীশিক্ষা বিষয়ে স্বামীজির স্বপ্নকে সাকার করে তুলতে। একটি ছোট বিদ্যালয় করতে হলেও তাঁকে অন্য বাড়ির সন্ধান করতে হবে। রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে আর একটি বাড়ি খোঁজার চেষ্টায় বিবেকানন্দের অনুরাগীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সমগ্র হৃদয় দিয়ে নিবেদিতা অনুভব করতেন, অজ্ঞ ও শিক্ষাশূন্য নারীজাতিকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলাই হবে তাঁর কর্মপ্রবাহের সূচনা। অনেক চেষ্টার পরে পাওয়া গেল বোসপাড়া লেনেই একটি বাড়ি। মা সারদার বাড়ির প্রায় উল্টো দিকে। ঠিকানা ১৬ নম্বর। বিরাট কোনও প্রাসাদ বা প্রাসাদোপম বাড়ি নয়। নিতান্তই মধ্যবিত্তের বাড়ি। দোতলায় শোওয়ার ঘর। পাঁচ ধাপওয়ালা সিঁড়ি। একতলায় দু’দিকে দু’টি ঘর। খিড়কি দুয়ার, মাঝখানে একটি ছোট উঠোন। বাগবাজারের জীবনযাত্রা ও এই সামান্য হতশ্রী বাড়িটিকে ভালবেসে ফেলেছিলেন নিবেদিতা। বাগবাজারও এর পরে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর আন্তরিকতা, ভালবাসা, নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম আর দীপ্র ব্যক্তিত্বকে। ১৬ নম্বর বাড়ির প্রতি তাঁর মমতার কথা নিবেদিতা লিখেছেন একটি পত্রে, “আমার বাড়িতে একটি আঙিনা আছে। ...বাড়ির মধ্যে এই জায়গাটি আমার আকাশ ও তারার সঙ্গে মিলনের স্থান। দিনের বেলা এখানে শীতল ছায়া বিছিয়ে থাকে, রাতে এটি হয়ে ওঠে অসীমের পূজামন্দির।”
বিবেকানন্দের আশীর্বাদ, অনুপ্রেরণায় নিবেদিতার স্কুল ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করল। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার থেকে ছাত্রী জোটানোই হয়ে উঠেছিল প্রধান অন্তরায়। স্বামীজি একটি সভা করে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের নিবেদিতা-পরিকল্পিত বিদ্যালয়ে পাঠানোর অনুরোধ জানালেন। গুরুভাইদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, “এরপর দেখবি নিবেদিতার কার্যকরী শক্তি। নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ। তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশঃ কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র। জানবি, এর কথা শুনে সবার তাক লেগে যাবে। নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসেনি।”
অবশেষে এল সেই মহালগ্ন। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর। রবিবার। সে দিন কালীপুজো। ১৬ নং বাড়িতে এলেন স্বয়ং শ্রীমা। এলেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ এবং আরও কেউ কেউ। প্রথাগত পূজাপাঠ সমাপন করে শ্রীমা সারদা মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন আশীর্বাণী, “আমি প্রার্থনা করি এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা আদর্শ কন্যা হয়ে উঠুক।” স্কুলের নাম নিবেদিতা দিলেন ‘রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস’। যদিও লোকমুখে প্রচলিত হল— সিস্টারের স্কুল। নিবেদিতার কাছে ‘ধ্রুবমন্দির’। দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে ১৮৯৯ সালে ১৬ নং বাড়ি নিবেদিতাকে ছেড়ে দিতে হল। অপর দিকে প্রাণঘাতী প্লেগরোগে আক্রান্ত কলকাতার সেবাকার্য ছেড়ে, স্বামীজির পরামর্শে টাকাপয়সার সংস্থান করার জন্য তিনি পাশ্চাত্যে চলে গেলেন। ফিরে আসার পরে (১৯০২) তিনি ভাড়া নিলেন ১৬ নম্বরের পিছনে অবস্থিত ১৭ নং বাড়ি। ১৯০৪-এ স্কুলের কাজ বেড়ে যাওয়ায় এবং পল্লির বিধবা এবং বাড়ির বধূদের জন্য ‘পুরস্ত্রী বিভাগ’ শুরু করার তাগিদে তাঁকে আবার ভাড়া নিতে হল ১৬ নম্বর বাড়ি। কিন্তু টাকার অভাব নিবেদিতার পিছু ছাড়েনি। অতএব পুনরায় ছেড়ে দিতে হল আদি বাড়িটি।
এই ১৬ ও ১৭ নম্বর বাড়িতে বাংলার বহু মনীষী এসেছেন কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, কখনও নিবেদিতার হিতব্রতের আকর্ষণে, কখনও বা তাঁর আমন্ত্রণে। আলো-বাতাসবিহীন এমন একটি বাড়িতে তাঁর মতো তেজস্বিনী মনীষা কী ভাবে বাস করছেন? তাঁরা শিউরে উঠেছেন। অনেকেই তাঁকে আরও ভাল কোনও স্থানে বসবাস করার জন্যে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কারও কথাই এই সাধিকা, আরাধিকা শোনেননি। নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন ‘আমার মেয়েদের’ ভাল-মন্দের গহনে, ওই দু’টি বাড়ির ভূগোলে, ইতিহাসে, মানুষ নির্মাণের (Man making) যজ্ঞে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রবন্ধ ‘ভগিনী নিবেদিতা’য় অকপটে লিখেছেন, “আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মূহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিনযাপন করিয়াছেন— ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই-সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যাভঙ্গ হয় নাই— তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।” তথ্যের দিক থেকে বলা যায়, এ দেশের মনীষীদের মধ্যে নিবেদিতাকে যাঁরা কাছ থেকে নিবিড় ভাবে দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। আর সম্ভবত প্রধানতম, রবীন্দ্রনাথেরই অন্তরঙ্গ সুহৃৎ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের শ্রদ্ধাময়, পুণ্য সম্পর্ক আর এক দীর্ঘ ইতিহাস।
প্রয়াত অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর শ্রমসাধ্য ও অপূর্ব বিশ্লেষণাত্মক মহাগ্রন্থ ‘নিবেদিতা লোকমাতা’য় নারীবজ্র নিবেদিতার সমগ্র চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছেন এক একটি শব্দবন্ধে। তাঁর বিশ্লেষণে নিবেদিতা “শিক্ষাতাত্ত্বিক ও শিক্ষাব্রতী, শিল্পতাত্ত্বিক, বিজ্ঞান-সহায়ক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, বাগ্মী, রাজনীতিক, ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা।” এর সঙ্গে আরও যুক্ত হতে পারে এই অভিধাগুলি— সাহিত্যস্রষ্টা, জাতীয়তাবাদী, সেবিকা, নিঃশঙ্ক চিত্ত, অনুবাদিকা, অসামান্য পত্রলেখিকা ইত্যাদি। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর তাঁর জীবৎকাল, অথচ প্রতিভা এমন অগণিত যে, তাঁকে ছোট একটি রচনায় চিত্রিত করা দুঃসাধ্য। সে প্রচেষ্টার জায়গাও এখানে নেই। নিবেদিতার এই বহুমুখী প্রতিভার একটি অপূর্ব ব্যাখ্যা আমরা পাই সমাজতাত্ত্বিক বিনয় সরকারের একটি মন্তব্যে— “নিবেদিতা মানবতাবাদী, সর্বক্ষেত্রে কর্মী— দেশাত্মবোধক কার্য, শিক্ষা, রাজনীতি, জাতীয়তা, শ্রমশিল্প, ইতিহাস, নৈতিক সংস্কার, সমাজকল্যাণ, নারী-উন্নয়ন, এবং কীসে নয়! বাংলার গৌরবময় বিপ্লবের কালে (১৯০৫-১০) তরুণ বাংলার কাছে তাঁর নাম যাদুমন্ত্রের তুল্য। কলকাতায় ঐকালে প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছোটবড় যে-কোনো মানুষের তিনি সহযোগী। বিবেকানন্দ আর কিছু না ক’রে যদি কেবল নিবেদিতাকে এনে ভারতীয় কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ক’রে দিতেন, তাহলেও তাঁর কর্মজীবন সফল ও যুগসৃষ্টিকারী, একথা বলা যেত। নিবেদিতা ভারতের জন্য বিবেকানন্দের অলৌকিক আবিষ্কার। নিবেদিতা ভারতীয় জনগণের জন্য মহাসম্পদ।” দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনালগ্নে নিবেদিতার ভূমিকা কত দূর বিস্তৃত ছিল, তার পরিমাপই আমরা করিনি। দেশাত্মবোধে পূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য তিনি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংশ্রব পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন (১৯০২)। যদিও আত্মিক যোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। ‘বজ্র’ চিহ্নকে তিনি বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতীক মনে করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে বজ্র উজ্জ্বলতম শক্তির উৎস, মুহূর্তের মধ্যে আত্মবলিদানে প্রস্তুত। বজ্র নিঃশঙ্ক, সতত আলোকময়। চেয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকায় যেন থাকে বজ্রচিহ্ন। এ কথা জোরের সঙ্গে বলার সময় এসেছে, আমরা নিবেদিতাকে যে ভাবে বিস্মৃত হয়েছি, তা বিস্ময়কর! বিবেকানন্দের সঙ্গে একই পঙ্ক্তিতে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়, তাঁকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষাক্ষেত্রে তো নয়ই, জীবনের অন্য কোনও অন্ধকার ঘোচানোর কাজেও স্মরণ করিনি। অথচ ভারত তাঁর কাছে ছিল মাতৃভূমিরও অধিক। আমরা ছিলাম তাঁর আত্মার আত্মীয়। ‘INDIA’ শব্দটিই তাঁর কাছে আদ্যন্ত মন্ত্রস্বরূপ। ‘ভারত’ তাঁর কাছে উপাস্য দেবতা। এ আমাদের দুর্ভাগ্য। তাঁর নামে একটা সরু গলি, কী পার্ক, কী সেতু, কী বিশ্ববিদ্যালয় বাইরের দিক থেকে মূল্যহীন আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এর বেশি কিছু নয়। নিজেদের জীবনচর্যায় আজও আমরা তাঁর বাণী ও আত্মত্যাগকে প্রয়োগ করার কোনও প্রচেষ্টা নিইনি। একমাত্র তাঁর রোপিত বিদ্যালয়টি নানা ঝড়-ঝাপটা সামলে আজ মহীরুহ। এই প্রতিষ্ঠান একশো কুড়ি বছরের উপরে নিবেদিতার নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করছে।
তাঁর প্রতি এই অপরিসীম উপেক্ষা নিবেদিতাকে কখনও স্পর্শ করবে না। আমরাই ছোট হতে হতে শূন্যে বিলীন হয়ে যাব। হয়তো অন্তিম মুহূর্তে হাহাকারের মতো মনে পড়বে, এক আলোকদূতীর হাতে অনির্বাণ আলো জ্বলে উঠেছিল, তা আমাদেরই শুভকামনায়! রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধে নিঃসংকোচে বলেছেন— “ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন; তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই— প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সেজন্য মানুষ যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল, যাহা একবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন— নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না— নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না— ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।” নিবেদিতার এই আত্মবলিদানকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিনি। স্পষ্টতই চলমান সময় বলছে, বজ্রে যাঁর বাঁশি বেজে উঠেছিল, হৃৎপদ্ম যিনি মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই নিবেদিতাকে যথাযোগ্য স্থান দিতে বড্ড দেরি করে ফেলেছে এই দেশ ও দেশের মানুষ। অথচ ভারতই ছিল তাঁর প্রাণভূমি।
স্বামীজির শেষ জীবনে, যখন তাঁর শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছে, নিবেদিতা ছায়ায় মতো তাঁর অনুগামী ছিলেন। ১৮৯৮ সালে স্বামীজি-সঙ্গের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় ধরা আছে নিবেদিতার ‘স্বামীজির সহিত হিমালয়ে’ গ্রন্থে। ওই বছরই স্বামীজির শেষবারের মতো হিমালয়ে যাওয়া। শৈবতীর্থ অমরনাথে শিবের কাছে স্বামীজি ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছিলেন। গুহা থেকে বেরিয়ে প্রিয় শিষ্যাকেই তিনি প্রথম সে কথা জানান। স্বামীজির মর্ত্যজীবনের এই পরম প্রার্থনাটির কথা জেনে বিস্মিত হন নিবেদিতা। আরও বিস্মিত হন স্বামীজি যখন বলেন, তাঁর এ বার হিমালয়ে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য শিবসুন্দরের কাছেই নিবেদিতাকে উৎসর্গ করা তাঁর জীবনব্রত উদ্যাপনের জন্য। আমরা জানি, হিমালয় তীর্থে সেই দুটি প্রার্থনাই পূরণ হয়েছিল বিবেকানন্দ ও তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতার জীবনে।
১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজির সেই প্রথম ইচ্ছাপূরণের দিনটি এল। সে দিন শুক্রবার। বেলুড় মঠে সন্ধ্যায় মন্দিরের প্রার্থনার সময় স্বামীজি তাঁর নিজের ঘরে ধ্যানাসনে বসে রাত ৯টায় শান্তভাবে মহাসমাধি লাভ করেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যকান্তি মুখমণ্ডল দেখে প্রথমে কেউ বুঝতেই পারেননি যে, এ স্বামীজির অমৃতধামযাত্রা তথা দু’বছর আগে হিমালয়তীর্থ অমরনাথধামে তুষারলিঙ্গ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁর ইচ্ছামৃত্যু প্রার্থনার ‘প্র্যাক্টিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন’। কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য হলেও তাঁর জীবনব্রত উদ্যাপনের জন্য যাঁদের রেখে গেলেন, এর পর তাঁদের কী হবে বা হল? এ বার সে কথাই।
পরদিন ৫ই জুলাই, শনিবার। তখন ভগিনী নিবেদিতার ঠিকানা ১৬ নন্বর বাগবাজার লেন। সকাল ৯টা নাগাদ বেলুড় মঠ থেকে একটা ছোট চিঠি পান স্বামী সারদানন্দজি স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বয়ানে,
"মাই ডিয়ার নিবেদিতা, দ্য এন্ড হ্যাজ কাম, স্বামীজি হ্যাজ স্লেপ্ট লাস্ট নাইট অ্যাট নাইন ও’ক্লক। নেভার টু রাইজ এগেন সারদানন্দ।"
চিঠির অক্ষরগুলি যেন চোখের সামনে কেঁপেছিল নিবেদিতার, সঙ্গে শরীরটাও। ঘরে উপস্থিত নিবেদিতার সেবিকাও কেঁদে উঠেছিলেন। মাত্র দু’দিন আগেই তো নিবেদিতা বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন স্বামীজিরই নিমন্ত্রণে। স্বামীজি তাঁদের খাইয়েছিলেন পরম যত্নে এবং আহার শেষে স্বামীজি অতিথিদের হাতে জল ঢেলে দিয়েছিলেন হাত ধোওয়ার জন্য। নিবেদিতা সঙ্কুচিত হয়েছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন, “যিশু তো শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।” কিন্তু সে তো শেষের দিনে। তখন নিবেদিতা ভাবতেও পারেননি, তাঁর গুরুর ক্ষেত্রেও এই কথাটা আক্ষরিক অর্থেই মিলে যাবে।
স্বামীজি কিন্তু অমরনাথে নিবেদিতাকে আভাস দিয়েই রেখেছিলেন, মহাদেব-কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছেন। যার নিহিত অর্থ হল, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হলে তাঁর দেহত্যাগ হবে না। স্বামীজির মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত আনুপূর্বিক সব কথা শুনে নিবেদিতার সে-সব কথাই মনে পড়েছিল। এক দিকে নিবেদিতার শোকস্তব্ধ উদ্গত নয়নের অশ্রুধারা, আর এক দিকে এই সব স্মৃতি। নিবেদিতা আর কালবিলম্ব না করেই বেলুড় থেকে আসা পত্রবাহকের সঙ্গেই রওনা হয়ে যান বেলুড় মঠ অভিমুখে। ইতিমধ্যে স্বামীজির প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল সারা শহরে। সবাই ছুটেছিল সেই বেলুড়ের দিকে। বেলুড় মঠে পৌঁছেই নিবেদিতা সোজা উঠে গিয়েছিলেন দোতলায় স্বামীজির ঘরের দিকে। ঘরে তখন বেশি লোকজন নেই। স্বামীজির দেহটি মেঝেতে শায়িত ছিল হলুদ রঙের ফুলমালা আচ্ছাদিত হয়ে। মানসকন্যা স্বামীজির শিয়রের কাছে বসে পড়েন। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা, মুখে কোনও কথা নেই। আবেগ-আকুল কম্পিত হাতে তুলে নেন গতপ্রাণ স্বামীজির মাথাটি। তখন আর তিনি কন্যা নন, তিনি মাতা! স্বামীজির তাঁর প্রতি আশীর্বচনের সার্থক রূপ একাধারে তিনি সেবিকা ও মাতা। যেন মায়ের মতোই প্রিয়বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হয়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দর শিবরূপী গুরুর সেবা করতে থাকেন ছোট একটি পাখা হাতে। এর পর সেই মহাযাত্রার পালা। একে একে সন্ন্যাসী-ভাইরা এসে স্বামীজির দেহটি নীচে নামিয়ে আনেন। আরতি ও প্রণাম-শেষে পা দু’টি অলক্তরাগে রঞ্জিত করেন ও মস্তক অবলুণ্ঠিত করে প্রণাম করেন। গুরুভাইরা শ্রীপাদপদ্মের ছাপ নেন। নিবেদিতাও অশ্রুসিক্ত নয়নে পা দুটি ধুয়ে একটি পরিষ্কার রেশমি রুমালে তাঁর গুরুর পদচিহ্ন গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী ও সমবেত জনতার সঙ্গে নিবেদিতাও চলেন পায়ে পায়ে সেই গতপ্রাণ বিজয়ী বীরের দেহটি নিয়ে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে। স্বামীজির শেষকৃত্য সমাপনের নির্দিষ্ট স্থানে, যে স্থান বিবেকানন্দ নিজেই চিহ্নিত করেছিলেন মহাপ্রয়াণের কিছু দিন আগে, তাঁর প্রিয় বেলগাছের কাছে অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গায়।
দেহটি নামানো হলে নিবেদিতা সেই গাছেরই একটু দূরে এসে বসে পড়েন। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করেন প্রথমে নিবেদিতা ও পরে একে একে গুরুভাই ও অন্যান্য সন্ন্যাসী-ভাইয়েরা। প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সামনে বিবেকানন্দের প্রিয় ‘জি.সি’ অর্থাৎ নাট্যকার ও মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিলাপ, “নরেন, তুমি তো ঠাকুরের ছেলে, ঠাকুরের কোলে গিয়ে উঠলে। আর আমি বুড়ো মানুষ, কোথায় তোমার আগে যাব, তা না হয়ে আজ আমাকে দেখতে হচ্ছে তোমার এই দৃশ্য !” এ কথা শোনামাত্র নিবেদিতা শোক চেপে রাখতে না পেরে দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজির প্রজ্বলিত চিতাগ্নির পাশে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এ দৃশ্যে বিচলিত স্বামী ব্রহ্মানন্দজি স্বামীজির শিষ্য নিশ্চলানন্দকে নিবেদিতাকে চিতাগ্নির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে বলেন। সেই অনুযায়ী নিশ্চলানন্দ রোরুদ্যমানা নিবেদিতাকে সেখান থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে, নানা সান্ত্বনাবাক্যে ভোলাতে লাগলেন।
সারা অঙ্গ চন্দনচর্চিত মনুষ্যদেহে তাঁর শিবরূপী গুরুর ধূপধুনো-গুগগুল সুবাসিত চিতাগ্নি তথা হোমাগ্নি নিবেদিতার অনর্গল নয়নধারায় বুঝি নির্বাপিত করতে চান। সেই হৃদয় হাহাকার করা মুহূর্তে সহসা গুরুর এক অলৌকিক স্নেহস্পর্শ নিবেদিতাকে চমকিত করে।
চিতাগ্নি থেকে একখণ্ড গেরুয়া বস্ত্র হাওয়ায় উড়ে এসে নিবেদিতার কোলে গিয়ে পড়ে। পরম মমতায় ও যত্নে নিবেদিতা তা গুরুর আশীর্বাদ ভেবে মাথায় ঠেকান। সেই পবিত্র স্পর্শ যেন শোকস্তব্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনা ও শক্তি জোগায়। তবু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন “পরের জন্য নিজেকে যিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকেও কেন ছেড়ে দিতে হয় আমাদের? হে ভগবান, কেন?”
এরপর নিবেদিতার বাকি জীবন যেন অগ্নিশিখাই। মানবসেবার পুণ্যব্রতে। ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে নিবেদিতার সংগ্রাম আর এক ইতিহাস। তার সবটুকুই গুরু বিবেকানন্দের দেখানো পথে।
নিবেদিতা হয়তো পাশ্চাত্যের প্রায়শ্চিত্ত। যে পশ্চিম বারে বারে দূত পাঠিয়েছে, যে দূত মনে করেছে ভারতের সবটা কেবল অন্ধকার আর কুসংস্কারে ঠাসা, তাকে নিজ ধর্মে স্নান করিয়ে সভ্য করানো তার মহান দায়িত্ব, যাকে বলে হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন, সেই তাদেরই ভূমি থেকে উঠে এসে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে রুখে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। নিজের তেজ দিয়ে আগলে রাখলেন ভারতের ঐতিহ্যকে, তার ধর্মকর্ম এবং সংস্কারকে। কালীপূজার বহু বিতর্কিত সাধনপদ্ধতির মধ্যে যে প্রকৃতি-অর্চনার বজ্রকঠিন অধ্যায় আছে, তাকে নমস্কার জানালেন। বললেন, ঈশ্বর শুভ ও অশুভ উভয়েই সমান ভাবে বিরাজ করেন। মহাকালীর যে করাল রূপ আমরা দেখি তা মিথ্যা মায়া, মরীচিকা, বিভ্রম। ওই রূপ দেখে যারা ‘না না’ বলে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যায়, তারা অভাগা। তারা কালীর কোলে বসে কালীর মিঠে কথা শুনতে পায় না। যা তিনি দেখান, তা তিনি নন। ওই ভয়ংকর, ওই অমানিশা, ওই ত্রাস পেরিয়ে তবেই নিত্যানন্দময়ী কালীকে পেতে হয়। শক্তিপূজায় এ ভাবেই শক্তি মেলে। হ্যাঁ, এ পুজোর আশেপাশে অনেক শয়তানি জড়ো হয়েছে সত্যি। কিন্তু সে সব আগাছার ভয়ে কি আমরা নন্দনকাননটিকে ত্যাগ করতে পারি?
কালাপানির ও পার থেকে এক অচ্ছুৎ এসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে কালী নিয়ে এমন আবেগ ভরে কথা বলছে। কালীর চর্চা করছে। রক্ষণশীল সমাজে কী তুমুল ঝড়ই না উঠল। কেউ আবার চোখের জল ফেলে ধন্য ধন্য করে উঠল, এই মেয়ে তো দেখি ঈশ্বরের কথা পৃথিবীকে বলার জন্যই জন্মেছে। সেই সব শংসা-নিন্দার লেশমাত্র তাঁর জ্যোতির্বলয়ে প্রবেশই করতে পারল না। কারণ তিনি তখন কালীকে মেনেছেন, কারণ তাঁকে পেয়ে গিয়েছেন। কালীর সকল সন্তানদের ভালবাসাও সেই মায়ের সঙ্গে খেলারই অঙ্গ। তাঁর যাপন জুড়ে থাকেন মৃত্যুরূপা কালভৈরবী। বাগবাজারের ভাড়াবাড়ির উনুনের মতো গরম এক চিলতে ঘরে যখন দগ্ধে দগ্ধে চরম পরিশ্রম করেন, তখন ঈশান কোণে কালবৈশাখীর মেঘের আভাস দেখলে সব যাতনা ভুলে উঠে দাঁড়ান তিনি। ‘ওই তো! কালী! কালী!’ গরিব ঘরের অপুষ্ট দুধের শিশু তাঁর সামনে শেষ নিঃশ্বাস ফেললে, তার শোকাকুল মাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, বলেন, ‘চুপ করো। তোমার মেয়ে এখন কালীর কাছে!’ শ্রীশ্রীমাকে আনিয়ে নিজের বড় সাধের স্কুলের ভিতপাথর স্থাপনা করেন তিথি দেখে অমাবস্যায়, ঠিক সেই কালীপুজোরই দিনে। ‘আহা, এখানে পড়ে আমার মেয়েরা যেন জগন্মাতার আশীর্বাদটুকু পায়’— রুদ্রাক্ষ চেপে ধরে প্রার্থনা করেন সিস্টার।
আর কালীর পায়ে আত্মোৎসর্গের তত্ত্বকে সত্যি করে একটু একটু করে নিংড়ে দেন নিজের রক্ত। তাঁর কালীর জন্য। কালীর সন্তানদের জন্য। সকালে স্কুল চালান, দুপুরে খর রোদে ছাতা হাতে ছাত্রী খুঁজতে বের হন, বিকেলে মুখের ফেনা তুলে খাটেন রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে। অতীত খুঁড়ে আবার যে ফিরিয়ে আনতে হবে ভারত সংস্কৃতির হীরের যুগ। সন্ধেয় বিপ্লবীদের শেখান স্বাধীনতার মানে। তার পর, রাত জেগে বই লেখেন। পর দিন কাকভোরে উঠে রাস্তা ঝাঁট দিয়ে প্লেগের ব্যাধি তাড়াতে ছোটেন। অক্লান্ত কর্মযোগে তিলে তিলে শেষ হতে হতে সময়ের অনেক আগে নিবেদিতা আশ্রয় নেন বরফের কফিনে।
শক্তিপক্ষেই তাঁর পৃথিবীতে আসা। শক্তিপক্ষেই তাঁর চিরতরে চলে যাওয়া। আমরা শুধু পড়তে পাই দার্জিলিঙের হিমেল শ্মশানভূমিতে তাঁর সমাধির ওপর লেখা কনকনে বাক্যগুলো-
"এখানে শান্তিতে শুয়ে আছেন তিনি, যিনি ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন— সিস্টার নিবেদিতা: ২৮ অক্টোবর ১৮৬৭-১৩ অক্টোবর ১৯১১।"
তাঁর সৎকারক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় লিপিটি মিশনের দান নয়। এটি স্থাপন করেছিলেন অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।
রক্তে আইরিশ, লোকমুখে ইংরেজ রমণী। বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর লন্ডনে আলাপ। বয়সে তখনও তরুণী। ওয়েস্ট এন্ডের এক বৈঠকখানায় বিবেকানন্দের একটি অভিভাষণ শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল তরুণীটির। সময় ১৮৯৫, নভেম্বর। তাঁর পোশাকি নাম মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। যে জীবন তিনি এত দিন খুঁজছিলেন, যে সন্ধানী মন নিয়ে তাঁর আকুলতা কোথাও শমিত হতে পারছিল না, বৃত্তিতে শিক্ষয়িত্রী এই মহৎপ্রাণ অন্বেষণ করছিলেন তাঁর পরিসর, তাঁর আত্মোৎসর্গের সঠিক জায়গা, বিবেকানন্দের ধারাবাহিক আলোচনা চক্রে উপস্থিত থেকে তিনি পেয়ে গেলেন সেই মহানভূমির ঠিকানা— ভারতবর্ষ।
২৩শে জুলাই, ১৮৯৭। আলমোড়া থেকে মিস নোব্লকে লিখছেন বিবেকানন্দ, ‘‘কাজ শুরু হয়ে গেছে এবং বর্তমানে দুর্ভিক্ষনিবারণই আমাদের কাছে প্রধান কর্তব্য। কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কাজ চলছে, দুর্ভিক্ষ-সেবা, প্রচার এবং সামান্য শিক্ষাদান।... তুমি এখানে না এসে ইংল্যান্ডে থেকেই আমাদের জন্য বেশি কাজ করতে পারবে।’’ ২৯শে জুলাইয়ের চিঠিতে আরও খোলাখুলি লিখলেন স্বামীজি, ‘‘এ দেশের দুঃখ, কুসংস্কার, দাসত্ব প্রভৃতি কী ধরনের, তা তুমি ধারণা করতে পারো না। এ দেশে এলে অর্ধ-উলঙ্গ অসংখ্য নর-নারীতে পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে। তাদের জাতি ও স্পর্শ সম্বন্ধে বিকট ধারণা... তা ছাড়া জলবায়ু অত্যন্ত গ্রীষ্মপ্রধান।... শহরের বাইরে কোথাও ইউরোপীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিছুমাত্র পাবার উপায় নেই।’’
ভারতবর্ষীয় বাস্তবের কঠোর ছবি তুলে ধরেও অবশ্য মিস নোব্লকে ইংল্যান্ডে আটকে রাখা গেল না। তিনি এ দেশে এলেন। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা অসুবিধেও টের পেলেন। ৩১শে জানুয়ারি ১৮৯৮। এরিক হ্যামন্ডকে তাঁর ভারতবাসের অভিজ্ঞতার কথা লিখছেন মিস মার্গারেট নোব্ল। সে চিঠিতে মিশেছে চকিত কৌতুক। পার্ক স্ট্রিটের যে বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে সে বাড়ির স্নানঘরটিই আয়ারল্যান্ডের মেমসাহেবের কৌতুকের কারণ। স্নানঘরে জলের একটি কল আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে টিনের মগে করে মাথায় জল ঢালতে হয়। এমন ধারা স্নানের অভিজ্ঞতা একেবারেই নতুন। কিছু দিন যেতে না যেতেই অবশ্য এই দেশের সব কিছুই বড় আপন বলে মনে হল। পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রার ফেলে আসা অভ্যেস ভুলে এই দেশটিকেই কর্মসূত্রে নিজের করে নিলেন। মিস নোব্ল হয়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। কিন্তু কী ভাবে? কোন মন্ত্রে?
বিবেকানন্দ যে কথাগুলি লিখেছিলেন তা সর্বৈব সত্য। এক জন শিক্ষিত ইউরোপীয়ের কাছে এ দেশের দুর্দশা বিরক্তিকর, কষ্টদায়ক। নিজেকে প্রত্যাহার করে নেওয়ার পক্ষে বাইরের এই প্রতিকূলতাই যথেষ্ট। তবু নিবেদিতা এই প্রতিকূলতা অতিক্রম করতে পেরেছিলেন তাঁর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে। অন্তর্দৃষ্টি বলতে কিন্তু অলৌকিক কিছু নয়। অন্তর্দৃষ্টি হল দেখার সেই চোখ যা অন্যের অবস্থানকে বুঝতে চায়, তাকে ‘অপর’ হিসেবে দূরে ঠেলে রাখতে চায় না। এই দৃষ্টি নিবেদিতা অর্জন করেছিলেন তাঁর ইতিহাসবোধ থেকেই। কোনও নতুন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অপরিচয়ের দূরত্ব মোচন করা যায় কী ভাবে? নিবেদিতা লিখছেন, ‘‘দ্য ফাউন্ডেশন-স্টোন অব আওয়ার নলেজ অব আ পিপল মাস্ট বি অ্যান আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব দেয়ার রিজিয়ন।’’ ভারতবর্ষের মানুষদের বুঝতে গেলে সে দেশের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য খেয়াল করতে হবে। এও বললেন যে, জানতে হবে সেখানকার মানুষদের শ্রমের প্রকৃতিটি ঠিক কী রকম।
নিবেদিতা তখনও এ দেশে আসেননি। বঙ্কিমচন্দ্র সাহেবি দৃষ্টি সম্বন্ধে ঠাট্টা করে লিখেছিলেন ‘‘বিলাতী বিদ্যার একটা লক্ষণ এই যে, তাঁহারা স্বদেশে যাহা দেখেন, মনে করেন বিদেশে ঠিক তাই আছে। তাঁহারা Moor ভিন্ন অগৌরবর্ণ কোন জাতি জানিতেন না, এ জন্য এ দেশে আসিয়া হিন্দুদিগকে Moor বলিতে লাগিলেন।’’ নিবেদিতা তো সাধারণ মেমসাহেব ছিলেন না, ভারতবর্ষকে চেনা ও চেনানোর সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। নিজের দেশে যা আছে অপর দেশেও তাই থাকবে এবং তা না-থাকলে মন্দ বলতে হবে এই সঙ্কীর্ণ আধিপত্যকামী দৃষ্টির অধিকারী কেবল পাশ্চাত্যের মানুষেরাই ছিলেন না, ভারতীয়রাও ছিলেন। ভারতীয়রা সাহেবদের মতো ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না বলে তাঁদের সঙ্কীর্ণতায় আধিপত্যবাদ ছিল না, তবে সাহেবমাত্রেই খারাপ এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল ছিল। সাহেব-মেমসাহেবদের যে বাঙালি-বাড়ির ত্রিসীমানায় যেতে দিতে নেই সে সংস্কার ছিল ষোলো আনা। নিবেদিতাকে সংস্কারমুক্ত মা সারদা তাঁর বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন। নিবেদিতা টের পেয়েছিলেন সারদা মায়ের পরিজনেরা এই উদার বাঙালিনীকে একঘরে করতে তৎপর। তিনি নিজেই অন্য বাড়িতে উঠে গেলেন।
বিবেকানন্দ যে ধর্ম-আন্দোলনের প্রবক্তা, সেই ধর্ম আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই ধারার মিলন। বিবেকানন্দ ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ নামের যে ধারাবাহিক নিবন্ধটি ‘উদ্বোধন’ পত্রে লিখেছিলেন, তাতে এই দুই সংস্কৃতির মিলনের কথা ছিল। দুই পক্ষেরই অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন— প্রাচ্যকেও চিনতে হবে পাশ্চাত্য সভ্যতার রীতি-নীতি, পাশ্চাত্যকেও বুঝতে হবে প্রাচ্যের গুরুত্ব। বিবেকানন্দের অনুগামী নিবেদিতার জীবন এই ব্রতেই স্থিতি লাভ করেছিল। ভারতবর্ষকে চেনাই ছিল তাঁর সাধনা, শুধু যে নিজে চিনছেন তা-ই নয়, তিনি ভারতবাসীদেরও তাঁদের দেশ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সচেতন করে দিচ্ছেন। পরাধীন ভারতীয়দের আত্মবিশ্বাস নেই। নিবেদিতা তাঁদের হারিয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে তৎপর। অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এঁদের সঙ্গে নিবেদিতার সখ্য গভীর। নিবেদিতার উৎসাহেই ভারতশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটল। ভারতীয় পুরাকথাকে, গুহাচিত্রের ঐশ্বর্যকে নিবেদিতার সাহচর্যে ভারতীয়রা পুনরাবিষ্কার করলেন। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করছিলেন ইংরেজিতে। নিবেদিতা তাঁর ইংরেজি পরিমার্জনা করে দেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাগাধুনিক উপাদান নিয়ে দীনেশচন্দ্রকে নানা প্রশ্ন করেন। এই প্রশ্নে দীনেশচন্দ্রের কাছে তাঁর নিজের দেশের সংস্কৃতি নতুন অর্থে উন্মোচিত হয়। নিবেদিতা লেখেন 'Cradle Tales of Hinduism'। সে বইতে আছে সতীর কাহিনি। সতীর কাছে পিতা দক্ষ শিবের নিন্দা করছেন। ‘‘থিফ, রাসকাল, ইভল, ডিজনেস্ট, ডটার-স্টিলার দ্যাট হি ইজ়!’’ দক্ষের তো অন্তর্দৃষ্টি নেই, তাই এ ভাবেই দেখেন তিনি শিবকে। সতী জানেন এ তো শিবের প্রকৃত রূপ নয়, দেখার চোখ না থাকলে সে রূপ অধরা থেকে যায়। শিবকে দেখার অন্তর্দৃষ্টি ছিল সতীর, যেমন ভারত সম্বন্ধে দেখার গভীর দৃষ্টির অধিকারিণী ছিলেন নিবেদিতা। তাঁর প্রয়াণের পর যে সংবেদী প্রয়াণলেখ রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাতে নিবেদিতাকে উপমিত করেছিলেন সতী হিসেবেই।
তা হলে কি এ দেশের অভাব নেই কিছুর? অন্তর্দৃষ্টিতে ভেতরের রূপ দেখেই মোহিত হয়ে থাকতে হবে? না, তা নয়। বিবেকানন্দ তাঁর পত্রে জানিয়েছিলেন নিবেদিতাকে সেবাকার্যের কথা, শিক্ষাব্রতের কথা, এ দেশের অভাবের কথা। নিবেদিতা এ দেশে এসে সে-দু’টি কাজই গ্রহণ করলেন, শিক্ষা আর সেবা এই দুই তাঁর ব্রত। সে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল কারণ অন্তর্দৃষ্টির অধিকারে তিনি এ দেশকে ভালবেসে ছিলেন। তাঁর ইস্কুলে যে পড়ুয়ারা আসে নিবেদিতা তাদের সম্বন্ধে নোট রাখেন। তাদের প্রবণতার ইচ্ছে-অনিচ্ছের খোঁজ নেওয়া চাই। তাঁর এ বাড়ির উঠোনে মাঝে মাঝে আসেন বাঙালি প্রতিবেশীরা। তাঁদের চেয়ারে বসতে দিয়ে মাটিতে বসে থাকেন নিবেদিতা। প্লেগ কলকাতায় মহামারির আকার নেয়। অক্লান্ত সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্বন্ধে দরিদ্র ভারতবাসীর অজ্ঞানতার শেষ নেই যেন। সেবাকার্যে দেশীয় যুবকদের সাহায্য নেন তিনি। বর্জ্যপদার্থ পরিষ্কার করেন যাঁরা, তাঁদের শারীরিক সামর্থ্য ও দেহসৌষ্ঠবে তিনি মুগ্ধ— এঁদের কিনা ভারতীয় সমাজের প্রান্তে ঠাঁই হয়! গোপালের মায়ের সেবা করেন একান্তে। গোপালের মা বালবিধবা, মা সারদার কাছে থাকেন। দু’জনে দু’জনের ভাষা বোঝেন না। তবু অন্তরের যোগ টের পাওয়া যায়। গোপালের মায়ের পায়ের কাছে বসে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দেন। এই বিধবার মধ্যে যেন খুঁজে পান নিজের ঠাকুমাকে। সারদা মায়ের বাড়িতে যান। সেখানে নিঃশব্দ বোঝাপড়ায় মেয়েরা ঠাকুরের পুজোর আয়োজন করছেন। তাঁদের এই সম্মিলিত পুজোর আয়োজনে কৌম সমাজের প্রাণ-স্পন্দন টের পান। এ ভাবেই প্রাত্যহিক ছোট ছোট কাজের মধ্যে এ দেশের সঙ্গে তাঁর আদান-প্রদান চলে। এই আদান-প্রদান চলে বলেই স্বামীজির প্রয়াণের পরেও এই দেশেই থেকে গেলেন তিনি। বিবেকানন্দ তাঁর পত্রে লিখেছিলেন নিবেদিতাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এ দেশকে নিজের মতো করে চিনেই নিবেদিতা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছিলেন। ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সীমার বাইরে যে দেশ, তাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন।
বিবেকানন্দ প্রথমে মার্গারেটকে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। নিদারুণ দারিদ্রপীড়িত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ইংরেজ শাসনের উৎপীড়নে রক্তাক্ত দেশটিতে এসে, অনালোকিত নারীদের মধ্যে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে দিতে চাওয়া উইম্বলডনের এই শিক্ষিকাকে প্রবল ভাবে হতাশ হতে হবে। পরিষ্কার ভাষায় একটি চিঠিতে মার্গারেটকে লিখলেন, “এ-দেশে যে কী দুঃখ, কী কুসংস্কার, কী দাসত্ব— সে তুমি কল্পনাতেও আনতে পারবে না। এ-দেশে এলে দেখবে, চারদিকে অর্ধনগ্ন অগণিত নর-নারী, — ‘জাতি’ ও স্পর্শ সম্বন্ধে তাদের উদ্ভট ধারণা, শ্বেতাঙ্গরা মনে করবে, তোমার মাথা খারাপ, তোমার প্রতিটি গতিবিধি তারা সন্দেহের চোখে দেখবে। তা ছাড়া দারুণ গরম। আমাদের শীতকাল অধিকাংশক্ষেত্রে তোমাদের গ্রীষ্মকালের মতো। দক্ষিণে তো সবসময় আগুনের হল্কা। শহরের বাইরে ইউরোপীয় সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই। ...এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস করো— স্বাগত তুমি, শতবার স্বাগত।”
স্বামীজির ওই ‘স্বাগত’ শব্দটিই মার্গারেটকে উদ্দীপিত করেছিল, ভারতের ভয়াবহ চরিত্রচিত্র নয়। নভেম্বর ১৮৯৫ থেকে তাঁর স্বপ্নযাত্রা ধরলে তা চূড়ান্ত হল জানুয়ারি ১৮৯৮-এ। ঠিক তিন বছর পরে মার্গারেট তখনকার বন্দর নগরী কলকাতার মাটিতে পা রাখলেন। কলকাতায় সে সময়ে শীতের আমেজ। শহরের কোনও ঘিঞ্জি অঞ্চলে নয়, আপাতত তখন তিনি থাকছেন চৌরঙ্গি অঞ্চলের একটি হোটেলে। ব্যবস্থাপনা অবশ্যই স্বামীজির। কোন হোটেল, তা এখনও জানা যায়নি। তবে যে জাহাজে মার্গারেট কলকাতায় এসেছিলেন, তার নাম ‘মোম্বাসা’। জানুয়ারির শেষ থেকে মার্চের একেবারে মাঝামাঝি সম্ভবত মার্গারেট কলকাতা ও চারপাশ ঘুরে দেখেছেন, তাঁর জীবনদেবতা বিবেকানন্দের অন্যান্য গুরুভ্রাতা ও অনুরাগীদের সান্নিধ্য লাভ করেছেন। সম্ভবত বলছি এই কারণে, ওই কয়েক মাসের মধ্যে লেখা নিবেদিতার কোনও চিঠি পাওয়া যায়নি। এর সম্ভাব্য কারণ, তখন মিস ম্যাকলাউড ও শ্রীমতী ওলি বুল ভারতে। বিবেকানন্দের বন্ধু ম্যাকলাউডকেই প্রাণ খুলে চিঠি লিখতেন মার্গারেট। সর্বাধিক পত্রপ্রাপিকার সঙ্গে তাঁর দেখাসাক্ষাৎ সে সময়ে যেখানে হাতের মুঠোয়, সেখানে পত্রপ্রেরণ অবান্তর। তবু এই পর্বে লেখা (১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮) একটি চিঠিতে সমসময়ের ইতিহাস খানিকটা চিত্রিত করেছেন মার্গারেট। প্রাপক তাঁর অন্যতম বন্ধু নেল হ্যামন্ডের স্ত্রী। তাঁকে লেখা সেই চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন, “...মঙ্গলবার স্বামীজির সাক্ষাৎ পেলাম। গতকাল তাঁর অতিথি হিসাবে পিকনিক করলাম সুন্দর এক নদীর তীরে (গঙ্গাতীরে), যে-জায়গাটি মিস মূলার মঠ তৈরির জন্য স্বামীজিকে কিনে দিচ্ছেন। জায়গাটা ঠিক উইম্বলডন কমনের কোন একটি অংশের মতোই— গাছপালাগুলোকে খুব খুঁটিয়ে নজর না করলে তফাৎ ধরা পড়ে না।...” এখানে বলে রাখা ভাল, অন্তরঙ্গ বন্ধু নেল হ্যামন্ডকেই পরবর্তী সময়ে লেখা একটি চিঠিতে অকপটে মার্গারেট লিখেছিলেন, “Oh, Nell, Nell, India is indeed a holy land.”
এ বছরের মার্চ মাসেই তাঁর জীবনের দু’টি অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল। ১৭ই মার্চ বাগবাজার পল্লির বোসপাড়া লেনের ১০/২ নং বাড়িতে তাঁর গুরুর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীমা সারদা দেবীর দর্শন লাভ করে তিনি ধন্য হলেন। সারদা দেবী তখনও প্রায় অবগুণ্ঠিতা, মৃদুভাষিণী, সর্বসাধারণের কাছে অপরিচিতা। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী শিষ্য ও গৃহী ভক্তরা তাঁর অপার মাতৃত্ব একটু একটু করে উপলব্ধি করছেন। বিকশিত হচ্ছে সারদার বিশ্বমাতৃকা শক্তি। অন্তরালে নির্মিত হচ্ছে তাঁর সর্বগ্রাহ্য, সর্বজনীন জননীর রূপপ্রতিমা। মা সারদার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিনটি মার্গারেটের ভাষায় ‘Day of days’। শ্রীমা সম্পর্কে তাঁর মনে হয়েছিল, “তিনি অনাড়ম্বর, সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।” সারা জীবন শ্রীমা সম্পর্কে এই পাবনীভাবনা তাঁকে প্রাণিত করেছিল। বলা যায়, নিবেদিতার অন্তরের নিভৃত কোণে জুঁইফুলের মতো বিরাজ করতেন সারদা, হৃদয়ে অমলিন শ্বেতপদ্মের মতো অধিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ, আর মননে-চিন্তনে, কর্মে বজ্রাগ্নির মতো প্রতিভাত হতেন বিবেকানন্দ।
মিস নোবলের জীবনে দ্বিতীয় এবং অভাবনীয় ঘটনার দিনটি এল ঠিক সাত দিন পরে অর্থাৎ ২৫শে মার্চ। ওই দিন মার্গারেটকে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে অবস্থিত অস্থায়ী বেলুড় মঠে স্বামীজি দীক্ষা দিলেন। বিবেকানন্দের স্নেহাশ্রয়ে ও আন্তরিক উপদেশে প্রাণিত মার্গারেট শিবপুজো করলেন। খুব সংক্ষিপ্ত পুজো, মন্ত্র, স্তোত্র। ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত বিদেশিনীর কাছে এই দিনও আর এক অভিধায় ভূষিত— ‘The day of Annunciation’। এই দিনটিতেই তো স্বর্গের দেবদূত যিশুজননী মেরিকে স্বপ্নে জানিয়েছিলেন— তোমার গর্ভে ঈশ্বর জন্মলাভ করবেন! দীক্ষার অন্তে মার্গারেটের হৃদয়ের ‘রাজা’ বিবেকানন্দ প্রত্যয়ের সঙ্গে তাঁর নতুন নাম রাখলেন— নিবেদিতা। মার্গারেট রূপান্তরিত, নিবেদিত হলেন, লাভ করলেন নবজন্ম। এখানে বলা যেতেই পারে, ১৮৯৮ সালের প্রেক্ষাপটে ‘নিবেদিতা’ নামটি ভীষণ ভাবে আধুনিক। ‘ডেডিকেশন’ যাঁর রক্তস্রোতে নিয়ত প্রবাহিত, তাঁকে এ ছাড়া আর কোন নামেই বা চিহ্নিত করা সম্ভব? তখনকার দিনে নারীদের নাম যেন পুরাণকল্পের সম্ভার কিংবা ছন্দের পারম্পর্য। তার চেয়েও বিপজ্জনক, চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন নামাবলি— তাতে না আছে সম্মান, না আছে মর্যাদা। এই সব ক’টি দিক বিচার করলে ‘নিবেদিতা’ নামটি অবিকল্প। কেননা স্বামীজি মর্মে মর্মে জানতেন, তাঁর এই মানসকন্যাটি সর্ব অর্থেই ‘আত্মাহুতির সমিধ’।
যাজকদের মতো প্রায় পা অবধি ঢাকা শ্বেতশুভ্র গাউন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কোমরে দড়ির মতো পাকানো রিবন, মাথায় লম্বা চুল— তবে এলায়িত নয়, খোঁপার আকারে পিছনে বেঁধে রাখা চুলের গুচ্ছ। সমস্ত দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে সকালবেলার রৌদ্রদীপ্ত আলো। মুখ বিরক্তিহীন, জগৎ ও পারিপার্শ্বিকের প্রতি প্রসন্নতায় পূর্ণ। বৈরাগ্যের প্রতীক গৈরিক বসন তিনি কখনও পরেননি। বরং ব্রহ্মচর্যের নিষ্কলুষ পোশাককে সারা জীবনে মহত্তর করেছেন। পুরুষদের দেউড়ি থেকে মহিলামহল পর্যন্ত আলোচনার কেন্দ্রস্থলে তিনি। সমস্ত ঔৎসুক্যের নির্যাস প্রচারিত হতে সময় লাগল না। সংস্কারে আচ্ছন্ন উত্তর কলকাতার বোসপাড়া অঞ্চলের মানুষ জেনে গেল, এই বিদেশিনী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা বা সিস্টার নিবেদিতা। হিন্দু ধর্মের ‘টলারেন্স’ ও ‘অ্যাকসেপ্ট্যান্স’-এর চিরসত্যকে যিনি আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা দিয়ে এসেছেন, এই তরুণীকে তিনিই নিয়ে এসেছেন এ দেশের সেবাব্রত সম্পাদনের জন্যে। তাঁরা এও জানলেন, এঁর ভিতরে তিনি জাগিয়ে তুলেছেন এক মহীয়সী সত্তা, যে সত্তার কাছে সিমলার নরেন দত্তের আহ্বান— “জগৎকে আলো দেবে কে? আত্মবিসর্জনই ছিল অতীতের ধারা; হায়! যুগ যুগ ধরে তা চলতে থাকবে! পৃথিবীর যারা বীরোত্তম ও সর্বোত্তম, তাদের আত্মোৎসর্গ করতে হবে ‘বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।’ ...নিঃস্বার্থ, অগ্নিজলন্ত প্রেম যাঁদের মধ্যে— তাঁদের এখন জগৎ চায়। সেই প্রেম প্রতিটি উচ্চারিত শব্দকে বজ্র করে তুলবে।”
এত দূর জানার পরেও পল্লিসমাজের ভ্রুকুঞ্চন থেকেই গেল। কেননা এই নারী যে বিধর্মী, ম্লেচ্ছ, বিদেশ থেকে এসেছেন! এঁর ছোঁয়াছুঁয়িতে জাত রাখাই যে বড় দায়! রেনেসাঁস ঋদ্ধ কলকাতা তখনও এই ঘন অন্ধকারে আচ্ছাদিত। এখন গল্পের মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু এটাই সত্যি। এর পরেও প্রশ্ন জাগে, চতুর্দিকের এই বিরূপতা, অসহযোগিতা, লুকোনো ঘৃণা, অপমানজনক চক্রান্ত সত্ত্বেও নিবেদিতা তাঁর কোন মাধুর্য, কোন সৌন্দর্যকে দৃপ্ত পদক্ষেপে ধূলিধূসরিত পথে পথে বয়ে নিয়ে নির্ভীক ভাবে চলতেন? এর উত্তরে মহান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথের একটি আলাপচারিতার উল্লেখই যথেষ্ট। এক বর্ণময় বর্ণনায় নিবেদিতার বাহ্যিক ও অন্তঃস্থিত রূপকে তিনি ছবির মতো এঁকে দিয়েছেন। হ্যারিংটন স্ট্রিটে মার্কিন কনসুলেটে একটি সান্ধ্য আসরে আমন্ত্রিতদের মধ্যে নিবেদিতাও একজন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের তুলিতে নিবেদিতা, “সন্ধে হয়ে এল, এমন সময় নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রূপালিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে কি বলব, যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল।... ‘সুন্দরী সুন্দরী’ কাকে বল তোমরা, জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা— সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল। ...সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থিরমূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা বললে মনে বল পাওয়া যেত। ...নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দু’টি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।”
প্রথমে ঠিক হয়েছিল, বোসপাড়া লেনের যে বাড়িতে মা ঠাকুরানি থাকেন, সেখানেই হবে নিবেদিতার আশ্রয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টায় বাধা দিল তখনকার কলকাতার গোঁড়ামি। ব্রাহ্মণী সারদার সঙ্গে একই বাড়িতে নিবেদিতা! এ তো জাতধর্মের উপরে আঘাত শুধু নয়, সরাসরি সমাজবিরোধিতা! অথচ এই সমাজরক্ষকরা হয়তো জেনেও জানতেন না, এই বিদেশিনীকে সারদা দেবী নিজের মেয়ের মতো দেখেন, তাঁকে ‘আদরের খুকি’ বলে ডাকেন। শত ইচ্ছে থাকলেও নিবেদিতা বুঝতে পারছিলেন, বাধার পরিমাণ বিপুল। তা ছাড়া তিনি ভারতে এসেছেন নারীশিক্ষা বিষয়ে স্বামীজির স্বপ্নকে সাকার করে তুলতে। একটি ছোট বিদ্যালয় করতে হলেও তাঁকে অন্য বাড়ির সন্ধান করতে হবে। রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতাকে উপেক্ষা করে আর একটি বাড়ি খোঁজার চেষ্টায় বিবেকানন্দের অনুরাগীরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সমগ্র হৃদয় দিয়ে নিবেদিতা অনুভব করতেন, অজ্ঞ ও শিক্ষাশূন্য নারীজাতিকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলাই হবে তাঁর কর্মপ্রবাহের সূচনা। অনেক চেষ্টার পরে পাওয়া গেল বোসপাড়া লেনেই একটি বাড়ি। মা সারদার বাড়ির প্রায় উল্টো দিকে। ঠিকানা ১৬ নম্বর। বিরাট কোনও প্রাসাদ বা প্রাসাদোপম বাড়ি নয়। নিতান্তই মধ্যবিত্তের বাড়ি। দোতলায় শোওয়ার ঘর। পাঁচ ধাপওয়ালা সিঁড়ি। একতলায় দু’দিকে দু’টি ঘর। খিড়কি দুয়ার, মাঝখানে একটি ছোট উঠোন। বাগবাজারের জীবনযাত্রা ও এই সামান্য হতশ্রী বাড়িটিকে ভালবেসে ফেলেছিলেন নিবেদিতা। বাগবাজারও এর পরে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর আন্তরিকতা, ভালবাসা, নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম আর দীপ্র ব্যক্তিত্বকে। ১৬ নম্বর বাড়ির প্রতি তাঁর মমতার কথা নিবেদিতা লিখেছেন একটি পত্রে, “আমার বাড়িতে একটি আঙিনা আছে। ...বাড়ির মধ্যে এই জায়গাটি আমার আকাশ ও তারার সঙ্গে মিলনের স্থান। দিনের বেলা এখানে শীতল ছায়া বিছিয়ে থাকে, রাতে এটি হয়ে ওঠে অসীমের পূজামন্দির।”
বিবেকানন্দের আশীর্বাদ, অনুপ্রেরণায় নিবেদিতার স্কুল ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করল। রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার থেকে ছাত্রী জোটানোই হয়ে উঠেছিল প্রধান অন্তরায়। স্বামীজি একটি সভা করে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও অনুরাগীদের নিবেদিতা-পরিকল্পিত বিদ্যালয়ে পাঠানোর অনুরোধ জানালেন। গুরুভাইদের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, “এরপর দেখবি নিবেদিতার কার্যকরী শক্তি। নিবেদিতার প্রাণ অতি মহৎ। তার ভেতর কোথাও প্রতিষ্ঠা, যশঃ কি মুরুব্বিয়ানা নেই। তার হৃদয় অতি উদার, পবিত্র। জানবি, এর কথা শুনে সবার তাক লেগে যাবে। নিবেদিতা প্রাণ দিতে এসেছে, গুরুগিরি করতে আসেনি।”
অবশেষে এল সেই মহালগ্ন। ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর। রবিবার। সে দিন কালীপুজো। ১৬ নং বাড়িতে এলেন স্বয়ং শ্রীমা। এলেন বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ এবং আরও কেউ কেউ। প্রথাগত পূজাপাঠ সমাপন করে শ্রীমা সারদা মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন আশীর্বাণী, “আমি প্রার্থনা করি এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হোক। এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা আদর্শ কন্যা হয়ে উঠুক।” স্কুলের নাম নিবেদিতা দিলেন ‘রামকৃষ্ণ স্কুল ফর গার্লস’। যদিও লোকমুখে প্রচলিত হল— সিস্টারের স্কুল। নিবেদিতার কাছে ‘ধ্রুবমন্দির’। দুঃখের বিষয়, অর্থাভাবে ১৮৯৯ সালে ১৬ নং বাড়ি নিবেদিতাকে ছেড়ে দিতে হল। অপর দিকে প্রাণঘাতী প্লেগরোগে আক্রান্ত কলকাতার সেবাকার্য ছেড়ে, স্বামীজির পরামর্শে টাকাপয়সার সংস্থান করার জন্য তিনি পাশ্চাত্যে চলে গেলেন। ফিরে আসার পরে (১৯০২) তিনি ভাড়া নিলেন ১৬ নম্বরের পিছনে অবস্থিত ১৭ নং বাড়ি। ১৯০৪-এ স্কুলের কাজ বেড়ে যাওয়ায় এবং পল্লির বিধবা এবং বাড়ির বধূদের জন্য ‘পুরস্ত্রী বিভাগ’ শুরু করার তাগিদে তাঁকে আবার ভাড়া নিতে হল ১৬ নম্বর বাড়ি। কিন্তু টাকার অভাব নিবেদিতার পিছু ছাড়েনি। অতএব পুনরায় ছেড়ে দিতে হল আদি বাড়িটি।
এই ১৬ ও ১৭ নম্বর বাড়িতে বাংলার বহু মনীষী এসেছেন কখনও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, কখনও নিবেদিতার হিতব্রতের আকর্ষণে, কখনও বা তাঁর আমন্ত্রণে। আলো-বাতাসবিহীন এমন একটি বাড়িতে তাঁর মতো তেজস্বিনী মনীষা কী ভাবে বাস করছেন? তাঁরা শিউরে উঠেছেন। অনেকেই তাঁকে আরও ভাল কোনও স্থানে বসবাস করার জন্যে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কারও কথাই এই সাধিকা, আরাধিকা শোনেননি। নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন ‘আমার মেয়েদের’ ভাল-মন্দের গহনে, ওই দু’টি বাড়ির ভূগোলে, ইতিহাসে, মানুষ নির্মাণের (Man making) যজ্ঞে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রবন্ধ ‘ভগিনী নিবেদিতা’য় অকপটে লিখেছেন, “আশৈশব তাঁহার সমস্ত সংস্কার ও অভ্যাসকে মূহূর্তে মুহূর্তে পীড়িত করিয়া তিনি প্রফুল্লচিত্তে দিনযাপন করিয়াছেন— ইহা যে সম্ভব হইয়াছে এবং এই-সমস্ত স্বীকার করিয়াও শেষ পর্যন্ত তাঁহার তপস্যাভঙ্গ হয় নাই— তাহার একমাত্র কারণ, ভারতবর্ষের মঙ্গলের প্রতি তাহার প্রীতি একান্ত সত্য ছিল, তাহা মোহ ছিল না। মানুষের মধ্যে যে শিব আছেন সেই শিবকেই এই সতী সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন।” তথ্যের দিক থেকে বলা যায়, এ দেশের মনীষীদের মধ্যে নিবেদিতাকে যাঁরা কাছ থেকে নিবিড় ভাবে দেখেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অন্যতম। আর সম্ভবত প্রধানতম, রবীন্দ্রনাথেরই অন্তরঙ্গ সুহৃৎ বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। নিবেদিতা ও জগদীশচন্দ্রের শ্রদ্ধাময়, পুণ্য সম্পর্ক আর এক দীর্ঘ ইতিহাস।
প্রয়াত অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তাঁর শ্রমসাধ্য ও অপূর্ব বিশ্লেষণাত্মক মহাগ্রন্থ ‘নিবেদিতা লোকমাতা’য় নারীবজ্র নিবেদিতার সমগ্র চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরেছেন এক একটি শব্দবন্ধে। তাঁর বিশ্লেষণে নিবেদিতা “শিক্ষাতাত্ত্বিক ও শিক্ষাব্রতী, শিল্পতাত্ত্বিক, বিজ্ঞান-সহায়ক, প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী, বাগ্মী, রাজনীতিক, ভারতীয় সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা।” এর সঙ্গে আরও যুক্ত হতে পারে এই অভিধাগুলি— সাহিত্যস্রষ্টা, জাতীয়তাবাদী, সেবিকা, নিঃশঙ্ক চিত্ত, অনুবাদিকা, অসামান্য পত্রলেখিকা ইত্যাদি। মাত্র চুয়াল্লিশ বছর তাঁর জীবৎকাল, অথচ প্রতিভা এমন অগণিত যে, তাঁকে ছোট একটি রচনায় চিত্রিত করা দুঃসাধ্য। সে প্রচেষ্টার জায়গাও এখানে নেই। নিবেদিতার এই বহুমুখী প্রতিভার একটি অপূর্ব ব্যাখ্যা আমরা পাই সমাজতাত্ত্বিক বিনয় সরকারের একটি মন্তব্যে— “নিবেদিতা মানবতাবাদী, সর্বক্ষেত্রে কর্মী— দেশাত্মবোধক কার্য, শিক্ষা, রাজনীতি, জাতীয়তা, শ্রমশিল্প, ইতিহাস, নৈতিক সংস্কার, সমাজকল্যাণ, নারী-উন্নয়ন, এবং কীসে নয়! বাংলার গৌরবময় বিপ্লবের কালে (১৯০৫-১০) তরুণ বাংলার কাছে তাঁর নাম যাদুমন্ত্রের তুল্য। কলকাতায় ঐকালে প্রতিটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছোটবড় যে-কোনো মানুষের তিনি সহযোগী। বিবেকানন্দ আর কিছু না ক’রে যদি কেবল নিবেদিতাকে এনে ভারতীয় কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ক’রে দিতেন, তাহলেও তাঁর কর্মজীবন সফল ও যুগসৃষ্টিকারী, একথা বলা যেত। নিবেদিতা ভারতের জন্য বিবেকানন্দের অলৌকিক আবিষ্কার। নিবেদিতা ভারতীয় জনগণের জন্য মহাসম্পদ।” দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনালগ্নে নিবেদিতার ভূমিকা কত দূর বিস্তৃত ছিল, তার পরিমাপই আমরা করিনি। দেশাত্মবোধে পূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য তিনি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় সংশ্রব পর্যন্ত ত্যাগ করেছিলেন (১৯০২)। যদিও আত্মিক যোগ কখনও ছিন্ন হয়নি। ‘বজ্র’ চিহ্নকে তিনি বিপ্লব-আন্দোলনের প্রতীক মনে করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে বজ্র উজ্জ্বলতম শক্তির উৎস, মুহূর্তের মধ্যে আত্মবলিদানে প্রস্তুত। বজ্র নিঃশঙ্ক, সতত আলোকময়। চেয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকায় যেন থাকে বজ্রচিহ্ন। এ কথা জোরের সঙ্গে বলার সময় এসেছে, আমরা নিবেদিতাকে যে ভাবে বিস্মৃত হয়েছি, তা বিস্ময়কর! বিবেকানন্দের সঙ্গে একই পঙ্ক্তিতে যাঁর নাম উচ্চারিত হয়, তাঁকে আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় শিক্ষাক্ষেত্রে তো নয়ই, জীবনের অন্য কোনও অন্ধকার ঘোচানোর কাজেও স্মরণ করিনি। অথচ ভারত তাঁর কাছে ছিল মাতৃভূমিরও অধিক। আমরা ছিলাম তাঁর আত্মার আত্মীয়। ‘INDIA’ শব্দটিই তাঁর কাছে আদ্যন্ত মন্ত্রস্বরূপ। ‘ভারত’ তাঁর কাছে উপাস্য দেবতা। এ আমাদের দুর্ভাগ্য। তাঁর নামে একটা সরু গলি, কী পার্ক, কী সেতু, কী বিশ্ববিদ্যালয় বাইরের দিক থেকে মূল্যহীন আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। এর বেশি কিছু নয়। নিজেদের জীবনচর্যায় আজও আমরা তাঁর বাণী ও আত্মত্যাগকে প্রয়োগ করার কোনও প্রচেষ্টা নিইনি। একমাত্র তাঁর রোপিত বিদ্যালয়টি নানা ঝড়-ঝাপটা সামলে আজ মহীরুহ। এই প্রতিষ্ঠান একশো কুড়ি বছরের উপরে নিবেদিতার নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষা করছে।
তাঁর প্রতি এই অপরিসীম উপেক্ষা নিবেদিতাকে কখনও স্পর্শ করবে না। আমরাই ছোট হতে হতে শূন্যে বিলীন হয়ে যাব। হয়তো অন্তিম মুহূর্তে হাহাকারের মতো মনে পড়বে, এক আলোকদূতীর হাতে অনির্বাণ আলো জ্বলে উঠেছিল, তা আমাদেরই শুভকামনায়! রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই বিখ্যাত প্রবন্ধে নিঃসংকোচে বলেছেন— “ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন তাহা অতি মহৎজীবন; তাঁহার দিক হইতে তিনি কিছুমাত্র ফাঁকি দেন নাই— প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তেই আপনার যাহা সকলের শ্রেষ্ঠ, আপনার যাহা মহত্তম, তাহাই তিনি দান করিয়াছেন, সেজন্য মানুষ যতপ্রকার কৃচ্ছ্রসাধন করিতে পারে সমস্তই তিনি স্বীকার করিয়াছেন। এই কেবল তাঁহার পণ ছিল, যাহা একবারে খাঁটি তাহাই তিনি দিবেন— নিজেকে তাহার সঙ্গে একটুও মিশাইবেন না— নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা, লাভলোকসান, খ্যাতিপ্রতিপত্তি কিছু না— ভয় না, সংকোচ না, আরাম না, বিশ্রাম না।” নিবেদিতার এই আত্মবলিদানকে আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিনি। স্পষ্টতই চলমান সময় বলছে, বজ্রে যাঁর বাঁশি বেজে উঠেছিল, হৃৎপদ্ম যিনি মানুষের কল্যাণে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই নিবেদিতাকে যথাযোগ্য স্থান দিতে বড্ড দেরি করে ফেলেছে এই দেশ ও দেশের মানুষ। অথচ ভারতই ছিল তাঁর প্রাণভূমি।
স্বামীজির শেষ জীবনে, যখন তাঁর শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়ছে, নিবেদিতা ছায়ায় মতো তাঁর অনুগামী ছিলেন। ১৮৯৮ সালে স্বামীজি-সঙ্গের কথা মর্মস্পর্শী ভাষায় ধরা আছে নিবেদিতার ‘স্বামীজির সহিত হিমালয়ে’ গ্রন্থে। ওই বছরই স্বামীজির শেষবারের মতো হিমালয়ে যাওয়া। শৈবতীর্থ অমরনাথে শিবের কাছে স্বামীজি ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছিলেন। গুহা থেকে বেরিয়ে প্রিয় শিষ্যাকেই তিনি প্রথম সে কথা জানান। স্বামীজির মর্ত্যজীবনের এই পরম প্রার্থনাটির কথা জেনে বিস্মিত হন নিবেদিতা। আরও বিস্মিত হন স্বামীজি যখন বলেন, তাঁর এ বার হিমালয়ে আসার অন্যতম উদ্দেশ্য শিবসুন্দরের কাছেই নিবেদিতাকে উৎসর্গ করা তাঁর জীবনব্রত উদ্যাপনের জন্য। আমরা জানি, হিমালয় তীর্থে সেই দুটি প্রার্থনাই পূরণ হয়েছিল বিবেকানন্দ ও তাঁর মানসকন্যা নিবেদিতার জীবনে।
১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজির সেই প্রথম ইচ্ছাপূরণের দিনটি এল। সে দিন শুক্রবার। বেলুড় মঠে সন্ধ্যায় মন্দিরের প্রার্থনার সময় স্বামীজি তাঁর নিজের ঘরে ধ্যানাসনে বসে রাত ৯টায় শান্তভাবে মহাসমাধি লাভ করেন। সেই অনিন্দ্যসুন্দর দিব্যকান্তি মুখমণ্ডল দেখে প্রথমে কেউ বুঝতেই পারেননি যে, এ স্বামীজির অমৃতধামযাত্রা তথা দু’বছর আগে হিমালয়তীর্থ অমরনাথধামে তুষারলিঙ্গ মহাদেবের কাছে গিয়ে তাঁর ইচ্ছামৃত্যু প্রার্থনার ‘প্র্যাক্টিক্যাল ডিমনস্ট্রেশন’। কিন্তু বিবেকানন্দের কাছে জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য হলেও তাঁর জীবনব্রত উদ্যাপনের জন্য যাঁদের রেখে গেলেন, এর পর তাঁদের কী হবে বা হল? এ বার সে কথাই।
পরদিন ৫ই জুলাই, শনিবার। তখন ভগিনী নিবেদিতার ঠিকানা ১৬ নন্বর বাগবাজার লেন। সকাল ৯টা নাগাদ বেলুড় মঠ থেকে একটা ছোট চিঠি পান স্বামী সারদানন্দজি স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত বয়ানে,
"মাই ডিয়ার নিবেদিতা, দ্য এন্ড হ্যাজ কাম, স্বামীজি হ্যাজ স্লেপ্ট লাস্ট নাইট অ্যাট নাইন ও’ক্লক। নেভার টু রাইজ এগেন সারদানন্দ।"
চিঠির অক্ষরগুলি যেন চোখের সামনে কেঁপেছিল নিবেদিতার, সঙ্গে শরীরটাও। ঘরে উপস্থিত নিবেদিতার সেবিকাও কেঁদে উঠেছিলেন। মাত্র দু’দিন আগেই তো নিবেদিতা বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন স্বামীজিরই নিমন্ত্রণে। স্বামীজি তাঁদের খাইয়েছিলেন পরম যত্নে এবং আহার শেষে স্বামীজি অতিথিদের হাতে জল ঢেলে দিয়েছিলেন হাত ধোওয়ার জন্য। নিবেদিতা সঙ্কুচিত হয়েছিলেন। স্বামীজি বলেছিলেন, “যিশু তো শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন।” কিন্তু সে তো শেষের দিনে। তখন নিবেদিতা ভাবতেও পারেননি, তাঁর গুরুর ক্ষেত্রেও এই কথাটা আক্ষরিক অর্থেই মিলে যাবে।
স্বামীজি কিন্তু অমরনাথে নিবেদিতাকে আভাস দিয়েই রেখেছিলেন, মহাদেব-কৃপায় তিনি ইচ্ছামৃত্যুর বর পেয়েছেন। যার নিহিত অর্থ হল, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত না হলে তাঁর দেহত্যাগ হবে না। স্বামীজির মহাসমাধির পূর্ব পর্যন্ত আনুপূর্বিক সব কথা শুনে নিবেদিতার সে-সব কথাই মনে পড়েছিল। এক দিকে নিবেদিতার শোকস্তব্ধ উদ্গত নয়নের অশ্রুধারা, আর এক দিকে এই সব স্মৃতি। নিবেদিতা আর কালবিলম্ব না করেই বেলুড় থেকে আসা পত্রবাহকের সঙ্গেই রওনা হয়ে যান বেলুড় মঠ অভিমুখে। ইতিমধ্যে স্বামীজির প্রয়াণের খবর ছড়িয়ে গিয়েছিল সারা শহরে। সবাই ছুটেছিল সেই বেলুড়ের দিকে। বেলুড় মঠে পৌঁছেই নিবেদিতা সোজা উঠে গিয়েছিলেন দোতলায় স্বামীজির ঘরের দিকে। ঘরে তখন বেশি লোকজন নেই। স্বামীজির দেহটি মেঝেতে শায়িত ছিল হলুদ রঙের ফুলমালা আচ্ছাদিত হয়ে। মানসকন্যা স্বামীজির শিয়রের কাছে বসে পড়েন। নয়নে অবিরল অশ্রুধারা, মুখে কোনও কথা নেই। আবেগ-আকুল কম্পিত হাতে তুলে নেন গতপ্রাণ স্বামীজির মাথাটি। তখন আর তিনি কন্যা নন, তিনি মাতা! স্বামীজির তাঁর প্রতি আশীর্বচনের সার্থক রূপ একাধারে তিনি সেবিকা ও মাতা। যেন মায়ের মতোই প্রিয়বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হয়ে সেই অনিন্দ্যসুন্দর শিবরূপী গুরুর সেবা করতে থাকেন ছোট একটি পাখা হাতে। এর পর সেই মহাযাত্রার পালা। একে একে সন্ন্যাসী-ভাইরা এসে স্বামীজির দেহটি নীচে নামিয়ে আনেন। আরতি ও প্রণাম-শেষে পা দু’টি অলক্তরাগে রঞ্জিত করেন ও মস্তক অবলুণ্ঠিত করে প্রণাম করেন। গুরুভাইরা শ্রীপাদপদ্মের ছাপ নেন। নিবেদিতাও অশ্রুসিক্ত নয়নে পা দুটি ধুয়ে একটি পরিষ্কার রেশমি রুমালে তাঁর গুরুর পদচিহ্ন গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসী ও সমবেত জনতার সঙ্গে নিবেদিতাও চলেন পায়ে পায়ে সেই গতপ্রাণ বিজয়ী বীরের দেহটি নিয়ে মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে। স্বামীজির শেষকৃত্য সমাপনের নির্দিষ্ট স্থানে, যে স্থান বিবেকানন্দ নিজেই চিহ্নিত করেছিলেন মহাপ্রয়াণের কিছু দিন আগে, তাঁর প্রিয় বেলগাছের কাছে অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গায়।
দেহটি নামানো হলে নিবেদিতা সেই গাছেরই একটু দূরে এসে বসে পড়েন। চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করেন প্রথমে নিবেদিতা ও পরে একে একে গুরুভাই ও অন্যান্য সন্ন্যাসী-ভাইয়েরা। প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সামনে বিবেকানন্দের প্রিয় ‘জি.সি’ অর্থাৎ নাট্যকার ও মহাকবি গিরিশচন্দ্রের বিলাপ, “নরেন, তুমি তো ঠাকুরের ছেলে, ঠাকুরের কোলে গিয়ে উঠলে। আর আমি বুড়ো মানুষ, কোথায় তোমার আগে যাব, তা না হয়ে আজ আমাকে দেখতে হচ্ছে তোমার এই দৃশ্য !” এ কথা শোনামাত্র নিবেদিতা শোক চেপে রাখতে না পেরে দাঁড়িয়ে উঠে স্বামীজির প্রজ্বলিত চিতাগ্নির পাশে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এ দৃশ্যে বিচলিত স্বামী ব্রহ্মানন্দজি স্বামীজির শিষ্য নিশ্চলানন্দকে নিবেদিতাকে চিতাগ্নির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে সান্ত্বনা দিতে বলেন। সেই অনুযায়ী নিশ্চলানন্দ রোরুদ্যমানা নিবেদিতাকে সেখান থেকে দূরে নিয়ে গিয়ে, নানা সান্ত্বনাবাক্যে ভোলাতে লাগলেন।
সারা অঙ্গ চন্দনচর্চিত মনুষ্যদেহে তাঁর শিবরূপী গুরুর ধূপধুনো-গুগগুল সুবাসিত চিতাগ্নি তথা হোমাগ্নি নিবেদিতার অনর্গল নয়নধারায় বুঝি নির্বাপিত করতে চান। সেই হৃদয় হাহাকার করা মুহূর্তে সহসা গুরুর এক অলৌকিক স্নেহস্পর্শ নিবেদিতাকে চমকিত করে।
চিতাগ্নি থেকে একখণ্ড গেরুয়া বস্ত্র হাওয়ায় উড়ে এসে নিবেদিতার কোলে গিয়ে পড়ে। পরম মমতায় ও যত্নে নিবেদিতা তা গুরুর আশীর্বাদ ভেবে মাথায় ঠেকান। সেই পবিত্র স্পর্শ যেন শোকস্তব্ধ হৃদয়ে সান্ত্বনা ও শক্তি জোগায়। তবু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন “পরের জন্য নিজেকে যিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁকেও কেন ছেড়ে দিতে হয় আমাদের? হে ভগবান, কেন?”
এরপর নিবেদিতার বাকি জীবন যেন অগ্নিশিখাই। মানবসেবার পুণ্যব্রতে। ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে নিবেদিতার সংগ্রাম আর এক ইতিহাস। তার সবটুকুই গুরু বিবেকানন্দের দেখানো পথে।
নিবেদিতা হয়তো পাশ্চাত্যের প্রায়শ্চিত্ত। যে পশ্চিম বারে বারে দূত পাঠিয়েছে, যে দূত মনে করেছে ভারতের সবটা কেবল অন্ধকার আর কুসংস্কারে ঠাসা, তাকে নিজ ধর্মে স্নান করিয়ে সভ্য করানো তার মহান দায়িত্ব, যাকে বলে হোয়াইট ম্যানস বার্ডেন, সেই তাদেরই ভূমি থেকে উঠে এসে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থানে রুখে দাঁড়ালেন নিবেদিতা। নিজের তেজ দিয়ে আগলে রাখলেন ভারতের ঐতিহ্যকে, তার ধর্মকর্ম এবং সংস্কারকে। কালীপূজার বহু বিতর্কিত সাধনপদ্ধতির মধ্যে যে প্রকৃতি-অর্চনার বজ্রকঠিন অধ্যায় আছে, তাকে নমস্কার জানালেন। বললেন, ঈশ্বর শুভ ও অশুভ উভয়েই সমান ভাবে বিরাজ করেন। মহাকালীর যে করাল রূপ আমরা দেখি তা মিথ্যা মায়া, মরীচিকা, বিভ্রম। ওই রূপ দেখে যারা ‘না না’ বলে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যায়, তারা অভাগা। তারা কালীর কোলে বসে কালীর মিঠে কথা শুনতে পায় না। যা তিনি দেখান, তা তিনি নন। ওই ভয়ংকর, ওই অমানিশা, ওই ত্রাস পেরিয়ে তবেই নিত্যানন্দময়ী কালীকে পেতে হয়। শক্তিপূজায় এ ভাবেই শক্তি মেলে। হ্যাঁ, এ পুজোর আশেপাশে অনেক শয়তানি জড়ো হয়েছে সত্যি। কিন্তু সে সব আগাছার ভয়ে কি আমরা নন্দনকাননটিকে ত্যাগ করতে পারি?
কালাপানির ও পার থেকে এক অচ্ছুৎ এসে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে কালী নিয়ে এমন আবেগ ভরে কথা বলছে। কালীর চর্চা করছে। রক্ষণশীল সমাজে কী তুমুল ঝড়ই না উঠল। কেউ আবার চোখের জল ফেলে ধন্য ধন্য করে উঠল, এই মেয়ে তো দেখি ঈশ্বরের কথা পৃথিবীকে বলার জন্যই জন্মেছে। সেই সব শংসা-নিন্দার লেশমাত্র তাঁর জ্যোতির্বলয়ে প্রবেশই করতে পারল না। কারণ তিনি তখন কালীকে মেনেছেন, কারণ তাঁকে পেয়ে গিয়েছেন। কালীর সকল সন্তানদের ভালবাসাও সেই মায়ের সঙ্গে খেলারই অঙ্গ। তাঁর যাপন জুড়ে থাকেন মৃত্যুরূপা কালভৈরবী। বাগবাজারের ভাড়াবাড়ির উনুনের মতো গরম এক চিলতে ঘরে যখন দগ্ধে দগ্ধে চরম পরিশ্রম করেন, তখন ঈশান কোণে কালবৈশাখীর মেঘের আভাস দেখলে সব যাতনা ভুলে উঠে দাঁড়ান তিনি। ‘ওই তো! কালী! কালী!’ গরিব ঘরের অপুষ্ট দুধের শিশু তাঁর সামনে শেষ নিঃশ্বাস ফেললে, তার শোকাকুল মাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, বলেন, ‘চুপ করো। তোমার মেয়ে এখন কালীর কাছে!’ শ্রীশ্রীমাকে আনিয়ে নিজের বড় সাধের স্কুলের ভিতপাথর স্থাপনা করেন তিথি দেখে অমাবস্যায়, ঠিক সেই কালীপুজোরই দিনে। ‘আহা, এখানে পড়ে আমার মেয়েরা যেন জগন্মাতার আশীর্বাদটুকু পায়’— রুদ্রাক্ষ চেপে ধরে প্রার্থনা করেন সিস্টার।
আর কালীর পায়ে আত্মোৎসর্গের তত্ত্বকে সত্যি করে একটু একটু করে নিংড়ে দেন নিজের রক্ত। তাঁর কালীর জন্য। কালীর সন্তানদের জন্য। সকালে স্কুল চালান, দুপুরে খর রোদে ছাতা হাতে ছাত্রী খুঁজতে বের হন, বিকেলে মুখের ফেনা তুলে খাটেন রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে। অতীত খুঁড়ে আবার যে ফিরিয়ে আনতে হবে ভারত সংস্কৃতির হীরের যুগ। সন্ধেয় বিপ্লবীদের শেখান স্বাধীনতার মানে। তার পর, রাত জেগে বই লেখেন। পর দিন কাকভোরে উঠে রাস্তা ঝাঁট দিয়ে প্লেগের ব্যাধি তাড়াতে ছোটেন। অক্লান্ত কর্মযোগে তিলে তিলে শেষ হতে হতে সময়ের অনেক আগে নিবেদিতা আশ্রয় নেন বরফের কফিনে।
শক্তিপক্ষেই তাঁর পৃথিবীতে আসা। শক্তিপক্ষেই তাঁর চিরতরে চলে যাওয়া। আমরা শুধু পড়তে পাই দার্জিলিঙের হিমেল শ্মশানভূমিতে তাঁর সমাধির ওপর লেখা কনকনে বাক্যগুলো-
"এখানে শান্তিতে শুয়ে আছেন তিনি, যিনি ভারতবর্ষকে তাঁর সর্বস্ব অর্পণ করেছিলেন— সিস্টার নিবেদিতা: ২৮ অক্টোবর ১৮৬৭-১৩ অক্টোবর ১৯১১।"
তাঁর সৎকারক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় লিপিটি মিশনের দান নয়। এটি স্থাপন করেছিলেন অভেদানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ।
(তথ্যসূত্র:
১- নিবেদিতা লোকমাতা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স।
২- বিদ্রোহীণী নিবেদিতা, ডঃ দীপক চন্দ্র, দে’জ পাবলিশিং।
৩- ভারতকন্যা নিবেদিতা, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, পত্র ভারতী।
৪- বিদ্রোহিনী নিবেদিতা, শশীভূষন দাশগুপ্ত, সুপ্রিম পাবলিশার্স (২০১৩)।
৫- আনন্দবাজার পত্রিকায় ২২শে অক্টোবর ২০১৭ সালে শংকর লিখিত প্রবন্ধ।
৬- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে অক্টোবর ২০১৭ সাল।
৭- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে অক্টোবর ২০১৮ সাল।
৮- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা জুন ২০১৯ সাল।
৯- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে অক্টোবর ২০১৭ সাল।)
১- নিবেদিতা লোকমাতা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, আনন্দ পাবলিশার্স।
২- বিদ্রোহীণী নিবেদিতা, ডঃ দীপক চন্দ্র, দে’জ পাবলিশিং।
৩- ভারতকন্যা নিবেদিতা, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, পত্র ভারতী।
৪- বিদ্রোহিনী নিবেদিতা, শশীভূষন দাশগুপ্ত, সুপ্রিম পাবলিশার্স (২০১৩)।
৫- আনন্দবাজার পত্রিকায় ২২শে অক্টোবর ২০১৭ সালে শংকর লিখিত প্রবন্ধ।
৬- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে অক্টোবর ২০১৭ সাল।
৭- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে অক্টোবর ২০১৮ সাল।
৮- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১লা জুন ২০১৯ সাল।
৯- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮শে অক্টোবর ২০১৭ সাল।)





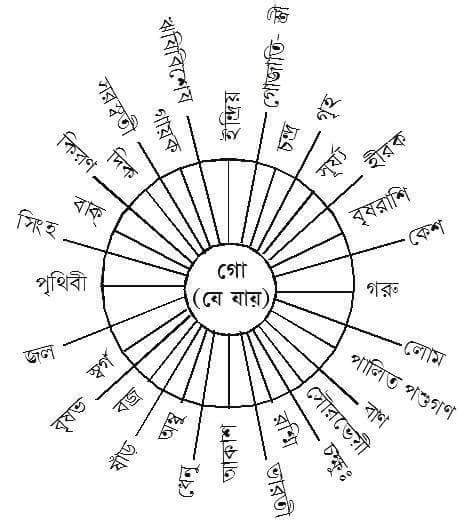

0 মন্তব্যসমূহ