তিনি ছিলেন বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য। বিশ্বভারতীকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সমসাময়িক অনেকের থেকেই তাঁর ভাবনাচিন্তা ছিল আলাদা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কিছু বিতর্কিত বিষয়-সহ নানা কারণে বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিভিন্ন ধাপে সম্পর্ক খারাপ হয়েছে তাঁর। জীবনের শেষ কয়েকটা বছর তিনি বিশ্বভারতী তো বটেই, এই বাংলা থেকেই অনেক দূরে কাটিয়েছেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র হিসেবেই পরিচিত রথীন্দ্রনাথ। অথচ এই রথীন্দ্রনাথই উদ্যোগী হয়ে ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতীকে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বভারতীর উপাচার্য ছিলেন ১৯৫১-র মে মাস থেকে ১৯৫৩ সালের অগস্ট পর্যন্ত। কবি-পুত্রের বাইরেও যে তাঁর একটা শিল্পীসত্তা, লেখার প্রতিভা ছিল তা প্রকাশ পায়নি। কোনও অজ্ঞাত কারণে বিশ্বভারতীর তরফ থেকেও সে রকম কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি।
©️রানা চক্রবর্তী©️
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের বড় ছেলে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। জীবনের শেষ আট বছর তিনি ছিলেন শান্তিনিকেতনের রসগুঞ্জনের অবিসংবাদিত খলনায়ক। জীবন-সায়াহ্নে নিজের স্ত্রীকে ছেড়ে-ছুড়ে, সুদূর দেহরাদূনে ঘর বেঁধেছিলেন তিনি। বন্ধুপত্নীর সঙ্গে।
প্রশাসনিক নানা জটিলতায় শান্তি ছিল না রথী ঠাকুরের। স্ত্রী প্রতিমা দেবীর সঙ্গে সম্পর্কেও হয়তো কোনও উত্তাপ অবশিষ্ট ছিল না। ১৯৫৩ সালের আগস্টে শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যান রথী ঠাকুর। সঙ্গে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মীরা। তাঁর আদরের ‘মীরু’! এর ঢের আগেই অবশ্য মীরার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নিয়ে কানাকানি চরমে ওঠে। উপাচার্য থাকতেই বন্ধুপত্নী মীরা চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে হাজারিবাগ গিয়েছিলেন, সেই হাওয়া-বদল সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয় শান্তিনিকেতনে। আবার উপাচার্যের লেটারহেডেই এক বার মীরা দেবীকে চিঠিতে লিখছেন -
‘ডাক্তার বাবু বলেছিলেন আজ sponging নিতে। সুপূর্ণা ঠিক পারে না— তাই তোমার যদি অসুবিধা না থাকে তবে কি একবার ১১টার কাছাকাছি এসে এটা করতে পারবে?’
এই প্রস্তাব একটু বিসদৃশ ও অস্বস্তিকর, হয়তো এই অনুমানেই চিঠির মাথাতেই ফের লিখে দিচ্ছেন: ‘যদি অভ্যাস না থাকে তো জানিও— আমি নিজে ম্যানেজ করে নেব। সঙ্কোচ কর না।’ কিন্তু সঙ্কোচের বিহ্বলতা যে দুজনেরই এত দ্রুত ও এত দূর পর্যন্ত কেটে যাবে, মুখরক্ষাই দায় হবে শেষমেশ, তা ঠাকুরবাড়ির লোকজন ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারেননি।
এ ঘটনার প্রসঙ্গেই রথীন্দ্রনাথের বোন মীরা ঠাকুর গঙ্গোপাধ্যায় মেয়ে নন্দিতা কৃপালনিকে চিঠিতে লিখেছিলেন -
‘বৌঠান আর আমি তাই বলি যে লোকের কাছে মুখ রক্ষার এই চমৎকার ব্যবস্থা করলেন। নিজে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে ত আর সে-গুলো শুনতে হবে না যা হয় আমাদের হবে।’
রথীন্দ্রনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবীও লিখছেন - ‘এত বৃদ্ধ বয়েসে শেষটা যে নিজেকে একটা এরকম উদ্দামতার মধ্যে নিয়ে ফেলবেন তা ভাবিনি।’
আর সমসময়েই, আত্মপক্ষ সমর্থনে ভাগ্নি নন্দিতাকে লিখছেন রথীন্দ্রনাথ, দেহরাদূন থেকে - ‘তোরা হয় তো অনেক গুজব শুনতে পেয়েছিস্— সব কথা সত্যি না জেনে হঠাৎ বিশ্বাস না করলে খুসী হব।’
©️রানা চক্রবর্তী©️
গুজব আর সত্যের রহস্যময় আলো-আবছায়ায় ঘেরা রথীন্দ্রনাথের জীবনের এই অংশটি ধরতে ‘আপনি তুমি রইলে দূরে’ গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ এই সব চিঠিপত্র সংকলন ও সবিস্তার আলোচনা করেছেন নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনকী রথীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘিরেও যে প্রশ্নের মেঘ জমাট বেঁধেছিল, সে প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। দেহরাদূনেই মারা যান রথীন্দ্রনাথ। ডেথ সার্টিফিকেট অনুযায়ী, মৃত্যু হয় অন্ত্রের সমস্যায়। কিন্তু তাঁর বোন মীরা ঠাকুর গঙ্গোপাধ্যায় মেয়েকে লিখছেন: ‘সময় মত রোগের চিকিৎসা করে নি তাও ত যে শুনছে সেই বলছে কিন্তু সত্যি কি ওরা কিছু খাইয়ে মেরে ফেলেছে? শেষকালে এই ছিল কপালে! ওদের সবই ত দিয়েছিলেন তবু প্রাণে মারল কেন?’
মীরা চট্টোপাধ্যায় ও রথীন্দ্রনাথের মধ্যে যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, সম্ভবত তা শুরু থেকেই স্পষ্ট ছিল মীরার স্বামী নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁর কোনও বিরোধিতা ছিল বলেও মনে হয় না। তাঁর সংরক্ষণে থাকা একটি চিঠিতেই ‘মীরু’র উদ্দেশে ‘রথীদা’ নিজের তীব্র অনুভূতি উজাড় করে দিয়েছেন -
‘আমার কেবল মীরু আছে— সেই-ই আমার সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড।... তাকে আমার সবকিছু দিয়েছি— নিজেকেও সঁপে দিয়েছি।’
প্রথাগত প্র্যাকটিসে শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাননি রথীন্দ্রনাথ। স্বভাবতই তাঁর বোন বা স্ত্রী কোনও দিনই তাঁর ‘মীরু’কে মেনে নিতে পারেননি। কখনও বলেছেন ‘কী ভয়ঙ্কর মেয়ে মানুষ’, কখনও শঙ্কিত হয়েছেন ‘বুড় বয়সের দুর্ব্বল মন, একেবারে মীরার কবলে তলিয়ে যাবেন।’ এ সব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা আজ সম্ভব নয়। কিন্তু সন্দেহ নেই, ঠাকুরবাড়ির ঝকঝকে, পবিত্র-পবিত্র উঠোনে রথীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্যতিক্রমী। সমালোচিত হয়েও, স্বতন্ত্র।
©️রানা চক্রবর্তী©️
এই কাহিনীর শুরুটা ঠিক কোথায়, বা কী ভাবে, তা খুব স্পষ্ট করে বলা কঠিন। অনুমান করা চলে শুধু। অনুমান করা চলে, তিনি দেখেছিলেন, দিগন্তে ঘনিয়ে আসছে মেঘ। দুপুরবেলার নিঃসঙ্গতার মতো মেঘ। বাবা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হয়েছেন প্রায় দশককাল হয়ে গেল। পড়ে আছে বিশ্বভারতী। সেই বিশ্বভারতীর রাশ তাঁরই হাতে, অথচ, তিনিই কি না ঘোর একলা।
না কি, একলা নন! রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নামসংক্ষেপে রথী ঠাকুরের রক্তে একটি মায়া। তিনি এস্রাজে ছড় টানেন, সুর ওঠে। সেই সুর কি বাতাসে ভেসে উত্তরায়ণ থেকে ধেয়ে যায় শ্রীপল্লীর দিকে? শ্রীপল্লীর পাঁচ নম্বর বাড়িটির দিকে?
বিশ্বকবি, কবিগুরু, গুরুদেব এমন নানা বিশেষণের পুষ্পরাজি যাঁর পায়ে সমর্পিত, সেই মহামহিম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিলাভের পরে প্রথম উপাচার্য রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রমে ক্ষয়ে যেতে থাকেন একটি গোপন টানে। বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল, সে কি আমারি পানে ভুলে পড়িবে না, একটি গানে লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রথী ঠাকুর যেন দেখতে পান, এ গান যেখানে সত্য, সেখানে বয়ে চলে শীর্ণ কোপাই, পথপাশে ঘন ছায়া, আঙিনাতে যে আছে অপেক্ষা করে, তার পরনে ঢাকাই শাড়ি, এবং কপালে সিঁদুর!
সিঁদুরের কথা মনে পড়তেই এস্রাজে সুর উতলা হয়! সীমন্তচিহ্নই প্রমাণ, সেই নারীটি পরস্ত্রী। শান্তিনিকেতনে প্রথম যুগের আশ্রমিক এবং পরবর্তী কালে বিশ্বভারতীর শিক্ষক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘকালের পরিচিত। সেই নির্মলচন্দ্রেরই তরুণী স্ত্রী, মীরা। পূর্বনামে মীরা বিশী, নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের পরে মীরা চট্টোপাধ্যায়। এই বিবাহ নিয়ে তখন শান্তিনিকেতনে কিছু বাধাও এসেছিল, পরে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে তা দূর হয়। রথীন্দ্রনাথের একটি দীর্ঘশ্বাস এস্রাজের সুরে মিশে যায়। কেন যে মন ভোলে, তা মন জানে না। শুধু এটুকু জানে যে এই মুহূর্তে তাঁর মানসপটে আর কেউ নেই। কিছু নেই। আছে দু’টি উজ্জ্বল, ঘনকৃষ্ণ চক্ষু। মীরা। আছে বিচিত্র একটি সম্পর্ক। যে সম্পর্কের দাবিতে ছোট্ট একটি হাতচিঠিতে লেখা যায় -
‘মীরা,
ডাক্তার বাবু বলেছিলেন আজ sponging নিতে। সুপূর্ণা ঠিক পারে না তাই তোমার যদি অসুবিধা না থাকে তবে কি একবার ১১টার কাছাকাছি এসে এটা করতে পারবে? আমি সকালে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলুম। জানি না তোমার অভ্যাস আছে কি না যদি অসুবিধা না থাকে তো এস মিনিট দশ-পনেরোর জন্য। তোমার উপর খুবই অত্যাচার করছি।
রথীদা।’
হাতচিঠি এখানেই ফুরোয় না, নীচে জুড়ে থাকে আরও একটি বাক্য।
‘যদি অভ্যাস না থাকে তো জানিও আমি নিজে ম্যানেজ করে নেব। সঙ্কোচ কর না।’
কিন্তু, আসলে ঠিক কাকে বিহ্বল করে সঙ্কোচ? পত্রলেখককেই কি নয়? পুনশ্চের মতো একটি বাক্য জুড়ে দিতে হয় কেন? বিশ্বভারতীর উপাচার্যের লেটারহেড-এ এক প্রৌঢ় পুরুষ তাঁর অঙ্গ-চর্যার জন্য ডাকছেন সদ্য ত্রিশ-পেরোনো এক যুবতীকে। যদিও সেই কাজ অসুস্থের চিকিৎসা-সংক্রান্ত, তবু আমন্ত্রণটিই তো ঈষৎ অ-স্বাভাবিক! গত শতকের মধ্যভাগের সমাজ-সম্পর্কের বিচারে তো বটেই, এমনকী এখনও, এই একুশ শতকী বঙ্গভূমেও, এমন চিঠি চার পাশে বেশ কিছু ভ্রু কুঞ্চিত করবে, নিশ্চিত! কী কথা তাহার সাথে? কেনই বা ডাক দেওয়ার পরে কয়েকটি শব্দে সহসা একটি দূরত্ব জাগিয়ে রাখার প্রয়াস? অন্তরঙ্গতা সত্ত্বেও কাছে থেকে দূর রচনার আলতো একটি খেলা? কেনই বা তার স্বামী নির্মলচন্দ্রকে আর একটি ছোট্ট হাতচিঠিতে জরুরি কাজ নিয়ে বসার কথা জানিয়ে রথীন্দ্রনাথ লেখেন:
‘কাল সকালে কফি টেবিলে কথা হতে পারে যদি তোমরা এস’।
রথীদা’
©️রানা চক্রবর্তী©️
সর্বনামের নীচে নজরটান তাঁরই দেওয়া, পাছে তাও চোখে না পড়ে, তাই অন্তিমে আরও দু’টি বাক্য জুড়তে হয়, ‘বহুবচনটা লক্ষ্য রেখ। আমাকে দোষের দায় ফেল না।’ কেন ‘তোমরা’? কাজ তো নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো-তে একটি অনুষ্ঠান নিয়ে বিশ্বভারতীর উপাচার্যের সঙ্গে এক শিক্ষকের জরুরি কিছু আলাপ। সেখানে ‘বহুবচন’টি কেন? স্বাভাবিক, প্রাতরাশের আমন্ত্রণ একলা শিক্ষকটিকেই করা হয়তো সৌজন্যের বিরোধী, বিশেষত তিনি যখন এই নবীন দম্পতিটির খুবই ঘনিষ্ঠ... কিন্তু, শুধুই কি ‘সৌজন্য’? শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা? টুকরো টুকরো চিঠিতে ছড়িয়ে থাকে এই ‘বহু’-বচন! ‘কাল ছুটি, তায় আজ চাঁদনী রাত। অশেষকে বলেছি এস্রাজ নিয়ে আসতে। আহারাদির পর ৮টা-৯টার মধ্যে তোমরা দু’জনে এস যদি বাজনা শুনতে ভাল লাগে।’ 'সন্ধ্যাবেলাটা একলা ভাল লাগে না। দেখেছ তো কেওই বড় আসে না। তোমরাও কি আসবে না?’
‘যদি বিশেষ অসুবিধা বোধ না কর তবে আজ রাত্রিতে যদি এস তবে খুসী হব। অনেক উপকার পেয়েছি তোমাদের কাছ থেকে তাই লোভও অতিমাত্রায় বেড়ে গেছে। তোমাদের বেশি লেখা বাহুল্য। এটা নিতান্তই ছেলেমানুষী আবদারের মত তোমাদের মনে হবে, না?’
‘নিতান্তই ছেলেমানুষী’ বুঝি? তা হলে শান্তিনিকেতনের রাঙা ধুলোয় কেন ওড়ে নানাবিধ গুঞ্জন? কেন জীবন্ত একটি প্রশ্নচিহ্নের মতো জেগে থাকেন আর এক নারী?
বয়সে রথীন্দ্রনাথের তুলনায় সামান্য ছোট। সম্পর্কে তাঁর সহধর্মিণী। ঠাকুর পরিবারের প্রথম ‘বিধবা’-বধূ। প্রতিমা দেবী। ‘কোণার্ক’ ভবনে তাঁর নিভৃত বাস। উত্তরায়ণের যে পম্পা সরোবরের ধারে রথীন্দ্রনাথের দারু-কর্মের স্টুডিও ‘গুহাঘর’, তারই উপরে প্রতিমা দেবীর স্টুডিও ‘চিত্রভানু’! গুহাঘরেই থাকেন রথীন্দ্রনাথ। অথচ দু’জনের সাক্ষাৎ নেই। কী করেই বা থাকে? যে শান্তিনিকেতন একদা পরিহাস করে বলত, বিশ্বভারতী কোথায়, এ তো ‘বিশ্ব বা রথী’, সেখানেই জনতার কানে কানে ভাসে আর একটি নাম। ‘রামী’। ‘মীরা’ নয়, ‘রামী’! চকিতে প্রাচীন এক প্রেমকথার অনুষঙ্গ জেগে ওঠে, আবার মিলিয়েও যায় লোকজনের বাঁকা হাসির মধ্যে! বিশ্বভারতীর উপাচার্য থাকাকালীনই একবার হাজারিবাগ যান রথীন্দ্রনাথ। সহচর ছিলেন নির্মলচন্দ্রের স্ত্রী মীরা। শান্তিনিকেতনের আকাশবাতাস বিদ্রূপে, সমালোচনায় তিক্ত হয়ে ওঠে।
সে কথা কি বোঝেন না প্রাজ্ঞ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর? তখনও গণমাধ্যম এমন সর্বত্রগামী নয়, পাপারাৎজির দল তাঁকে তাড়া করেনি, কিন্তু মুখরোচক এমন একটি সংবাদ গোপন থাকেনি। রথীন্দ্রনাথের বোন, মীরা ঠাকুর গঙ্গোপাধ্যায় মেয়ে নন্দিতাকে একটি চিঠিতে লিখছেন:
‘রোজই কাগজ খুল্লে একটা আশঙ্কা হোত যে না জানি ওখানকার বিষয় কি লিখে বসে। একদিন Blitz কাগজে দাদার হাজারিবাগ যাওয়া নিয়ে বেশ স্পষ্টই লিখেছিল শুধু দাদার নামটা দেয়নি। বিশ্বভারতীর কাজ ছেড়ে দিলে সে দিকে আর কোনও দুশ্চিন্তা রইল না যে কে কি ছেপে দেবে Private Life-এ যা খুশী করতে পারবেন সে দিক দিয়ে আরো স্বাধীন হলেন কারোর বলবার কিছু রইল না।’
©️রানা চক্রবর্তী©️
সজ্ঞানেই হোক, বা অজান্তে, বোন মীরাই ধরিয়ে দেন অগ্রজ রথীন্দ্রনাথের জীবনে নিহিত সংকট! এক দিকে বিশ্বভারতী, জনসমাজ, বিপুল দায়িত্ব। অন্য দিকে, Private Life, ব্যক্তিগত জীবন। এক দিকে ইতিহাসের চাপ, ভাবমূর্তির দায়। অন্য দিকে, লুকোনো বেদনা।
যতই দেখি তারে ততই দহি আপন মনজ্বালা নীরবে সহি, তবু পারিনে দূরে যেতে...
অতঃপর? তিক্ত, বিষণ্ণ রথীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখলেন:
‘আমাকে চলে যেতেই হবে এই কলুষিত আবহাওয়া ছেড়ে। আমার সামান্য যেটুকু পুঁজি আছে তাতে জীবনটা আয়েসে না হলেও কোনোরকমে চলে যাবে। টাকার চেয়ে যেটা বেশি দরকার মনে করি সেটা হচ্ছে একটু যত্ন ও সমবেদনা। এটা বলতে আমার লজ্জা হয় কিন্তু বয়স ও স্বাস্থ্যের কাছে হার মেনেছি। আমার এই দুর্বলতার জন্য তোমার কাছে অসম্ভব দাবি করেছি যা আমার আত্মীয়দের কাছেও করি নি, করতে ইচ্ছাও করে না।’
গুহাঘরের নিভৃতে বসে নির্মলচন্দ্রের কাছে কী ‘অসম্ভব দাবি’ রাখার কথা ভাবেন রথীন্দ্রনাথ? উত্তরায়ণের নিকটে পম্পা সরোবরের স্থির জল এলোমেলো হয় সহসা। এস্রাজ মৌন হয়।
তার ছিঁড়ে গেছে কবে, সে খোঁজ কে-ই বা রাখে?
রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁরই অতি স্নেহভাজন এক শিক্ষকের পত্নীর সঙ্গে পাড়ি দেন দূর দেশ। দেরাদুন। সঙ্গে সেই নবীনার মা ছিলেন যদিও, জনরব তাতে মন্থর হয়নি একটুও। স্বামী নির্মলচন্দ্র বিশ্বভারতীতেই কর্মসূত্রে নিয়োজিত। কন্যা জয়িতাও বিশ্বভারতীর ছাত্রী। মীরা চট্টোপাধ্যায় আছেন দূরে। রথীন্দ্রনাথ এবং মা কমলা দেবীর সঙ্গে। দেরাদুন-এ। তাঁদের নতুন বাড়ির নাম, ‘শেষের কবিতা’-র অনুষঙ্গে, ‘মিতালি’। নির্মলচন্দ্রের নীরবতা বিস্ময়কর এবং প্রলম্বিত। ছুটিতে তিনিও যাচ্ছেন সেখানে। ফিরেও আসছেন শান্তিনিকেতনে। কিন্তু, এই ত্রিভুজের গভীরে কি থেকে যায় আরও কিছু? শুধুই কি নির্মলচন্দ্রই যান দেরাদুনে? দূর থেকে কি আরও বেশ কিছু উৎসুক চক্ষু অপলকে সেই বাড়ির দিকে তাকায় না?
©️রানা চক্রবর্তী©️
রথীন্দ্রনাথের বোন মীরা দেবী মেয়ে নন্দিতা কৃপালনিকে চিঠিতে লিখছেন:
‘বৌঠানের সঙ্গে দাদার চাক্ষুষ দেখা হয়নি তবে মুসুরি যাওয়া আসার পথে দাদা যেখানে আছেন বাড়ীটা দু দিন বার দেখেছেন। বারান্ডা থেকে নতুন শাড়ী ঝুলছে তাও দেখছেন। রামকৃষ্ণ আশ্রমের কাছে জমি কিনে নতুন বাড়ী তৈরি করছেন দুজনে মিলে তদারক করতে যান তাও শুনেছেন।... এখন বুঝছি যে বাবার নাটকগুলোর জবাই করে সে টাকায় রামীর জন্যে নতুন প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে। কালিংপংএর বাড়ীর ভিতরে যে সব কাঠের কাজ আছে তার ডিজাইন ও মাপ জোপের খাতা সুবলকে পাঠাতে লিখেছেন। বুঝলুম যে এটা রামীর আবদার রাখবার জন্যে যাতে চিত্র-ভানুর চেয়ে তার বাড়ী কোন অংশে খাটো না হয়। সম্ভব হলে বোধহয় দ্বিতীয় আর একটা উদয়ন করে ফেলত তবে অত টাকা বোধহয় এখন নেই। আশ্চর্য্য ক্ষমতা রামীর, কোন যোগ্যতা না থেকেও শেষ পর্যন্ত বৌঠানের উপর টেক্কা মারল। দেরাদুনে দাদার ছবির একজিবিশন হচ্ছে শুনে মুসুরি যাবার পথে বৌঠান সেখানে একবার নেমেছিলেন দাদার আঁকা ছবির পাশে রামীর আঁকা ছবি পাশাপাশি ঝুলছে দেখলেন। আর কি চাই বল?’
সহসা মনে হতেই পারে, আশ্চর্য কোনও চিত্রনাট্য! চলন্ত গাড়ি থেকে পথের পাশে, কিছুটা দূরে একটি বাড়ির দিকে সতৃষ্ণ চেয়ে আছেন যিনি, তাঁরই স্বামী সেই গৃহের বাসিন্দা। আছেন স্বেচ্ছা-নির্বাসনে। সঙ্গে অন্য এক নারী। লং শটে দেখা যায় সেই বাড়ির বারান্দায় দোদুল্যমান একটি শাড়ি। সেই বস্ত্রের ঝকঝকে অবয়ব থেকে ঠিকরে আসে রৌদ্র। গাড়ি এগিয়ে যায়। মাথার ভিতরে, গম্ভীর পেন্ডুলামের মতো একটি শাড়ি দুলে চলে। অবিরাম।
প্রতিমা দেবী ননদের মেয়ে নন্দিতাকে লেখেন:
‘কী ভয়ঙ্কর মেয়ে মানুষ শান্তিনিকেতনে আমাদের পাসা পাসি ছিল তা কখন পূর্ব্বে তো ভাবিনি।...আমার নিজের চেয়েও তোর মামার জন্যই কষ্ট আজ আমি পাচ্ছি। কী মতিভ্রম হোল নিজের কাজ কর্ম সব ছেড়ে ঐ একটা অতি অর্ডিনারী টাইপের মেয়ের সঙ্গে চলে গেলেন, মানুষের কত পরিবর্তন হয় তাই ভাবি।’
©️রানা চক্রবর্তী©️
যে নারীকে নিয়ে এই বিস্ময়কর আখ্যান, তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং রথীন্দ্রনাথের কী ধারণা? দু’টি চিঠি দাখিল করা চলে দৃষ্টান্তবশত। নির্মলচন্দ্রকে লিখছেন রথীন্দ্রনাথ:
‘মীরার মধ্যে হাল্কা-হাসির দিক ছাড়াও যে গভীরতা আছে, যা সকলের চোখে পড়ে না, সেইটা না থাকলে বা আমি যদি না বুঝতে পারতুম তবে আমার এতটা ভাল লাগত না। আমার মনে হয় লোকে মীরাকে ভুলই বোঝে।’
এ বার মীরাকে লেখা তাঁর চিঠির একটি টুকরো:
‘যা চাচ্ছিলুম, যার অভাবে মন অসাড় হয়ে গিয়েছিল তোমার মধ্যে তা দেখতে পেয়ে অন্তরাত্মা উল্লসিত হয়ে উঠল। একটুও দ্বিধা বোধ হয় নি...আমি তৃপ্ত হলুম, নিঃসঙ্গ জীবন সঙ্গী পেল, নিজেকে ধন্য বোধ করলুম। বাইরের জগৎ অদৃশ্য হয়ে গেল তোমার মধ্যেই আমার সমস্ত জগৎ পেয়ে গেলুম।’
দেরাদুনে একটি নিভৃতবাস ছাড়া বাকি সমূহ জগৎ অদৃশ্য হোক, এই আকাঙ্ক্ষাটি রথীন্দ্রনাথের তদানীন্তন মানসিক পরিস্থিতির পক্ষে অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে না। ঘটেওনি। ফলে নির্মলচন্দ্রকে চিঠিতে লিখতে হয় -
‘আমাদের তিনজনের মধ্যে যদি কোনো ভুল বোঝাবুঝি থাকে তবে সেটা মর্মান্তিক বেদনাদায়ক হবে।’ কিংবা ওই চিঠিতেই আর এক জায়গায় তাঁর বক্তব্য: ‘মীরা যে আমার মন অধিকার করেছে তার মধ্যে সন্তান স্নেহ, মাতৃভক্তি এবং অকৃত্রিম অকলুষ ভালবাসা সব মেশান আছে। এ কথা কি তুমি জান না?’
পাশাপাশি থাক মীরা চট্টোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠি -
‘তোমারি সব, আমার কিছু নয়। আমার কেবল মীরু আছে সেই-ই আমার সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড। তাকে ছাড়া আমি কিছুই নই আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। তাকে আমার সবকিছু দিয়েছি নিজেকেও সঁপে দিয়েছি।’
আশ্চর্য এই সমর্পণ! মাঝে মাঝে দেরাদুন থেকে শান্তিনিকেতনে আসেন রথীন্দ্রনাথ। সঙ্গে মীরা। কানাকানি চলে, প্রতিমা দেবী চলে যান নিঃশব্দ অন্তরালে, রথীন্দ্রনাথ অবিচলিত। আবার মীরা চট্টোপাধ্যায় যখন স্বামী নির্মলচন্দ্রকে ‘নিমু আমার’ সম্বোধন করে একটি চিঠি লেখেন, তখন সেই কাগজেই থাকে রথীন্দ্রনাথের লেখা একটি সংযোজন। সংযোজনটি কেন সেখানেই থাকে, কেন অন্য পত্রে নয়, সেই প্রশ্নটি অবশ্য বিশেষ অসঙ্গত নয়। উত্তর মেলে না।
রথীন্দ্রনাথের নিজস্ব দাম্পত্য জীবনের কথা মনে আসে প্রসঙ্গত। সেখানেও কি ব্যক্তিগত কোনও পরিসর রচনা করে নিতে পেরেছিলেন তাঁরা? পারলেও, কতটা পেরেছিলেন? সুপ্রসিদ্ধ পিতৃদেবের ছায়ায় গ্রস্ত তাঁর ব্যক্তিগত জীবন। প্রতিমা দেবী রবীন্দ্রনাথের পরিচর্যায় নিরন্তর নিয়োজিত। ‘আমার রাস্তা দিয়ে যে তোমাদের জীবনের পথে তোমরা চলবে এ কথা মনে করা অন্যায় এবং এ সম্বন্ধে জোর করা দৌরাত্ম্য’, এ কথা প্রতিমা দেবীকে লিখছেন বটে রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু বাস্তবে কি অনেকটা সে রকমই ঘটল না রথী এবং প্রতিমার যুগল-জীবনে? এর সঙ্গে যুক্ত হল তাঁদের নিঃসন্তান জীবন। এমনকী, পালিতা কন্যা নন্দিনী (পুপে)-র আগমনও অন্তর্গত ফাটলটি তেমন করে জুড়তে পারল না। দু’জনে দু’ভাবে মুক্তির সন্ধান করলেন হয়তো। ঝড় এল, যেমন আসে। চলেও যায়।
প্রয়াণের আগের বছর, ১৯৬০-এ ‘ভাই প্রতিমা’ সম্বোধন করে একটি চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘আমরা দুজনেই এখন জীবনের সীমান্তে এসে পড়েছি। এখন আর কারো প্রতি রাগ বা অভিমান পুষে রাখা শোভনীয় হয় না। সেইজন্য জেনো আমার মনে কোনো রাগ নেই আমি সব ঝেড়ে ফেলেছি।’
©️রানা চক্রবর্তী©️
অনুমান করা চলে, আজ, ২৭ নভেম্বর রথীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কোনও অ-লৌকিকে তাঁদের দেখা হল হয়তো! রাত্রি এসে যেথায় মেশে দিনের পারাবারে, তেমন কোনও স্থানে। রবীন্দ্রনাথ ‘নৌকাডুবি’-তে ঝড়ের পরে চরাচরের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, যেন বা আক্ষরিকই সে রকম: ‘কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুময় বালুভূমিকে নির্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মতো আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিল না, রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে স্থলে স্তব্ধভাবে বিরাজ করিতেছে।’
সেই স্তব্ধতার মধ্যে এসে দাঁড়ালেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এসে দাঁড়ালেন প্রতিমা দেবী। তাঁদের কি পুনরায় দেখা হল? হয়তো বা। হয়তো নির্মলচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন তাঁর স্ত্রী মীরা। আর, ওই যে মায়াকুমারীগণ গান ধরলেন,
'যদি আর কারে ভালবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস, তবে তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো...
আমার পরান যাহা চায় ...'
হৃদয়ের যে-সব সুকুমারবৃত্তিকে আমরা মনুষ্যচরিত্রের প্রকৃষ্ট লক্ষণ বলে মনে করি, বাবার মধ্যে সেগুলি ছিল পূর্ণ মাত্রায়। কিন্তু সব কিছু মিলে তাঁর স্বভাব ছিল জটিল ও দুর্জ্ঞেয়।
©️রানা চক্রবর্তী©️
পুরনো সাদা-কালো বাংলা সিনেমার সেই প্রতাপশালী বাবাদের কথা মনে আছে? ‘দেয়া-নেয়া’র কমল মিত্র, ‘সপ্তপদী’র ছবি বিশ্বাস। এঁদের দাপটে দুই সিনেমাতেই ছেলের, ম্যাটিনি আইডল উত্তমকুমারের, অবস্থা বেশ ঢিলে। কোথায় যাচ্ছেন, কী করছেন, কার সঙ্গে প্রেম করছেন, জবাবদিহি করতে করতে ছেলে জেরবার। পিতা-পুত্রের ‘মেলোড্রামাটিক’ টানাপড়েন অবশ্য আম-বাঙালি টানটান হয়ে উপভোগ করত। থিম হিসেবে বাবা-ছেলের চাপান-উতোরের কোনও মার নেই। সিনেমায় যেমন হয়, বাস্তবে কি তা হয় না? হয়, অন্য রকম ভাবে, কখনও আরও গভীর, আরও জটিল চেহারা নেয় সেই টানাপড়েন। যেমন রবীন্দ্রনাথ আর রথীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছবির কমল মিত্র বা ছবি বিশ্বাসদের মতো প্রবল-প্রতাপ বাবা ছিলেন না। পরনে হাউস কোট, মুখে পাইপ, প্রবাসী বাঙালি শিল্পপতি বাবা কমল মিত্র দেয়া-নেয়া ছবিতে যে ভাবে সুগায়ক পুত্র উত্তমকুমারকে ধমক দেন, গান গাইবার জন্য ব্যঙ্গ করেন, সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথ মোটেই তেমন নন। রবিবাবুর গান তো সকলের প্রিয়। আর তাঁর পিতামহ, ব্যবসায়ী, উদ্যোগপতি প্রিন্স দ্বারকানাথ সম্বন্ধে গায়ক-কবি রবীন্দ্রনাথের মন খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত। সম্পদের চাইতে সংস্কৃতির প্রতিই রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক টান। রবীন্দ্রনাথের সাতাশ বছর বয়সে, জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে পুত্র রথীন্দ্রনাথের যখন জন্ম হয়েছে, তত দিনে শুধু কবি হিসেবেই নন, তিনি সুগায়ক হিসেবেও আদৃত। রথীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি স্মৃতিকথা অন দি এজেস অব টাইম-এ কিশোরবেলার স্মৃতি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন পিতার গান গাইবার কথা।
তারকনাথ পালিতের বাড়িতে আত্মতৃপ্ত, ইংরেজিয়ানায় অভ্যস্ত কংগ্রেস নেতাদের ডিনার পার্টিতে ধুতি-চাদর পরা রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন, ‘আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না’। বাবা হিসেবে জাত-পাত-ধর্ম ইত্যাদির ‘কুসংস্কার’ থেকেও রবীন্দ্রনাথ মুক্ত। তারাশঙ্করের লেখা থেকে তৈরি ছবি সপ্তপদী’তে বাবা ছবি বিশ্বাস বেজাতের, ভিনধর্মের মেয়েকে পুত্রবধূ রূপে মানতে নারাজ। উদার আধুনিক রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর পুত্রের ‘বিধবা বিবাহ’ দেন। তা হলে?
পুত্র রথীন্দ্রনাথের ওপর পিতার চাপটা অন্য। সে চাপ প্রত্যাশার। সুদর্শন, সুগায়ক, সুকবি, সংবেদনশীল রবীন্দ্রনাথের পুত্র কেমন হবেন, কী করবেন, তা নিয়ে রথীন্দ্রনাথের জন্মের আগে থেকেই ঠাকুর পরিবারে আলাপ আলোচনার শেষ নেই। রথীন্দ্রনাথ তা জানতেন। তাঁর ইংরেজি স্মৃতিকথার গোড়াতেই আছে সে প্রসঙ্গ। রবিকার সন্তান কেমন হবে ছেলে না মেয়ে, হাসিখুশি না সিরিয়াস টাইপ, সমাজ সংস্কারক না ঘরকুনো, হিতেন্দ্রনাথ তা নিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন। বলেন্দ্রনাথ রবিকার সঙ্গে এই ‘আসছে’ সন্তানের মিল-বেমিল নিয়ে ফুট কাটছেন। আর এই সব পারিবারিক কৌতুকের দাপটে রথীর মনে হচ্ছে, সে দেখতে ভাল নয়, তার গায়ের রং কালো। লিখছেন রথীন্দ্র,
'My life thus started with a handicap which gave me a complex that has been difficult to overcome even at a mature age.'
বিখ্যাত বাবার ছেলে হওয়ার, সুখ্যাত পরিবারের সন্তান হওয়ার কী জ্বালা! সহজাত ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স।
©️রানা চক্রবর্তী©️
অথচ অনেক গুণ ছিল তাঁর। বাংলা ইংরেজি দু’ভাষাতেই চমকার লিখতেন, ছবি আঁকতেন, কাঠের কাজ আর উদ্যানচর্চায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কৃষিবিজ্ঞানের ভাল ছাত্র, খেলাধুলোয় উৎসাহী, সংগঠনী ক্ষমতা যথেষ্ট। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় কসমোপলিটান ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই ক্লাবের বেসবল টিমের তিনি উত্সাহী উদ্যোক্তা। আবার পিতা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা আর আনুগত্য কিছু কম ছিল না। বিশ্বভারতীর জন্য কত কিছু করেছেন। বিদেশে গবেষক জীবনের ভবিষ্যত্ ফেলে দেশে ফিরে পিতার কাজে যোগ দিয়েছেন। চিত্তরঞ্জন দাশ রথীন্দ্রনাথকে ভারতীয় লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য করতে উদ্যোগী হন, রথীন্দ্রনাথ নারাজ। তাঁর সমস্ত উদ্যম ও সময় নাকি বিশ্বভারতীর জন্য নির্দিষ্ট।
বিশ্বভারতীর প্রতি শ্রদ্ধার একটা নিদর্শন মনে রাখার মতো, তাতে এক স্বাভাবিক উদারতাও প্রতিফলিত হয়। বাবার মৃত্যুর পর রথীন্দ্রনাথ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখছেন, ‘বাবার personality ঘরের কোণে আবদ্ধ করে রাখবার নয়। তাঁর জীবনের কোনো ঘটনাই চাপা দিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে অন্যায়। তাঁর জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা যত প্রকাশ হয় ততই ভাল। আমি মনে করি আমার right নেই কোনো বিষয় লুকিয়ে রাখার। এই জন্যই আমার কাছে যা কিছু mss, চিঠি, cuttings ফোটো diary প্রভৃতি ছিল, সে collection বড়ো কম নয়, আমি একত্র করে museum-এর মতো সাজিয়ে বিশ্বভারতীকে দান করেছি।’
ছেলে তো বাবাকে সকলের জন্য ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাবা? রবীন্দ্রনাথ ‘আশীর্বাদ’ কবিতায় লিখেছিলেন, ‘পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।’ তাই, যে ছোট প্রদীপখানি নিয়ে তিনি আলো দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন, অথচ আলোর থেকে যে প্রদীপ ছায়া দিচ্ছিল বেশি, কবি সে প্রদীপ ‘ভেঙে দিনু ফেলে’। কিন্তু পিতা? রবীন্দ্রনাথের নানা সময়ের নানা খেয়াল মেটাতে হয়েছে রথীকে।
‘পুরুষের মন’ নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন রথীন্দ্র। লিখেছিলেন,
‘ছিল এক সময়
মেয়েদের আঁচলের হাওয়ায় দুলিয়ে দিত মন
তাদের ছোঁয়া গায়ে দিত কাঁটা
...কত জনের মাধুরী চুনে গড়লুম কল্পনার এক মূর্তি,
সব কাজের ফাঁকে উঠতে লাগল মনে
একটি মোহন ছবি।’
রবীন্দ্রনাথ নানা শব্দ যোগবিয়োগ করে লেখাটি শুধরে দিয়েছিলেন। ‘সব কাজের ফাঁকে উঠতে লাগল মনে’, ছেলের কবিতার এই লাইনটি পিতার সংশোধনের পর হল, ‘কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় আর ঢাকা পড়ে’। এ তো যেমন তেমন সংশোধন নয়, উঠে-পড়া মন যেন ঢাকাও পড়ে গেল।
©️রানা চক্রবর্তী©️
আর তাই হয়তো বাবাকে শ্রদ্ধা করছেন, বাবার জীবন ও কার্যের ইতিহাসকে জনগণের জন্য খুলে দিচ্ছেন পুত্র, কিন্তু জানাতে ভুলছেন না, তাঁর বাবা ‘a most complex charecter’. এই নির্মোহ বিশ্লেষণ কি শুধু বাবা সম্বন্ধেই? আছে অন্যদের কথাও। রথীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি স্মৃতিকথা লিখেছিলেন পরিণত বয়সে। অন দি এজেস অব টাইম (ওরিয়েন্ট লংম্যান) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। রথীন্দ্র স্মৃতিকথায় পরিবারের বর্ণময় গুরুজনদের নিরপেক্ষ ভাবে নিজের মতো করে বোঝার চেষ্টা করছেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বারকানাথ সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত, রথীন্দ্রনাথ নন। তাঁর কলমে দ্বারকানাথ ‘romantic figure’. আর মহর্ষি? পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে থাকতেন কান্ট আর বেদান্ত পড়া, আপনভোলা দ্বিজেন্দ্রনাথ। রথীন্দ্রনাথ জানাতে ভোলেননি, দ্বিজেন্দ্রনাথ পার্থিব বিষয়-আশয়ে শিশুর মতো বেখেয়ালি হলেও মহর্ষি মোটেই তেমন নন। রোমান্টিক দ্বারকানাথ, বাবার জটিল চরিত্র, বিষয়ী মহর্ষি, এ-সবই রথীন্দ্র ইংরেজি ভাষায় নিচু স্বরে লিখে ফেলেছিলেন। এ যেন নিজস্ব প্রতিবাদ। বিখ্যাত বাবা আর সুখ্যাত পরিবারের যে অনিবার্য ছায়া তাঁকে ধাওয়া করত, তা থেকে বাইরে আসার চেষ্টা।
জীবনের শেষ পর্বে রথীন্দ্রনাথ চলে গিয়েছিলেন, বলা ভাল, চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন, দেহরাদূনে। সেখানে নিজের মতো সময় যাপনের অবসর হয়েছিল তাঁর। শান্তিনিকেতনের জোব্বা ছেড়ে পরতেন শার্ট শর্টস। তবে বাবাকে, বাবার কর্মসাধনাকে ভুলতে চাননি শান্তিনিকেতনের এই ছাত্র। ১৯৬১। পিতার জন্মশতবর্ষ। রথীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য, শতবর্ষ পালনের উৎসবে ডাক পাননি প্রতিষ্ঠান থেকে। এ বড় আঘাত। সেই বছরেই পুত্রের প্রয়াণ। রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষের আলো সারা দেশে, নীরবে চলে গেলেন পুত্র। পিতাপুত্রের এই কাহিনির সঙ্গে কি বাংলা ছায়াছবির তুলনা চলে?
জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে সকলের যা-ইচ্ছে-তাই লেখার একটা খাতা ছিল। ‘পারিবারিক খাতা’। ১৮৮৮-র নভেম্বরে হিতেন্দ্রনাথ সেখানে লিখলেন, তাঁর রবিকাকার মেয়ে হবে না। হবে মান্যবান, সৌভাগ্যবান, রবীন্দ্রনাথের চেয়েও গম্ভীর একটি ছেলে। সে-মাসেরই ২৭শে নভেম্বর, মৃণালিনী আর রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সন্তান হিসেবে এলেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গায়ের রং সেই তখন থেকেই চাপা। পেরিয়ে যাই বছর কয়েক।
সাত-আট বছর বয়সে একবার শিলাইদহ থেকে রথী ফিরে এলেন রোদে জলে পুড়ে। যেন আরও একটু ‘কালো’ হয়ে। পাশেই গগনেন্দ্রনাথদের বাড়িতে জ্যাঠাইমাকে প্রণাম করতে গেলেন। তিনি বললেন, ‘‘ছিঃ, রবি তাঁর ছেলেকে একেবারে চাষা বানিয়ে নিয়ে এল।’’ কথাটা সে দিন খুব মনে লেগেছিল রথীন্দ্রনাথের। এতটাই যে, তার পর থেকে ওই বাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিলেন তিনি। আর এমনই কাণ্ড, বাংলার পল্লিমঙ্গলের স্বপ্ন দেখে, সেই ‘চাষা’ হয়ে ওঠার পাঠ নিতেই, ছেলেকে তার পর একদিন সত্যি-সত্যি বিদেশে পাঠিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ!
©️রানা চক্রবর্তী©️
১৯০৬। স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ তখন তুঙ্গে। রথীন্দ্রনাথ আর আশ্রমে তাঁর সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দিলেন ছাত্রদের এক দলের সঙ্গে জাপানে। কিছু দিন পর দু’জনে পৌঁছলেন আমেরিকার আর্বানায়, ইলিনয়ের স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকেই হয়েছিলেন কৃষিবিজ্ঞানে স্নাতক। ১৯০৭-এ আমেরিকা থেকে রথী বাবাকে পরীক্ষার জন্য পাঠাতে লিখছেন একবার ফসল দিয়ে ঝিমিয়ে-পড়া মাটি। জানাচ্ছেন, বিদেশে তিনি যে কেবল মাটিই ‘বিশ্লেষ’ করছেন তা নয়, পরীক্ষা চলছে শস্য এবং পশুখাদ্য নিয়েও।
২১শে জুন ১৯০৮। ছেলেকে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করে লিখলেন, ‘‘...আমাদের দেশের হাওয়ায় কী চাষা কী ভদ্রলোক কোনও মতে সমবেত হতে জানে না। তোরা ফিরে এসে চাষাদের মধ্যে থেকে তাদের মতিগতি যদি ফেরাতে পারিস তো দেখা যাবে।’’
বাবাকে নিরাশ করলেন না রথী। রবীন্দ্রনাথের ডাকে জমিদারি দেখাশোনার কাজে ১৯০৯-এ ফিরে এলেন শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ যেন এই সময় একেবারে আঁকড়ে ধরলেন রথীকে। তাঁকে চেনালেন বাংলার পল্লিসমাজ। ছেলের মুখে কৃষিবিদ্যা, প্রজননশাস্ত্র, অভিব্যক্তিবাদের কথা শুনতেন খুব মন দিয়ে। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ‘‘১৯১০ সালের সেই সময়টাতে আমরা পিতাপুত্র পরস্পরের যত কাছাকাছি এসেছিলাম তেমন আর কখনো ঘটে নি।’’ শিলাইদহে রথীন্দ্রনাথ গড়ে তুললেন প্রশস্ত খেত। মাটি পরীক্ষার গবেষণাগার। বিদেশ থেকে আমদানি করলেন ভুট্টার এবং গৃহপালিত পশুর খাওয়ার মতো ঘাসের বীজ। তৈরি করালেন দেশের উপযোগী লাঙল, ফলা, আর নানা যন্ত্রপাতি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কাছ থেকে পাতিসরের জন্য চেয়ে আনলেন একটা ট্রাক্টর। চালাতেন নিজেই। বাংলার কৃষি আর কৃষকের হাল ফেরাতে যখন ঝাঁপিয়ে পড়েছেন রথী, তখন আবার এল রবীন্দ্রনাথের ডাক। এ বার নাকি তাঁর বিয়ে!
মৃণালিনী রথীর বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের ভাগ্নী প্রতিমার সঙ্গে। ছেলের বিয়ে দিতে তখনই রাজি হননি রবীন্দ্রনাথ।১৯১০-এ তত দিনে বাল্যবিধবা সেই প্রতিমাকেই ঘরে আনা ঠিক করে, রথীকে খবর পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ। পাঁচ বছরের ছোট প্রতিমার গুণে যে তিনি পাগল, সে-কথা জানিয়ে ভগ্নিপতি নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘‘প্রতিমা এখন আমার... সে কী চমৎকার মেয়ে তোমাকে কী করে লিখি।’’ আর একবার খোদ প্রতিমাকেই লিখেছিলেন, ‘‘আমি কখনই একজন কুশ্রী মেয়েকে সম্পূর্ণ ভালবাসতে পারতুমনা— আমার সে দুর্ব্বলতা আমি স্বীকার করছি।’’
©️রানা চক্রবর্তী©️
২৭শে জানুয়ারি ১৯১০। হল বিয়ে। নিজের বিয়ে নিয়ে স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন, ‘‘আমাদের পরিবারে এই প্রথম বিধবা বিবাহ।’’ বিয়ের কয়েক মাস পর প্রতিমাকে শিলাইদহে নিয়ে এলেন রথী। এর পর হঠাৎ একদিন আবার ডাক রবীন্দ্রনাথের! শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয়ে এ বার তাঁর দরকার রথীকে! কুঠিবাড়ির চার দিকের গোলাপ বাগিচা, একটু দূরে সুদূরবিস্তারী খেত, সেই পদ্মা নদী, সেই কত সুখদুঃখের কাহিনি মোড়া বজরা... বাবার এক ডাকে সব ছেড়ে এলেন রথীন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের কথায়, ‘‘এই-সব যা কিছু আমার ভাল লাগত— সেই সব ছেড়ে আমায় চলে যেতে হল বীরভূমের ঊষর কঠিন লাল মাটির প্রান্তরে।’’
২রা মে ১৯১০-এ লেখা এক চিঠিতে অনভিজ্ঞ, ‘ছেলেমানুষ’ প্রতিমার প্রতি রথীন্দ্রনাথের কর্তব্য তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। লিখেছিলেন, ‘‘... তার চিত্তকে জাগিয়ে তোলবার ভার তোকেই নিতে হবে— তার জীবনের বিচিত্র খাদ্য তোকে জোগাতে হবে। তার মধ্যে যে শক্তি আছে তার কোনোটা যাতে মুষড়ে না যায় সে দায়িত্ব তোর।’’ কিন্তু ভিতরে-ভিতরে কোথাও মুষড়ে পড়েছিলেন যেমন রথী, তেমনই প্রতিমা। এতটাই যে, এক চিঠিতে স্ত্রীকে রথীন্দ্রনাথ জানালেন, ‘‘কতদিন বোলপুরের মাঠে একলা পড়ে যে কেঁদেছি তা কেউ জানে না। তুমিও না।’’ চাইলেও নিজেকে মেলে ধরতে না পারার অক্ষমতার কথা জানিয়ে লিখলেন, ‘‘ভগবান আমাকে বোবা করে জন্ম দিয়েছেন।’’
প্রতিমাকে লেখা রথীন্দ্রনাথের তারিখবিহীন কয়েকটা চিঠিতে বোঝা যায়, দু’জনের বোঝাপড়ার এক সময় কোথাও একটা সমস্যা হচ্ছিল। মন খুলে দু’জনে আসতে পারছেন না কাছাকাছি। রথী লিখছেন প্রতিমাকে, তাঁর শুষ্ক, শূন্য সত্তার ভিতরেও আছে, ‘‘আর একটাকেও যে খুব ভালোবাসতে চায়, যে খুব সুন্দর হতে চায়... কিন্তু তার একটি দোষ আছে সে ভারী লাজুক।’’ তার পর প্রতিমাকেই রথী দিচ্ছেন সেই লাজুক মানুষটার আড়াল থেকে তাঁর প্রকৃতিকে টেনে বের করে আনার ভার। মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ‘‘আর তা যদি না পারো তো চিরকাল তোমাকে কষ্ট পেতে হবে— তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করো।’’ আর একবার লিখলেন, ‘‘তোর মনটা সম্পূর্ণ পাবার জন্যে আমি কিরকম ব্যাকুল হয়ে থাকি তা তুই জানিস না।’’
১৯২২-এ দু’জনের সংসারে এলেন নন্দিনী, তাঁদের পালিতা কন্যা হয়ে। ‘দাদামশায়’ রবীন্দ্রনাথের রাখা আদরের নাতনি নন্দিনীর অনেক নামের মধ্যে একটা ছিল ‘পুপে’। সম্ভাব্য নাতির জন্যও একটা নাম আগলে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তেইশ বসন্ত অপেক্ষার পর ‘রাসভেন্দ্র’ নামটা কবি দিয়ে দিলেন প্রিয়ভাজন সুরেন্দ্রনাথ করকে।
©️রানা চক্রবর্তী©️
ইলিনয়ে ছাত্রজীবনে রথীর সঙ্গে পরিচয় হওয়া ভাষার অধ্যাপক আর্থার সেমুর-এর স্ত্রী মেস সেমুরকে রথীন্দ্রনাথ আগেই লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ মারা যাওয়ার পর তাঁর মূল কাজ ছিল, বিশ্বভারতীর ভাঙন ঠেকিয়ে রাখা। এক সময় তিনি চাইলেন, বাবার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানকে একটা স্থায়িত্ব দিয়ে যেতে। ১লা নভেম্বর, ১৯৪৮। ইংরেজি এক চিঠিতে মেস সেমুরকে লিখলেন, বিশ্বভারতীর কাজ তাঁকে আর আনন্দ দেয় না, নৈতিক কর্তব্য পালনের তাগিদেই সে কাজ করে থাকেন শুধু। বহু বছর ছিলেন কর্মসচিব। ১৯৫১-য় বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে, রথীন্দ্রনাথ হলেন তার প্রথম উপাচার্য। তার পরই বুঝলেন, কবির আশ্রম থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে বদলে যাওয়াটা আসলে এক বিপর্যয়! ক্ষমতার রাজনীতি ছিলই, তার সঙ্গেই এ বার বিশ্বভারতীতে জুড়ে গেল নিয়মের ঘেরাটোপ! তার মধ্যেই ব্যক্তিগত আক্রমণ আর কুৎসায় নাজেহাল হয়ে গেলেন রথীন্দ্রনাথ। আর্থিক অনিয়মের মিথ্যে অভিযোগে ফাঁসানোর চেষ্টাও হল তাঁকে। বাঁচাল আদালত।
সব গুঞ্জনকে ছাপিয়ে গেল আশ্রমের অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর তাঁর স্ত্রী মীরার সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের প্রথাভাঙা অন্তরঙ্গতা। ও দিকে নির্মলচন্দ্র আর মীরাকে শান্তিনিকেতন থেকে সরিয়ে দেওয়ার মৌখিক পরামর্শ দিয়ে, উপাচার্য রথীন্দ্রনাথের কাছে খবর পাঠালেন আচার্য জওহরলাল নেহরু। এতেই যেন ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল অপমানিত রথীন্দ্রনাথের। পদত্যাগ করলেন তাঁর কাছেই। কারণ হিসেবে লিখলেন, তাঁর শরীর খারাপ। ঠিক করলেন, বিশ্বভারতীর কলুষিত পরিবেশ ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবেন। সেই স্বেচ্ছা-নির্বাসনে তাঁকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য নির্মলচন্দ্রের কাছে তার পর তিনি করে বসলেন এক ‘অসম্ভব দাবী’। নির্মলের কাছে এক রকম সোজাসাপটা চেয়েই বসলেন বয়সে একত্রিশ বছরের ছোট মীরাকে। এই চাওয়ার কথা প্রথম স্বীকার করে চিঠি লিখেছিলেন নির্মলচন্দ্রকে। তারিখ ছিল ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩।
১৯১৮-য় নির্মলচন্দ্র ছিলেন আশ্রমের ছাত্র, এর পর রবীন্দ্রনাথের ডাকে ১৯৩৮-এ সেখানেই ফিরে আসেন ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে। কোলের ছেলে জয়ব্রতকে নিয়ে মীরাকে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেহরাদুনে গিয়ে বসবাসের সম্মতিও দিয়ে দিলেন তাঁর উদার-হৃদয় স্বামী। নিজে রইলেন মেয়েকে নিয়ে। যাওয়ার আগে প্রতিমাকে রথীন্দ্রনাথ লিখে গেলেন, ‘‘আমি লুকিয়ে চুরিয়ে যাচ্ছি না, এখানে সবাইকে জানিয়েই যাচ্ছি মীরা আমার সঙ্গে যাচ্ছে।’’
রথীন্দ্রনাথের নিজের কথায়, বিশ্বভারতী থেকে তাঁর ‘মুক্তি’ পাওয়ার দিন ২২শে অগস্ট ১৯৫৩। আর আশ্রম ছেড়েছিলেন তার দু’-একদিন পর।
©️রানা চক্রবর্তী©️
১৯৫৩ থেকে ১৯৬১। দেহরাদুনে প্রথমে তিনটে ভাড়াবাড়ি। তার পর ’৮৯-এ রাজপুর রোডে তাঁর নিজের তৈরি বাড়ি ‘মিতালি’তেই মীরাকে নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিলেন রথীন্দ্রনাথ। দেহরাদুনে স্বামীর বাড়ির সামনে দিয়ে মুসুরি যাওয়ার পথে প্রতিমা একবার শুধু দেখতে পেয়েছিলেন, বারান্দা থেকে ঝুলে থাকা নতুন শাড়ি। রথীন্দ্রনাথের বোন, দাদার সঙ্গিনী মীরা প্রসঙ্গে একবার মেয়েকে লিখেছিলেন, ‘‘...ওনার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ঐ মেয়ে গ্রাস করে নেবে।’’
এক সাময়িক বিচ্ছেদের সময় দেহরাদুনে বসে, তাঁর বেলাশেষের আলো মীরা চট্টোপাধ্যায়কে তারিখবিহীন এক চিঠিতে রথীন্দ্রনাথ লিখলেন, ‘‘আমার কেবল মীরু আছে— সে-ই আমার সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাণ্ড। তাকে ছাড়া আমি কিছুই নই— আমার কোনও অস্তিত্ব নেই। তাকে আমার সবকিছু দিয়েছি— নিজেকেও সপেঁ দিয়েছি।’’
অন্য এক চিঠিতে মীরার সঙ্গে দেখা হওয়ার অপেক্ষায় আকুল রথীন্দ্রনাথ তাঁকে লিখছেন, ‘‘সময় যত কাছে আসছে মন আরও অস্থির হয়ে উঠছে। কী করে শান্ত করি বল তো?... তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকে এতদিনের ছাড়াছাড়ি এই প্রথম। বাপরে আর যেন এরকম না ঘটে।’’
চিঠি লিখতেন মীরাও, তাঁর ‘রথীদা’-কে। যদিও এযাবৎ খোঁজ নেই রথীন্দ্রনাথকে লেখা মীরা চট্টোপাধ্যায়ের কোনও চিঠির। দেহরাদুনে রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে মীরা ও তাঁর শিশুপুত্র ছাড়াও থাকতেন মীরার মা। ছুটিছাটায় মেয়েকে নিয়ে নির্মলচন্দ্র এসে ঘুরে যেতেন কখনও।
বিশ্বভারতী ছেড়ে তাঁর দূরে চলে যাওয়ার ইচ্ছের কথা জেনেই প্রতিমা রথীকে লিখেছিলেন, শুধু ‘‘ভাল আছ এই খবর পেলেই খুশী হব।’’ ভাল থাকার খবর দিয়ে দেহরাদুন থেকে প্রতিমাকে নিয়মিত মমতায় মাখা সব চিঠি লিখেছেন রথীন্দ্রনাথ। ও দিকে অদৃষ্টের হাতে সব ছেড়ে দিয়েও রথীর জন্য উতলা হয়েছেন প্রতিমা।
১৯৬০। বাংলা নববর্ষের আগে প্রতিমাকে রথী লিখলেন, ‘‘আমরা দু’জনেই এখন জীবনের সীমান্তে এসে পড়েছি। এখন আর কারও প্রতি রাগ বা অভিমান পুষে রাখা (শোভনীয়) হয় না। সেইজন্য জেনো আমার মনে কোনও রাগ নেই— আমি সব ঝেড়ে ফেলেছি। আমাদের মধ্যে প্রীতি সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ থাকে এই নতুন বছরে তাই কামনা করি।’’
রতনপল্লিতে ‘ছায়ানীড়’-এ মেয়ে নন্দিনীর নিজের বাড়ি শুরু হওয়ার আগে সেখানেই রথীন্দ্রনাথ চাইলেন, নিজের মাথা-গোঁজা আর কাঠের-কাজের জন্য দু’-একটা ঘর। বললেন, উত্তরায়ণ আর ভাল লাগে না তাঁর। বাবার শততম জন্মবর্ষে একবার এসে ছুঁয়ে গেলেন আশ্রমের মাটি। ৪ঠা মার্চ। মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরে যাওয়ার দিন গাড়িতে তুলে দিতে গিয়ে, তাঁর স্বামী গিরিধারী লালার সঙ্গে নন্দিনী সেই প্রথম দেখলেন, বহু দুর্যোগে এযাবৎ অবিচল বাবার চোখে জল।
৩রা মে ১৯৬১। দেহরাদুনের ‘মিতালি’তে, রবীন্দ্রনাথের শতবাৰ্ষিক জন্মদিনের দিনকয়েক আগে, চলে গেলেন প্রতিভাবান পুত্র রথীন্দ্রনাথ। নির্বিবাদী, সিংহরাশি, ‘সেবক রথী’র বিষণ্ণ জন্মপত্রীতে তখন শুধু জেগে: ‘অমিত নবমী পূর্ব্বফল্গুনী’।
©️রানা চক্রবর্তী©️
★ অশেষ প্রতিভার রথীঠাকুর ~
এঁকেছিলেন মিশ্রমাধ্যমে বহু উল্লেখযোগ্য ল্যান্ডস্কেপ আর ফুলের ছবি।
চামড়ার উপর কারুকাজ, দারুশিল্পেও ছিল অনায়াস দক্ষতা।
আসবাব, স্থাপত্য, উদ্যান নির্মাণেও ছিলেন অনন্য।
তৈরি করতেন গোলাপ, জুঁই, মগরা সহ রকমারি ফুলের আতর আর সুগন্ধি পাউডার। তাঁর আতরের বাজারি নাম ছিল ‘Arty Perfume’।
রান্নার, জ্যাম, জেলি, আচার আর দই পাতার হাত ছিল চমৎকার।
চাষ করতেন মৌমাছির, নেশা ছিল শিকারেরও।
গান গাইতেন, বাজাতেন এস্রাজ।
চিঠি আর দিনলিপি ছাড়াও লিখেছেন কবিতা, গল্প প্রবন্ধ। ইংরেজিতে প্রকাশিত তাঁর বই “On the Edges of Time”। বাবার নির্দেশে অনুবাদ করেছিলেন অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’। তাঁর লেখা অন্য দুটি বই: ‘প্রাণতত্ত্ব’, এবং ‘অভিব্যক্তি’।
রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক সংবাদ কর্তিকার সংগ্রহে ইচ্ছুক হয়ে সদস্য হন লন্ডনের International Newspaper Clipping Service -এর। ছিলেন রবীন্দ্র-সৃষ্টির সংগ্রাহক।
©️রানা চক্রবর্তী©️
■ কেমন আছে ‘মিতালি’ ~
দেহরাদুনে রথীন্দ্রনাথের বাড়ি ছুঁয়ে এসেছিলেন বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শ্রী স্বপনকুমার দত্ত। তাঁর বয়ান অনুসারে:
"দেহরাদুনে গিয়েছিলাম কর্মসূত্রে। এখানেই বিশ্বভারতীর প্রথম উপাচার্য, রথীন্দ্রনাথের বাড়ি ‘মিতালি’র কথা নানা স্মৃতিচারণে পড়েছিলাম, যেখানে কেটেছিল তাঁর শেষ জীবন। ভাবলাম খুঁজে দেখি। বেরিয়ে পড়লাম ৮৯এ রাজপুর রোডের দিকে।
খুঁজে পেলাম দোতলা একটা বাড়ি, অবশ্য রথীবাবুর বাড়ি কি না, প্রতিবেশীরাও নিশ্চিত নন। প্রকাণ্ড প্রাচীর। দুর্ভেদ্য লোহার গেট। বাড়ির ভিতর প্রাচীন গাছ। দুটো বিলাসবহুল গাড়ি...
কিন্তু না আছে নেমপ্লেট, না সে বাড়ির নম্বর! শান্তিনিকেতনের উদয়নের আদলে গড়া রথীন্দ্রনাথের ‘মিতালি’র দোতলায় ছিল অতিথিদের জন্য সাজানো ঘর। জানালায় মোড়া রথীন্দ্রনাথের ঘর থেকে দেখা যেত পাহাড়ি উপত্যকা। বাগানে ফুলগাছের বাহার, স্ট্রবেরির ছোট খেত। বাগানের চৌবাচ্চায় ফুটত নীল শালুক, ভোরবেলা ভেসে আসত বনমোরগের ডাক। রথীন্দ্রনাথ মেতে থাকতেন শিল্প বা উদ্যান চর্চায়। কখনও বাজাতেন এস্রাজ।
হাত-বদল হওয়া বাড়িটা ভেঙেচুরে বদলানো হয়েছে। ফিরে আসব, এমন সময় চোখ আটকে গেল বুজিয়ে দেওয়া জানালার উপরে সিমেন্টের নকশায়! রথীন্দ্রনাথের সিগনেচার স্টাইল, যা ছড়িয়ে আছে শান্তিনিকেতনের উদয়ন আর গুহাঘরে। দেখলাম, সিমেন্টে খোদাই করা ফুলও। ‘‘এটাই মিতালি,’’ বললাম সঙ্গী উৎসাহীদের। তার পর বিষণ্ণ মনে ফিরে এলাম স্মৃতিভারাতুর বাড়িটির সামনে থেকে।"
©️রানা চক্রবর্তী©️
(তথ্যসূত্র:
১- আপনি তুমি রইলে দূরে, সঙ্গ নিঃসঙ্গতা ও রথীন্দ্রনাথ, নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, দে’জ পাবলিশিং।
২- পিতৃস্মৃতি (রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
৩- চিঠিপত্র: দ্বিতীয় খণ্ড (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।
৪- রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর: জন্মশতবর্ষপূর্তি-শ্রদ্ধার্ঘ্য (অনাথনাথ দাস সম্পাদিত)।
৫- রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়স্বজন (সমীর সেনগুপ্ত)।
৬- On the Edges of Time (Rathindranath Tagore)।
৭- A Home in Urbana: Correspondences between the Tagores and Seymours (Supriya Roy Ed.) The Diaries of Rathindranath Tagore (Supriya Roy Ed.)।
৮- Rathindranath Tagore: The Unsung Hero (Tapati Mukhopadhyay and Amrit Sen Ed.)।
৯- বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অভিলেখাগার।
১০- আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সাল।
১১- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে নভেম্বর ২০১৩ সাল।
১২- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৭শে নভেম্বর ২০১১ সাল।
১৩- আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫শে জানুয়ারি ২০১৫ সাল।
১৪- বিশেষ কৃতজ্ঞতা: শ্রী জয়ব্রত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী সুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সংগ্রহ।)






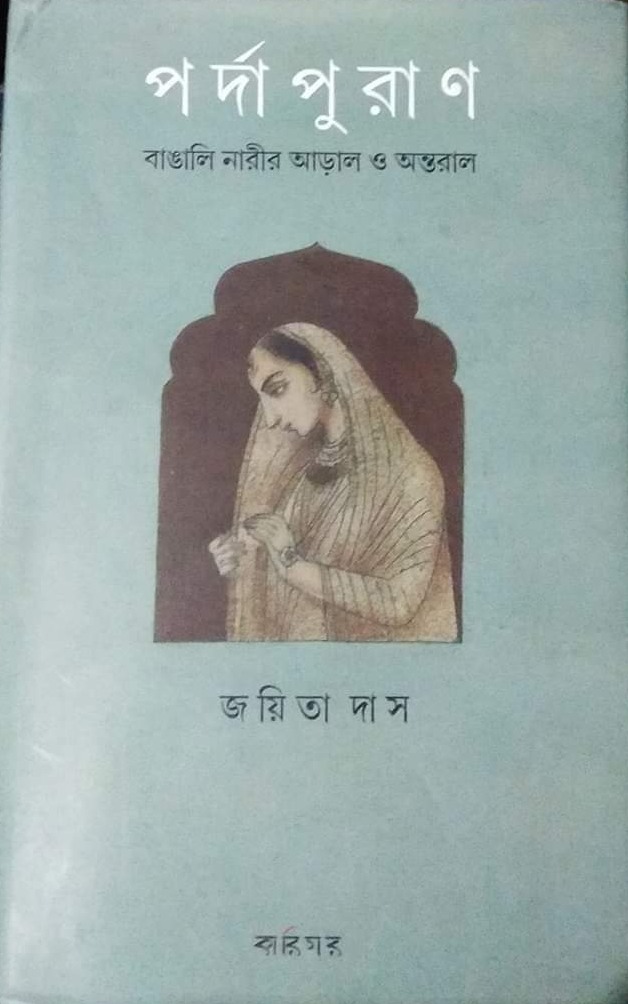
0 মন্তব্যসমূহ