রসায়নের ক্লাস। ছাত্রদের সামনে এক টুকরো হাড় হাতে নিয়ে বুনসেন বার্নারে পুড়িয়ে মুখে পুরে দিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। ছাত্রদের শেখালেন, এটা ক্যালসিয়াম ফসফেট। এছাড়া আর কিছুই নয়। সেটা কোন প্রাণীর হাড় তা-ও আর চেনার উপায় রইল না। রসায়ন দিয়ে শুধু রসায়ন শিক্ষাই নয়, ছাত্রদের মনে ধর্মান্ধতার মূল উপড়ে ফেলার মন্ত্রটিও প্রবেশ করিয়ে দিতেন তিনি। যত টুকু দরকার, তার বাইরে কতটুকুই বা পড়ার আগ্রহ আছে আমাদের বইবিমুখ আগামীর? অথচ, বই পড়ার আগ্রহ থেকেই জন্ম হয়েছিল এই বাঙালি মনীষীর। নিজের সফলতাকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন সার্থকতার শিখরে।
‘আত্মচরিত’ গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণের শুরুতেই তিনি বলেছেন,
‘‘একটি সমগ্র জাতি মাত্র কেরানী বা মসীজীবী হইয়া টিকিতে পারে না; বাঙালি এতোদিন সেই ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ সে সকল প্রকার জীবনোপায় ও কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত। বৈদেশিকগণের তো কথাই নাই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশসহ লোকের সহিতও জীবন সংগ্রামে আমরা প্রত্যহ হটিয়া যাইতেছি। বাঙালি যে নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে ইহা আর কবির খেদোক্তি নহে, রূঢ় নিদারুণ সত্য।’’
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘লাইফ অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স অব এ বেঙ্গলি কেমিস্ট’ (প্রথম খণ্ড ১৯৩২ দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৩৫) বহুল উদ্ধৃত একটি বই। তাঁর আর একটি স্মরণীয় গ্রন্থ ‘এ হিস্টি অব হিন্দু কেমেস্ট্রি ফ্রম দ্য আর্লিয়েস্ট টাইমস টু দ্য মিডল অব সিক্সটিনথ সেঞ্চুরি’ (প্রথম খণ্ড ১৯০১, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯০৯)।
তাঁর স্নাতকপর্বের অভিসন্দর্ভ ইন্ডিয়া বিফোর দ্য মিউটিনি, পরবর্তীকালে প্রকাশিত ‘এসেস অ্যান্ড ডিসকোর্সেস’ এবং তাঁর বহুসংখ্যক প্রবন্ধ সমাজ গঠনের নির্দেশনা দেয়।
১৯১০-এ প্রকাশিত হয় তাঁর দেখা ‘বেঙ্গলি ব্রেইন অ্যান্ড ইটস মিসইউজ’ বিজ্ঞান আবিষ্কার বিষয় লেখাগুলো তখনকার শ্রেষ্ঠ জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জৈব রসায়নকে রহস্যময় ঐশ্বরিক তত্ত্ব ‘প্রাণবাদ’-এর নির্মোক মুক্ত করে বিজ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে যে-মানুষটির সর্বোচ্চ ভূমিকা ছিল তিনি হলেন ‘মার্সিলিন বার্থেলট’ (‘বের্তেলো’)। 1827 সালে প্যারিসে জন্ম তাঁর। তিনি ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যক সৌভাগ্যবান বিজ্ঞানীদের একজন যাঁরা জীবদ্দশায় পেয়েছেন বিজ্ঞানীর প্রাপ্য সম্মান, পরিচিতি ও খ্যাতি।
খ্যাতির মধ্যগগনে থাকার সময় তিনি হাত দিলেন খাঁটি বিজ্ঞান সাধনার বাইরে একটি বিরল প্রচেষ্টায়। কাজটি ছিল সমগ্র আলকেমির ইতিহাস বিশ্লেষণের মাধ্যমে হারানো বিজ্ঞানের সন্ধান। প্রাচীন বিজ্ঞানের ইতিহাসে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছিল কিংবদন্তি এবং পরীক্ষামূলক বাস্তব। সে ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে রসায়নের বিকাশ হয়েছে কিছুটা যেন অযাচিত এবং আকস্মিক ভাবেই। তাই এই আলকেমির হাত ধরেই পরশপাথরের নিষ্ফল সন্ধান বহু শতাব্দীর ট্রায়াল এন্ড এরর পদ্ধতির উপজাতক হিসেবে জন্ম দিয়েছিল রসায়ন শাস্ত্রের। রসায়নবিদ বার্থেলট নেমে পড়লেন ইতিহাসের আকর খুঁড়ে সেই আবিষ্কারের মুহূর্তগুলির সন্ধানে। অনেকগুলি ভাষার ওপর ছিল তাঁর অসামান্য দখল। একে একে ফরাসিতে অনুবাদ করে ফেললেন গ্রিক, সিরিয় এবং আরবি ভাষায় লেখা আলকেমির বহুসংখ্যক প্রাচীন পাণ্ডুলিপি। তারই নির্যাস নিয়ে লিখলেন বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ের ওপর বহু খণ্ডের একটি মহাগ্রন্থ।
প্রাক মধ্যযুগ থেকে রেনেসাঁস পর্যন্ত পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ ধরা পড়ল তাঁর লেখায়। তাঁর একটি রচনা পড়ে উনিশ শতকের শেষ দিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বার্থেলটের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর নাম প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বার্থেলটের উৎসাহে এই আগ্রহী অধ্যাপক ভারতীয় রসায়নের ইতিহাস চর্চার শূন্যতা লক্ষ করে নিজেই একটি গ্রন্থ লেখার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে ‘রসেন্দ্রসার সংগ্রহ’ নামক একটি পুঁথি অবলম্বন করে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দেন বিজ্ঞানী বার্থেলটকে। প্রবন্ধটি পড়ে আপ্লুত বার্থেলট নিজের রচনার সবগুলি খণ্ডই উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দেন এই বাঙালী রসায়নবিদটিকে। সূচনা হয় এক বন্ধুত্বের যা আমৃত্যু বজায় ছিল। এই ফরাসী রসায়নবিদের উৎসাহে বেশ কিছুদিন গবেষণা স্থগিত রেখে অধ্যাপক রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন বহু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি ও দুষ্প্রাপ্য তান্ত্রিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে। কয়েক জন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সাহায্যে নিজের অসামান্য সংস্কৃত জ্ঞান ও মনীষা কাজে লাগিয়ে ইতিহাস চর্চা শুরু করেন। ভারত ইতিহাস প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে এক বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগার। এর পরিণতিতে ১৯০২ সালে লন্ডন এবং কলকাতা থেকে প্রকাশ পায় এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা গ্রন্থ, ‘এ হিস্টোরি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি, প্রথম খন্ড’, লেখক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।
এটিই ছিল ভারতবর্ষে রসায়নের ক্রমবিকাশ বিষয়ে রচিত প্রথম আকর গ্রন্থ। প্রফুল্ল চন্দ্রের বইটির প্রভূত প্রশংসা করে বিখ্যাত একটি ফরাসী পত্রিকায় সমালোচনা লেখেন বার্থেলট। প্রফুল্ল চন্দ্র সংস্কৃত পুঁথির সূত্র ধরে প্রথমবারের মতো দেখান ভারতের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এবং তান্ত্রিক ঔষধ প্রস্তুতির মাঝে লুকিয়ে রয়েছে রসায়ন। এর পর ১৯০৯ সালে বেরোয় বইটির দ্বিতীয় খণ্ড। সেখানে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের লেখা একটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালির দর্শন চিন্তার স্বর্ণযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তিনি দার্শনিক হলেও গণিত, লজিক ও সংস্কৃত সহ নানা বিষয়ে তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়ে কীভাবে বৈজ্ঞানিক ভাবনা বিকশিত হয়েছিল তা দেখান। বিশ্লেষণ করেন ষড়দর্শনের বিভিন্ন ধারা। বিশ্বভারতীর প্রথম আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ পরবর্তী কালে নিজেও এ বিষয়ে ‘দ্যা পজিটিভ সায়েন্সেস অফ দ্যা এনশিয়েন্ট হিন্দুস’ নামে একটি গবেষণালব্ধ বই লেখেন।
প্রফুল্ল চন্দ্রের ‘এ হিস্টোরি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি, দ্বিতীয় খন্ড’ প্রকাশিত হবার পরই দেশ বিদেশের নানা পত্রিকায় এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ছাপা হয়। বলা হয় এই সম্পূর্ণ নতুন দিকদর্শনকারী কাজের জন্য তিনি অমর হয়ে থাকবেন। প্রফুল্ল চন্দ্রের গভীর আক্ষেপ ছিল যে বার্থেলট এই খণ্ডটি দেখে যেতে পারেননি। এই গ্রন্থটি যখন প্রকাশিত হয় তখন বার্থেলট আর জীবিত নেই। মৃত্যুর আগে নিজের সমস্ত আবিষ্কার দান করে দিয়েছিলেন ফরাসী সরকারকে, মানবজাতির কল্যাণে উন্নতি সাধনের জন্য। ভারতীয় ইতিহাস পুনঃ-দর্শনের সংশ্লেষণ বিক্রিয়ায় বার্থেলট ছিলেন ধনাত্মক অনুঘটক।
দ্বিতীয় খণ্ডটি তাঁকেই উৎসর্গ করেন প্রফুল্ল চন্দ্র। বেশ কয়েক জন ইউরোপীয় ও ভারতীয় লেখকদের চর্চা থেকে একথা জানা যায় যে প্রাচীন ভারতের শল্য চিকিৎসা সমসাময়িক সভ্যতাগুলি থেকে অনেক উন্নত ছিল। চরকসংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা থেকে প্রমাণ মেলে সে আমলে ভারতীয়দের আয়ত্তে ছিল নাকের কাটা অংশের প্রতিস্থাপন সহ বিভিন্ন প্রকারের ‘অপারেশন’। অর্থাৎ মানবদেহের অঙ্গসংস্থান সম্পর্কে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। সেযুগে এনাটমি বিষয়ে ভারতীয়রা পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন যা বিনা শল্য চিকিৎসার এত উন্নতি সম্ভব ছিল না। সার্জারির কাজে ব্যবহৃত হত বিভিন্ন রকম ছুরি ও নানা যন্ত্রপাতি। এ বিষয়টিকেই আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র যুক্তি বিশ্লেষণে দেখালেন প্রাচীন ভারতের ধাতুবিদ্যার উন্নতি হিসেবে। সার্জারির কাজে দেহ ব্যবচ্ছেদকারী ছুরি বা যন্ত্রগুলির অত্যন্ত সূক্ষ্মাগ্র হওয়া প্রয়োজন। অতএব সে যুগে নানা ধাতুকে পরিমিত পরিমাণে মিশিয়ে বিভিন্ন ধাতু সঙ্কর তৈরি করা এবং লাগাতার পিটিয়ে সরু ধারালো ধাতুর পাতে পরিণত করার জন্য এদের মধ্যে কোন মিশ্রণগুলি আদর্শ ছিল তা ভারতীয়দের জানা ছিল। তাই স্ক্যালপেল বা ল্যানসেট-এর প্রাচীন ভারতীয় সংস্করণের অস্তিত্ব অবশ্যই ধাতুবিদ্যায় পারদর্শিতার প্রমাণ। ধাতুবিদ্যার কথা এলে যে জিনিসটি নিয়ে আজও ভারতীয়দের গর্ব করা সাজে তা হল ‘উটজ স্টিল’ (‘wootz steel’)। প্রায় ছশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে বর্তমান তেলেঙ্গানা সহ দক্ষিণ ভারতের বেশ কিছু স্থানে এই ইস্পাত তৈরি হত। পরবর্তীকালে তা রপ্তানি করা হত দামাস্কাস সহ আরবের অন্যান্য জায়গায়। এই ভারতীয় উটজ স্টিলের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। ভারত থেকে রপ্তানিকৃত উটজ স্টিলের চাঙর থেকে দামাস্কাসে তৈরি হত তলোয়ার। ইউরোপে তা প্রসিদ্ধ হয় দামাস্কাস স্টিল নামে। মধ্যযুগে ক্রুসেড চলাকালীনও ব্যবহার হত উটজ ইস্পাতে নির্মিত তরবারি। অস্ত্রের উৎকর্ষর কারণে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে অনেক যুদ্ধে জয়লাভ হয়েছে বলেও জানা যায়। পারস্যদেশে একটি প্রবাদ তৈরি হয়েছিল, যুদ্ধ ক্ষেত্রে শত্রু সৈনিকের মাথা এক কোপে কেটে ফেলাকে তারা বলত “জবাব-ই-হিন্দ” অর্থাৎ ভারতীয়দের (তৈরি অস্ত্রের) জবাব। এই ইস্পাতে এমন শান দেওয়া যেত যে, অস্ত্রের ওপর একটি চুল খসে পড়লেও নাকি তা দুভাগ হয়ে কেটে যেত – এরকম কথাও লোকমুখে প্রচলিত ছিল। এধরনের অতিকথনের মাঝেও একটি সত্য লুকিয়ে থাকে, তা হল, উৎকর্ষর চরম সীমায় উত্তরণই জন্ম দেয় এরকম অতিরঞ্জিত ‘মিথ’ এর। উটজ স্টিলের উৎপাদন ইংরেজ আমলেও দেশজ রাজ্যে হত। ইংরেজরা ব্যাপক মাত্রায় এর ব্যবসায়িক উৎপাদন করতে চাইলেও ব্যর্থ হয়। কারণ অতি উন্নতমানের ধাতু হলেও এর উৎপাদন পদ্ধতিটি ছিল নিতান্ত আদিম, ফলে ব্যবসায়িক দিক থেকে লাভজনক ছিল না। শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত ইস্পাতের সাথে পাল্লা দিতে না পেরে একসময় বিদায় নেয় উটজ স্টিল। আশার কথা এই যে দক্ষিণ ভারতের স্বল্প কিছু আদিবাসীদের মাঝে এই পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে, সেখান থেকে পদ্ধতিটি ভালো করে শেখবার চেষ্টা করছেন বর্তমানের কয়েকজন গবেষক।
প্রাচীন যুগে আমাদের দেশে আয়ুর্বেদের ঔষধ তৈরিতে পাতার নির্যাস সংগ্রহের জন্য নানা ধরনের ও নানা আকারের বকযন্ত্র ব্যবহার করা হত । ইউরোপের আলেমবিক বা আরবের আল-আণবিক আর ভারতীয় বকযন্ত্র আসলে অভিন্ন। এর উৎপত্তিস্থল ভারত না হলেও ভারতীয়রা এর ব্যবহারে মোটেই পিছিয়ে ছিল না। রসায়নে আরেকটি বিষয়ে ভারতীয়রা ছিল পৃথিবীর পথ প্রদর্শক। নাইট্রাইট যৌগ নিয়ে গবেষণায় যিনি জগতকে দিশা দেখিয়েছেন সেই ‘মাস্টার অফ নাইট্রাইটস’ প্রফুল্ল চন্দ্র দেখালেন, পারদ বা মার্কারি প্রসেসিংয়ে ভারতে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। মকরধ্বজ ঔষধের একটি উপাদান হল পারদ। তিনি দেখালেন কীভাবে এই ওষুধ তৈরিতে ব্যবহৃত হত বকযন্ত্র, মাটির হাঁড়ির মাঝে কীভাবে তাপ নিয়ন্ত্রণ করা হত। পারদ প্রক্রিয়াকরণের এত উন্নত পদ্ধতি সমকালীন পৃথিবীতে অজানা ছিল।
তবু দুঃখের বিষয়, ভারতে রসায়নের এই উন্নতিগুলি না ছিল ধারাবাহিক না ছিল দ্রুত। বলা চলে প্রায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রসায়নের উন্নতি হচ্ছিল। নতুন জ্ঞান অর্জনের পর কিংবা একটি আবিষ্কারের পর বিজ্ঞান সাধারণত একটি ত্বরণ নিয়ে কিছুকাল এগিয়ে চলে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান চর্চায় তার গতি ছিল শ্লথ, যা একসময় প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে। সেকারণে দেখা যায় তেরোশো থেকে চোদ্দশো শতাব্দী পর্যন্ত এই উন্নতি হলেও তারপর তা থেমে যায়। অন্যদিকে রেনেসাঁস পরবর্তী সময়ে ইউরোপ হয়ে উঠেছিল বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির পীঠস্থান। নিত্যনতুন তাত্ত্বিক ও পরীক্ষামূলক আবিষ্কারে পৃথিবীকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছিলেন সেখানকার বিজ্ঞানীরা। আর তখন ভারতীয় বিজ্ঞান চর্চা ছিল প্রায় বন্ধ্যা। প্রাচীন ভারতের রসায়ন, এনাটমির উন্নতি, শল্য চিকিৎসার উন্নতি সব একসময় হারিয়ে গেল কেন? সভ্যতা বিকাশ-লাভের স্বাভাবিক নিয়মেই তো তার রেশ বর্তমান থাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তা হয়নি।
এই বিলুপ্তির দুটি কারণ প্রফুল্ল চন্দ্র দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ যুগের ঠিক পরে যখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আবার নতুন করে উত্থান ঘটে তাতে বর্ণাশ্রম এবং জাতিভেদ প্রথা প্রবল আকার ধারণ করে। ফলে “মস্তিষ্কের সঙ্গে হাতের একটি বিচ্ছেদ ঘটে যায়।’’ অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা বিদ্যাচর্চা করতেন, কোনো কায়িক পরিশ্রম করতেন না। অন্য দিকে শারীরিক পরিশ্রম করতেন শূদ্ররা অথচ তাঁদের লেখাপড়া করা নিষিদ্ধ। ফলে তাত্ত্বিক চর্চা এবং বাস্তবের প্রেক্ষিতে পরীক্ষানিরীক্ষা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। এভাবেই বিজ্ঞানের পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ-সিদ্ধান্ত ধারাটি ভারতে নির্মূল হয়ে যায়। ব্রাহ্মণরা অবরোহী যুক্তি বা ডিডাক্টিভ লজিকের সাহায্যে বিভিন্ন তত্ত্ব দিলেও পরীক্ষার কষ্টিপাথরে তা যাচাই করার প্রয়োজন মনে করলেন না। তার মধ্যে উচ্চ মার্গের তত্ত্ব থাকলেও পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের আওতায় তারা আসেনি। রসায়নবিদ হিসেবে নিজের হাতে রাসায়নিক নিয়ে কাজ যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা প্রফুল্ল চন্দ্র অভিজ্ঞতা থেকে জানতেন। তাই তিনি দেখান, বৌদ্ধ যুগের বর্ণাশ্রম-জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা ভারতে বিজ্ঞান চর্চার উন্নতির যে বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল তা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে ক্রমে ধ্বংস হয়ে যায়।
দ্বিতীয় যে কারণটি বিজ্ঞান চর্চার অন্তরায় হয়েছিল সেটি দার্শনিক। প্রফুল্ল চন্দ্র দেখালেন বেদান্তবাদী শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ ছিল বিজ্ঞানের পক্ষে মস্ত ক্ষতিকারক। তিনি স্বীকার করেছেন শঙ্করাচার্যের মতো প্রতিভাবান লজিশিয়ান ভারতে খুবই কম জন্মেছেন। কিন্তু সে-প্রতিভা তিনি ব্যয় করেছেন ভুল দিকে। তাঁর প্রচারিত মায়াবাদ শেখায় যে, আমাদের চারপাশের সব বস্তু, তার উপাদান সবই আসলে মিথ্যা। যে দৃশ্যমান জগতের মাঝে আমাদের অস্তিত্ব সেই বিশ্ব প্রকৃত পক্ষে অস্তিত্বহীন। এ কারণে তিনি প্রবল আক্রমণ করেছিলেন প্রাচীন ভারতের বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুবাদকে। ঋষি কণাদের অসামান্য অবদান ছিল পরমাণুবাদ। সমস্ত পদার্থ আসলে খুব সূক্ষ্ম কিছু অতি ক্ষুদ্র কণা দিয়ে তৈরি, এহেন আধুনিক মতবাদটির বিকাশ লাভ করার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়েছিল শঙ্করাচার্যের প্রভাবশালী বিরোধিতা।
এছাড়াও ন্যায়, বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত বৈশেষিকে যেভাবে এ বিশ্ব চরাচরের সমস্ত মৌল বস্তুকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল তারও তুমুল সমালোচনা করেছেন শঙ্করাচার্য। আজকের প্রেক্ষিতে সেই বিভাগ ভ্রান্তিবহুল মনে হলেও মৌলের শ্রেণীবিভাগ করার প্রয়োজনীয়তা ভারতীয়রা সে যুগে উপলব্ধি করেছিলেন, এও কম আশ্চর্যের কথা নয়। প্রফুল্ল চন্দ্র শঙ্করাচার্যের রচনার শ্লোক তুলে দেখালেন এই ধরণের সমালোচনায় তিনি কোনও রকম যুক্তির সাহায্য নেননি, কেবল মনু সহ নানা প্রাচীনতর ঋষিরা যেহেতু একে মন্দ বলেছেন, তাই এর বিরোধিতা করা কর্তব্য হিসেবে মেনেছেন। যুক্তিগ্রাহ্য মত অস্বীকারের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় কর্তৃত্বের দোহাই দেবার মতো ভ্রান্ত একটি পথ তিনি অবলম্বন করেছিলেন। অপর পক্ষে তাঁর মায়াবাদ প্রচার করেছিল বাস্তব বিমুখতা। মায়াবাদ অনুসারে বস্তু সৃষ্ট এই জগতের অস্তিত্বই যদি না থাকে, তবে সেই বস্তুর গঠন বিশ্লেষণ কিংবা তা নিয়ে গবেষণায় কেন উৎসাহী হবে মানুষ? ফলে মায়াবাদে প্রচারিত জগত সম্পর্কে এই নেতিবাচক ভাবনা নষ্ট করে দেয় বিজ্ঞান চিন্তার পরিমণ্ডল।
ভারতের বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পরীক্ষানিরীক্ষার অভাব লক্ষ করেছেন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি দেখিয়েছিলেন, সাধারণ ভাবে বিজ্ঞানের চর্চা কোনো অতীতের বিজ্ঞানীর তত্ত্বকে উন্নততর করার মাধ্যমে এগিয়ে চলে। যেমন টাইকো ব্রাহের এক জীবনের বিপুল পর্যবেক্ষণকে সূত্রে গেঁথেছিলেন কেপলার আবার কেপলারের সূত্র থেকে তত্ত্বে পৌঁছান নিউটন। ভারতবর্ষে এই বিষয়টি লক্ষিত হয়নি। কোপার্নিকাসের বহু আগে আর্যভট্ট ঘোষণা করেছিলেন পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। গ্রহদের পর্যায়ক্রমিক গতির কথাও ভারতীয়দের জানা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এদের মিলিয়ে কেউ আরও গবেষণা করেননি কিংবা এগিয়ে নিয়ে যাননি তত্ত্ব নির্মাণের পথে। বরং বাধা দিয়েছেন। আদর্শগত বিরোধ থেকে এবং পরীক্ষায় যাচাই হবার সম্ভাব্যতা না থাকায় কোনো মতবাদই সঠিক বলে নির্বাচিত হতে পারেনি। তাই সৃষ্টি হয়নি ইন্ডাক্টিভ লজিকের। সঠিক মতবাদকে একই আসনে সহাবস্থান করতে হয়েছে ভ্রান্তদের সাথে। পরবর্তীকালে তাই ভুল তত্ত্বগুলি প্রাধান্য পেয়ে যায়। আসলে বিচ্ছিন্ন ভাবে উন্নতি ঘটলেও বিজ্ঞান চর্চার একটি সার্বিক পরিমণ্ডল ভারতে গড়ে ওঠেনি। তাই নিউটন, লাইব্নিৎজ, দেকার্ত যখন ইউরোপের বিজ্ঞান জগতে রাজত্ব করছেন, তখন ভারতে বলবার মত কোনো অবদান নেই। বঙ্কিমচন্দ্রেরই মতো এ প্রসঙ্গে ব্যথিত প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছিলেন, “ভারতবর্ষের নাম বিজ্ঞানের মানচিত্র হইতে মুছিয়া গেল”।
ভারতীয় বিজ্ঞানের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আক্ষেপ হল ধারাবাহিকতার অভাবে এর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা এই যে সেই ইতিহাস ফুটে উঠেছিল যে মানুষটির কলমে সেই প্রফুল্ল চন্দ্রের বইটি নিয়েও ব্যতিক্রমী এক দুজন ভারতীয় ছাড়া কেউ বিশেষ চর্চা করেননি। অথচ বইটি বহু চর্চিত, বন্দিত হয়েছে ফ্রান্সে, ইতালিতে। আসলে দৃঢ় চরিত্রের বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র সরাসরি সমালোচনা করেছিলেন ভারতীয় বেদান্ত দর্শন ও মায়াবাদকে। কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিলেন শঙ্করাচার্যর মতো দার্শনিককে। তাই সত্য সামনে দেখেও “প্রাচীন ভারতের সবই ভালো” মতে বিশ্বাসীরা সেসময়ে তাঁকে গ্রহণ করতে পারেননি।
আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ভারতীয় বিশেষ করে বাংলার চাকরিমুখী শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে খুব অসন্তুষ্ট ছিলেন; বিদ্যাশিক্ষা যে খান কয়েক পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এ কথা বারবার বলেছেন। কয়েকটি উদ্ধৃতিতে তাঁর অসন্তোষ এবং একই সঙ্গে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্ট হয়ে উঠেছে।
“আমাদের ছেলেমেয়েদের বাল্যকাল হইতে এই ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া হয় যে বিদ্যাশিক্ষা মানে ক্লাস-প্রমোশন ও পরীক্ষা পাশ; ইহা প্রকৃত শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায়।
পুঁথিগত বিদ্যা যথার্থই ভয়ঙ্করী। কতগুলো গত্ মুখস্ত করিয়া আওড়াইতে পারাই যে বিদ্যাশিক্ষা, এ ভ্রমাত্মক ধারণা যত দিন না আমাদের সমাজ হইতে দূরীভূত হয়, ততদিন বাঙালি জাতির উদ্ধার নাই।
আইএ/আইএসসি/বিএ/বিএসসি/এমএ/এমএসসি পড়িতে হয়। ইহার বারো আনা সময়ই আলস্যে ও ঔদাস্যে অতিবাহিত হয়, কারণ ছাত্র-ছাত্রী জানে পরীক্ষার আগের দু’মাস টীকা-টিপ্পনি নোট ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিয়া পাশ করা যাইবে, ছাত্রদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা বলে যাহারা যত নির্বোধ তাহারা তত বড় পুস্তক পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করে।
আমি বক্তৃতা ও প্রবন্ধদিতে এই কথা বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়াছি যে, জগতে যাঁহারা সাহিত্যবিজ্ঞান ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে অসাধারণত্ব দেখাইয়াছেন, তাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধরাবাঁধা নিয়মের বিশেষ ধার ধারিতেছেন না, কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকেই এক একজন গ্রন্থকীট ছিলেন।’’
(জয়ন্ত কুমার ঘোষের গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)
১৩৩৯ পৌষ সংখ্যা বিচিত্রায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রফুল্ল চন্দ্রকে নিয়ে যা লিখেছিলেন, তার পুরোটাই উদ্ধৃত হওয়ার দাবি রাখে; এখানে কেবল সূচনাটুকুই উদ্ধৃত করলাম,
“আমরা দুজনে সহযাত্রী।
কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পৌঁছেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।
আমি প্রফুল্ল চন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই। যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন— কেবলমাত্র তাকে জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে ছাত্র নিজেকে পেয়েছে।’’
বস্তুজগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন ... সংসারে জ্ঞানতাপসী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাঁকে ক্রিয়াবান করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।
এটা জানানো অপ্রাসঙ্গিক হবে না গান্ধীবাদী চরকা কাটায় রবীন্দ্রনাথ উৎসাহ দেখাননি বলে অপবাদ দিয়ে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে ছাপার কালিতে লাঞ্ছিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথও খোঁচা দিতে ছাড়েননি; সকল মানুষ মিলে মৌমাছির মতো একই নমুনার চাক বাঁধবে বিধাতা এমন ইচ্ছে করেননি।
প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যে রবীন্দ্রনাথকেও ছেড়ে কথা বলবেন না এটাই স্বাভাবিক। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন নিয়ে তিনি এত কটূক্তি করেছেন যে, ব্রিটিশ রাজ্যের প্রিয়ভাজন তিনি কখনো হননি, কারণ অন্তরলোকে তিনি ছিলেন বিদ্রোহী -
“আমি বৈজ্ঞানিক, গবেষণাগারেই আমার কাজ, কিন্তু এমন সময় আসে, যখন বৈজ্ঞানিককেও দেশের আহ্বানে সাড়া দিতে হয়।’’
তিনি তা দিয়েছেনও, অস্ত্র ক্রয়ের জন্য বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য দিয়ে।
“মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, দিল্লীওয়ালা ব্যবসাবাণিজ্যের সকল ক্ষেত্র করতলগত করিতেছে, আর আমরা বাঙালিরা তাঁদের হিসাব লিখিয়া মাসমাহিনা লইয়া পরমানন্দে কলম পিষিতেছি। বাঙালি শ্রমজীবির দশাও কিছু ভাল নহে।”
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একজন আদ্যন্ত মননের বাঙালি। বঙ্গদেশে বিবিধ শিল্পোন্নতি বিধানের এবং ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারের প্রচেষ্টায় তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। তাই তিনি বাঙালির চরিত্রের গলদ কোথায় তা শত বর্ষ আগেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন। একশ বছর আগেই লিখে গেছেন –
“প্রকৃত ব্যাপার এই শিক্ষাপ্রণালীর কোথাও একটা মস্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে। কার্যক্ষেত্রে ‘পাস করা বুদ্ধি’ প্রায়ই অকেজো হইয়া দাঁড়ায়।”
আরও লিখে গেছেন-
“আমরা দোকান করিয়া ফেল মারি। কারণ সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া কৃতিত্ব অর্জনের প্রয়াস আমাদের যুবক গণের মধ্যে দেখা যায় না।”
প্রফুল্লচন্দ্র বাঙ্গালিজাতকে চিনেছিলেন যথাযথ ভাবেই। তা না হলে লিখতে পারেন অত দিন আগেই এই সাংঘাতিক সত্য কথাটা।
আমাদের জীবনটা যেন দিনগত পাপক্ষয়। শুধু আলস্যের আরাম শয্যায় শয়ন করিয়া আমরা পদে পদে মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা ও অবমাননা করিতেছি। আজ বাঙালির পরাজয় পদে পদে।
বিভুঁই উষ্ণতায় চৈতন্যচ্যুত পরাণেও হঠাৎ খেলে যায় কীর্তিমানদের খেয়াল। যদিও জং ধরা টিনে ছাওয়া হয়েছে মননের চৌচাল, তবু বিস্মিত হই যখন দেখি বিশ্বখ্যাত, বিশ্বনন্দিত এক মহান বিজ্ঞানী যিনি আমাদেরই পড়শি। অতিথি নয়, এলাকার গৌরব। অপার তৃষ্ণায় ছুটে যাই স্বরূপ বিশ্লেষণে। যদিও কার্পণ্যতায় আড়ষ্ট হয় কণ্ঠস্বর, তবু দেখি সম্মুখে মূর্তিমান এক দিব্য জ্যোতি বিজ্ঞানসাধক। যদিও একক পরিচয়ে নয় সীমাবদ্ধ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ও পরে ওই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমৃত্যু ইমেরিটাস প্রফেসর। স্বীয় মেধা-মনন-প্রজ্ঞা বলে স্যার উপাধিতে ভূষিত। কলকাতা বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা স্থাপনের এক মহৎ কর্মোদ্যোক্তা। যা চিকিৎসা জগতে অভূতপূর্ব এক নির্মাণ, আর্তমানবের সেবার আলোকবর্তিকা। একাধারে শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গবেষক, দার্শনিক, শিল্পপতি, সমাজ সংস্কারক, সমবায় আন্দোলনের পুরোধা, লেখক, পন্ডিত, বিপ্লবী, বিদ্যোৎসাহী ও বহুমুখী গুণের অনন্য সাধারণ এক বিস্ময়কর প্রতিভা তিনি। তবে বিজ্ঞানী হিসেবেই তিনি আমাদের কাছে সমধিক পরিচিত। এর লক্ষণ তাঁর ভেতর ছোটবেলা থেকেই বিদ্যমান ছিল। প্রথম জীবনে তিনি সরিষার তেল ও ঘি নিয়ে গবেষণা করতেন। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ নিয়েও তাঁকে গবেষণা করতে দেখা যেত। তবে গবেষণায় অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন ১৮৯৫ সালে। ওই বছর তিনি আবিষ্কার করেন নতুন এক যৌগিক পদার্থ। যার নাম ‘মারকিউরাস নাইট্রাইট’। এটি তাঁর আবিষ্কারগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান।
বাবা আদর করে তাঁকে ডাকতেন ‘ফুলু’ বলে। আমরা তাঁকে চিনি আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বা সংক্ষেপে ‘স্যার পিসি রায়’ নামে। বর্ণাঢ্য জীবনে কীর্তি অপার। গ্রাম বাংলার খেটে খাওয়া, ভুখা নাঙ্গা মানুষের জীবনযাপনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি তিনি। সহজ সরলতার সামাজিক দর্পণ।
আজীবন অকৃতদার। ক্লাস তাঁর সংসার, ছাত্রছাত্রীরা তাঁর সন্তান। দীপ্যমান আলোকবর্তিকার সংস্পর্শে এসে যেন সৃষ্টি হলো আরো অনেক আলোক প্রভা। একদল নব্য ও কীর্তিমান বাঙালি রসায়নবিদ সৃষ্টিতে তাঁর অবদান চির স্মরণীয়। ড. মেঘনাথ সাহা, হেমেন্দ্র কুমার সেন, বিমান বিহারী দে, ড. কুদরত-ই খুদা, প্রিয়দা রঞ্জন রায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র লাল দে, প্রফুল্ল কুমার বসু, বীরেশ চন্দ্র গুহ, অসীম চ্যাটার্জী প্রমুখ গুণধর প্রতিভারা তাঁর সান্নিধ্যে এসে প্রকাশিত হয়েছিলেন আপন মহিমায়। তাই তো তিনি বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানী। তবুও চেনার মাঝে যেন অনেক অচেনা, জানার মাঝে সুদূর অজানা, অথবা প্রচেষ্টাহীন নশ্বর জীবন আমাদের সেই জিতেন্দ্রীয় সাধককে উন্মোচনের। তিনি নন্দিত এক মহাজন। যেন হাজার বছর ধরে লিখেও শেষ হবে না তাঁর বন্দনা। কখনো তিনি সমুদ্রের মতো প্রসারিত এক বিশালতা, কখনো বারিধারায় ভিজে যাওয়া মাটির হৃদয়। কিন্তু এই সঞ্চিত মাটির প্রাণ রসায়নকে বাষ্পোন্মোচিত করার সুতীব্র প্রাণোন্মাদনা আমাদের কই?
‘প্রেম রসায়নে, ওগো সর্বজনপ্রিয়’
তাম্রপত্রে উৎকীর্ণ দু’পঙিক্তর শুরুটা এভাবেই, ‘প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজনপ্রিয়’। পরের পঙিক্তটি, ‘করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়’। পঙিক্ত দুটো রবীন্দ্রনাথেরই। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে নিয়ে লেখা। ১৯৩২-এ আচার্যের ৭০তম জন্মজয়ন্তীর সংবর্ধনায় ৭০ বছর বয়স্ক সভাপতি গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে তাঁর হাতে তাম্রপত্র তুলে দেন।
তিনি কত বড় বিজ্ঞানী, কত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প উদ্যোক্তা— এ প্রশ্নকে তুচ্ছ জ্ঞান করে রাজশেখর বসু সামনে নিয়ে এলেন - তিনি কত বড় মানুষ সে প্রশ্ন। অন্তত প্রফুল্ল চন্দ্রের কালে তাঁর সমকক্ষ কোনো মানুষের দেখা মেলেনি।
তিনি বেশি রোজগার করেননি, সে জন্য তাঁর দানের পরিমাণ ধনকুবের তুল্য নয়। তথাপি তিনি দাতাদের অগ্রগণ্য। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁকে দধীচির সঙ্গে তুলনা করেছেন। সংসার চিন্তা ও সব রকম বিলাসিতা ছেড়ে দিয়ে তিনি নিজের সমস্ত ক্ষমতা-ভাবনা আর অর্থ জনহিতে লাগিয়েছিলেন।
দেশে দুর্ভিক্ষ বা বন্যা হয়েছে, আচার্য তৎক্ষণাৎ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কোনো হাসপাতাল বা অনাথ আশ্রম বা স্কুল-কলেজে টাকার অভাব, আচার্য তাঁর নিজের পুঁজি নিঃশেষ করে দান করলেন। কোনো ছোকরা এসে বললে, আমার মাথায় একটা ভালো মতলব এসেছে, ময়রার দোকান খুলব কিংবা ট্যানারি করব কিংবা কাপড়ের ব্যবসা করব, কিন্তু হাতে টাকা নেই। আচার্য তখনই মুক্তহস্ত হলেন। নতুন শিল্প স্থাপনের জন্য তিনি অনেক লিমিটেড কোম্পানিতে টাকা দিয়েছিলেন, ডিরেক্টরও হয়েছিলেন। অনেক কোম্পানি ফেল হওয়ায় বিস্তর টাকা খুইয়েছেন, সময়ে সময়ে বদনামও পেয়েছেন কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেননি। কোন কোম্পানি টাকা ধার করবে, উনি অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে জামিন হয়ে দাঁড়ালেন।
এমনই ছিলেন বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। ধনকুবের প্রপিতামহের বার্ষিক আয় যখন ১০ হাজার টাকা, তখন সোনার ভরি কুড়ি টাকা। প্রপিতামহ মানিকলাল নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। কোনো ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা কিংবা ডাকে অর্থ প্রেরণের ব্যবস্থা বহাল না থাকায় মানিকলালের বিশ্বস্ত বরকন্দাজরা প্রায় ২০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে সেকালে দুর্বৃত্তদের ফাঁকি দিয়ে এ অর্থ খুলনার পাইকগাছার রাড়ুলি গ্রামে পৌঁছে দিত। এ গ্রামেই ২ আগস্ট ১৮৬১ প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জন্ম। মাস তিনেক আগে ৮ই মে ১৮৬১ সালে কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে ধনাঢ্য ঠাকুর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। প্রফুল্ল মূলত বৈজ্ঞানিক লেখালেখি যথেষ্ট পরিমাণে করেছেন, তবে আত্মজীবনীতে নিজের কথা বিশেষ করে শৈশব ও বেড়ে ওঠার কাহিনীরও অকপট বর্ণনা দিয়েছেন।
যশোর কালেক্টরেটের সেরেস্তাদার আনন্দলাল রায় সম্পদের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে পরিবারের কুবের পরিচিতি ধরে রেখেছিলেন।
‘‘এত ঐশ্বর্য, এত প্রাচুর্য, রায়দেব পিতামহ আনন্দলাল রায় যশোরে হঠাৎ সন্যাসরোগে মৃত্যুবরণ করেন। সঞ্চিত অর্থ ও স্বর্ণ বিশাল বাড়িতে বা কোথাও কোনো গোপন স্থানে ছিল কিনা কিছুই জানতে পারেন নাই আমার পিতা হরিশচন্দ্র রায়। ছোটবেলায় দেখেছি বাড়ির অনেক জায়গায় শাবল দিয়ে ইট খোঁচানো চিহ্ন। ভাঙা ভাঙা স্থান বিশাল বাড়িতে কোথাও সেই কল্পিত সম্ভাব্য গচ্ছিত ধনের সন্ধান মেলেনি।’’
আনন্দলাল রায়ের অর্থ লগ্নি করা ছিল পামার অ্যান্ড কোম্পানি নামের ব্রিটিশ এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে। তিনি তখন দাবায় মনঃসংযোগ করেছেন, এমন সময় বার্তাবাহক যে চিঠি নিয়ে এল তার সারকথা, পামার অ্যান্ড কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ চিঠির দিকে তাকিয়ে থেকে তিনি আবার খেলায় মন দিলেন। এ ঔদাসীন্যের সাথে যোগ হলো প্রফুল্ল চন্দ্রের বাবা হরিশচন্দ্রের যথেচ্ছ দানশীলতা। কালেক্টরেটের মালখানার মতো তাঁদের বাড়িতেও মালখানা নামের লোহার ভল্ট ছিল। জমিদারির এক একটি অংশ যখন বিক্রি হতে চলেছে, প্রফুল্ল চন্দ্রের মা ভুবন মোহিনী দেবী গুনীন ডাকিয়ে আনেন— গুনীন তার অপার্থিব জ্ঞান দিয়ে জানিয়ে দেবে এ বাড়ির কোথায় কোথায় গুপ্তধন রয়েছে। গুনীনের কথায় যথেষ্ট খোঁড়াখুঁড়ি হলো, কিন্তু ধনের হদিস মেলেনি। আট বছর বয়সী কিশোর প্রফুল্ল গুনীনের শক্তিতে এতটুকুও বিশ্বাস করেননি। কারণ গুনীনের কথায় জ্ঞানের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তিনি মাকে আশ্বস্ত করেছেন, অর্থ উপার্জন করে প্রয়োজন মেটাবেন, কিন্তু মিথ্যে আশ্বাসে বাড়িঘর আর ভাঙচুরের দরকার নেই।
প্রফুল্লের জন্মের নয় বছর আগে হরিশচন্দ্র স্ত্রী ভুবন মোহিনীর নামে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একটি উদার ও অসাম্প্রদায়িক পরিবেশে তিনি লালিত হয়েছেন। বর্ণপ্রথা, অস্পৃশ্যতার নামে জাত্যভিমানের বাড়াবাড়ি তিনি কখনো মেনে নেননি। মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে কংগ্রেসের ফরিদপুর অধিবেশনে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বলেছিলেন,
‘‘কুকুর বিড়াল আঁস্তাকুড় থেকে এসে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলে আমাদের জাত যায় না, মনে কোনো নীচভাব জাগে না। অনুন্নত হিন্দুসমাজের তথাকথিত ছোট জাত অনুন্নত শ্রেণীকে, মুসলমানকে চিরদিন অধম ঘৃণ্য মনে করে, পদদলিত, শোষণ, অত্যাচার করে এক ঘরে করে রেখে বাংলার সমগ্র সমাজ দেহটাকে সবদিক থেকে দুর্বল ও ঘুণ ধরবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।’’
‘ছুটির অবকাশে ছাত্রদের কর্তব্য’ - এই শিরোনামের একটি নিবন্ধে আরো স্পষ্টভাবে এই বর্ণপ্রথাকে তুলোধুনো করেছেন। ৫৫ কোটি মানুষের দেশ চীন (যখন নিবন্ধটি লিখিত হয়, তখনকার হিসেবে) তিন হাজার বছরের জড়তা কাটিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি লিখেছিলেন,
‘‘চীনের অধিবাসী মুসলমানের সংখ্যা প্রায় এক কোটি (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্ট)। কিন্তু এই সকল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যে ছুত্মার্গ (ছোঁয়াছোঁয়ির কুসংস্কার) নেই। এই ছুত্মার্গ আমাদের উন্নতির পথে এক মস্ত বাধা। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণেরাই বেশি গোড়া। তাঁরা যখন বিদেশীদের হাতে প্রস্তুত গোলাপজল, কেওড়া জল, লেমনেড, ফান্টা, কোকাকোলা, চকোলেট ঔষধপত্র ইত্যাদি পান করে, তখন তাদের জাতবিচার থাকে না। কিন্তু যদি নমশূদ্র বা মুসলমান ঘরের চৌকাঠে দাঁড়ায়, তাহলে বিশ হাতের দূরের খাদ্য, জল তাঁদের নিকট অস্পৃশ্য হয়ে যায়। জানি না হিন্দু শাস্ত্রের কোথায় এরূপ ব্যবস্থা বিধিবিধান আছে।’’
জয়ন্ত কুমার ঘোষ আচার্য প্রফুল্লের জীবন স্মৃতি আলোচনায় প্রফুল্লের শিশুমনের মৌলিক প্রশ্নগুলোকে সামনে নিয়ে এসেছেন—মেঘ কেন ডাকে? বিদ্যুৎ কেন চমকায়? মানুষ কেন মরে? মানুষ মৃত্যুর পর কোথায় যায়? মা যতটা সম্ভব উত্তর দিয়েছেন। ছেলেকে সুশিক্ষিত করতে হবে এবং কলকাতার শ্রেষ্ঠ স্কুলে পড়াতে হবে। জমিদারির দায়দায়িত্ব কর্মচারীদের ওপর ছেড়ে দিয়ে চার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হরিশচন্দ্র ১৮৭০-এ বসত গাড়লেন কলকাতায়। সবার বড় জ্ঞানেন্দ্র জুনিয়র বৃত্তিপ্রাপ্ত, মেজ নলিনী পরবর্তীকালে বোম্বে মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তার, সেজ প্রফুল্ল, ছোট পূর্ণচন্দ্র—কলকাতার আর্মহাস্ট স্ট্রিটে বাসা। ১৮৭১-এ প্রফুল্ল ভর্তি হলেন হেয়ার স্কুলে। ১৮৭৪-এ অসুখে আক্রান্ত হয়ে দুবছর স্কুলের বাইরে, কিন্তু সময় নষ্ট হতে দেননি, ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞান-বিষয়ক পড়াশোনায় ব্যস্ত রাখলেন নিজেকে,
‘‘আমি গ্রোগ্রাসে বই গিলতাম, আমার বয়স তখনও বার বছর হয়নি। ভোর তিনটা চারটায় ঘুম থেকে উঠতাম— কোন রকম ব্যাঘাত ছাড়া একটানা পড়া চালিয়ে যেতাম। নিউটন ও গ্যালিলিওর জীবন এবং তাদের অবদান আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে।’’
তাঁর প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের কষ্টকর জীবন ও অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানকে মানবকল্যাণের কাজে লাগাতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। গোল্ডস্মিথের ভিকার অব ওয়েকফিল্ড, শেক্সপিয়ারের জুলিয়াস সিজার ও হ্যামলেট, জর্জ এলিয়টের সিনস ফ্রম ক্ল্যারিক্যাল লাইফ; এদিকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, প্রফুল্ল ব্যানার্জির বাল্মীকিও তাঁর যুগ, রামদাস সেনের কালিদাসও তাঁর যুগ, রাজেন্দ্র লাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ আর কলকাতা থেকে প্রকাশিত বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা ও সাময়িকী, সে সাথে ল্যাটিন ভাষা শেখা— অপার এক আনন্দ ও জ্ঞানের জগতে মেতে ওঠেন তিনি। এর মধ্যে নতুন করে ভর্তি হলেন অ্যালবার্ট স্কুলে। এখানে পুরস্কৃত হলেন উইলিয়াম হ্যাজলিট ও শেক্সপিয়ারের রচনা সমগ্র। থ্যাকারের ইংলিশ হিউমারিস্টস অফ দ্য এইটিন্থ সেঞ্চুরি, অ্যালবার্ট স্কুলে কেশব চন্দ্র সেনের বক্তৃতা ও বিশ্লেষণ তাঁকে ব্রাহ্মসমাজের সদস্য হতে আকৃষ্ট করে।
১৮৭৯ থেকে ১৮৮২ তিনি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের ছাত্র, একই সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে স্যার জন এলিয়ট এবং রসায়নে স্যার আলেক্সান্ডার পেডলারের লেকচার সেশনে অংশ নেন এবং সেকালের দুর্লভ এক বৃত্তি গিলক্রিস্ট স্কলারশিপের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছ’বছরের বৃত্তি লাভ করেন।
সময় খানিকটা বদলে গেলেও ‘কালাপানি’ পাড়ি দিলে জাত খোয়ানোর আশঙ্কা রয়েই যায়। ১৮৪১-এ দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন বিলেত যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁর আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, বাড়ির মাইনে করা দৈবজ্ঞ পুরোহিতের দল যেন একজোট হয়ে দ্বারকানাথকে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, জাতিভ্রষ্ট, সমাজভ্রষ্ট হওয়াটা অনন্ত নরক যন্ত্রণার তুল্য। কালাপানি পেরোবার ফলে তাঁর বয়োজ্যেষ্ঠ ও পরম শ্রদ্ধের রামমোহন রায়ের কী দুর্দশা হয়েছিল, সে কথাটা তো একবার ভাবা দরকার। শাস্ত্রের নিষেধ অমান্য করার ফলে কী দণ্ডটাই না তিনি পেলেন— বিদেশে-বিভুঁয়ে বেঘোরে তাঁর মৃত্যু হল, অগ্নিসৎকার তো হলই না, কবর দেওয়া হল অপবিত্র জমিতে— যেন তিনি ম্লেচ্ছদেরও অধম। এখন অভিশাপ কি কেউ সাধ করে কুড়াতে চায়?
দ্বারকানাথ যখন দ্বিতীয়বার কালাপানি পাড়ি দিলেন, দেশীয় ভ্রাতৃবর্গের আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল। ১লা আগস্ট ১৮৪৬ লন্ডনে আলবেমার্ল স্ট্রিটে সেইন্ট জর্জেস হোটেলে মাত্র ৫১ বছর বয়সে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পাপের ভাগ মাথায় নিয়ে দেহত্যাগ করলেন।
সে পথেই পা বাড়াচ্ছেন খুলনার রাড়ুলির ছেলে প্রফুল্ল। ১৮৪৪-এ দ্বিতীয়বার বিলেত যাত্রার সময় দ্বারকানাথ মেডিকেল কলেজের দুজন ছাত্রের সমুদয় ব্যয়ভার বহন করে ও বৃত্তি দিয়ে তাঁর সাথে বিলেত নিয়ে যাবার জন্য সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখলেন। আশঙ্কা ছিল জাত খোয়ানোর আতঙ্ক বাধা হয়ে দাঁড়াবে। শেষ পর্যন্ত চারজন— ভোলানাথ বসু, সূর্যকান্ত চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বসু ও গোপালচন্দ্র শীল ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করলে দ্বারকানাথের টাকায় দু’জনের, ইংরেজ শিক্ষক প্রফেসর গুডিভের টাকায় ৩ জনের, বাংলার নবাব নাজিমের চার হাজার টাকাসহ কিছু চাঁদায় অপর একজনের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। জাত যাওয়ার যত আশঙ্কাই থাকুক— এই চারজনই ভারতবর্ষের প্রথম এফআরসিএস এবং এমডি।
৪০০ টাকা দামের টিকেট কিনে এসএস ক্যালিফোর্নিয়া জাহাজে বিলেত রওয়ানা হলেন প্রফুল্ল।
কিন্তু পরাধীনতা যে গ্লানির বিষয় এবং উপনিবেশীকরণ যে গৌরবের কিছু নয়, তা তাঁর কথায় প্রকাশিত হতে সময় লাগেনি, তিনি সহিংস কখনো হননি, কিন্তু পরাধীনতার জ্বালাতে পীড়িত হয়েছেন, ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়েছেন তাঁর ইংরেজ অধ্যাপক অকুণ্ঠ প্রশংসা করেও তাঁর জন্য এক সময় ভালো চাকরি নিশ্চিত করতে পারেননি।
৫ই এপ্রিল ১৮৮৮ সাল, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ক্রাম ব্রাউন লিখছেন,
‘‘১৮৮২ সালে ডক্টর পিসি রায় যখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন, তখন থেকেই তাকে আমি চিনি, খুব আগ্রহ নিয়ে আমি তার অধ্যয়ন ও পেশাগত দিক পর্যবেক্ষণ করেছি। সাধারণভাবে বিজ্ঞানে তাঁর ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত, বিশেষ করে তিনি রসায়নে আত্মনিবেদিত। ১৮৮৫ সালে তিনি বিএসসি এবং ১৮৮৭ সালে ডিএমসি ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮৭-৮৮ বর্ষে তিনি রসায়নে হোপ প্রাইজ স্কলারশিপ লাভ করেছেন। ১৮৮৩-এর মে থেকে শুরু করে ১৮৮৮-এর মার্চ পর্যন্ত তিনি সামার ও উইন্টার সেশনে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ডক্টর গিবসন ও আমাকে সহায়তা করেছেন। আমার তত্ত্বাবধানে তিনি যে কাজ করেছেন, তাতে আমি তার কর্মক্ষমতা ও জ্ঞানের পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে পারি। তাত্ত্বিক রসায়নের সকল শাখা সম্পর্কে তিনি বিশেষভাবে অবহিত। তিনি একজন সতর্ক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষক। তিনি দেখাতে সমর্থ হয়েছেন ডিএমসি ডিগ্রির জন্য মৌলিক গবেষণার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। তাঁর কাজটি চমত্কার বিশ্লেষণধর্মী, সুসংগঠিত, সচেতনভাবে এবং যথাযথভাবে তা সম্পাদিত হয়েছে।’’
কিন্তু এতেও বিলেতে তাঁর ভাগ্য খোলেনি।
তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার পাশাপাশি জীবনভর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি ‘উদ্যোক্তা’ হয়েই রইলেন।
তাঁর হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম রাসায়নিক দ্রব্য ঔষধ তৈরির কারখানা বেঙ্গল কেমিকেল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস। তাঁর হাতে অপূর্ণাঙ্গ পিরিয়ডিন টেবিল সমৃদ্ধ হয়, ১৮৯৫ সালে তিনিই আবিষ্কার করেন মারকিউরাস নাইট্রেট যৌগ। কেবল রসায়ন-বিষয়ক তাঁর আবিষ্কার পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনার দাবি রাখে। তিনিই বাংলায় শিল্পায়নের প্রধান উদ্যোক্তা। বাংলায় বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় প্রফুল্ল চন্দ্রের যে অবদান, তাঁর সমকক্ষ কেউ দুর্লভই হবেন।
বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা যতটুকু এগিয়েছে, অন্যতম পথিকৃৎ তিনিই। ১৬ই জুন ১৯৪৪ সালে চিরকুমার মহান এই আচার্যের প্রয়াণ ঘটে।
প্রশ্ন হল, ভারতীয় জনমানস কি আজও প্রস্তুত, মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস হারিয়ে সে সত্য মানতে, যে সত্য আজ থেকে প্রায় এক শতাব্দী দুই দশক আগে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়?
(তথ্যসূত্র:
১- অধ্যায়ন ও সাধনা, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সুত্রধর (২০১০)।
২- দেশপ্রেমী বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, টিচার্স বুক এজেন্সী (২০১১)।
৩- আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের পল্লি মঙ্গল, ড. তপন বাগচী, কলি প্রকাশনী (২০১১)।
৪- আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়: জীবন, কর্ম, রচনাসংগ্রহ; ড. সন্তোষকুমার ঘোড়ই, পারুল প্রকাশনী (২০১০)।
৫- আত্মচরিত (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়।
৬- আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রনজিত কুমার মন্ডল, পুথিনিলয় প্রকাশনী।)






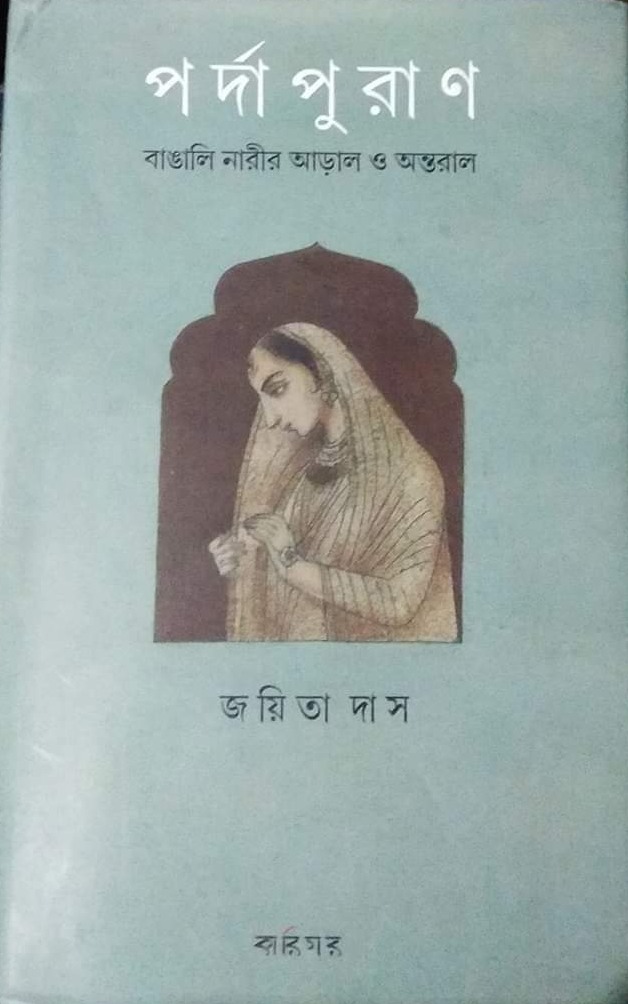
0 মন্তব্যসমূহ